নবগঙ্গা থেকে আদিগঙ্গা, ভুঁইফোঁড়দের সুলুক-সন্ধান ঃ পর্ব দুই
Posted by bangalnama on December 22, 2010
– লিখেছেন রবি-দা
৩
উদ্বাস্তু স্রোতের ভেসে আসা মিছিলে সমাজের সব শ্রেণীর মানুষজন ছিলেন – শ্রমজীবী থেকে বুদ্ধিজীবী, চাষী, কামার, কুমোর, ধোপা, নাপিত, পুরোহিত, শিক্ষক, অধ্যাপক, উকিল, ডাক্তার, মোক্তার – সবাই। জীবিকার সন্ধানে তাই প্রথমে যে যার রাস্থায় হাঁটার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউ কেউ ছোটখাটো ঠিকানায় পৌঁছে গেলেও সকলের মনস্কামনা পূরণ হবার ছিল না। শ্রমজীবীদের অধিকাংশও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লেন আরো বিস্তৃত পরিসরে, একে অপরকে খোঁজ দিতে লাগলেন কাজের। পূর্ববঙ্গের সীমানা পেরিয়ে কলকাতা পর্যন্ত অঞ্চলের রূপরেখা পাল্টাতে লাগল হঠাৎ করে। খেদিয়ে দেওয়া ওই বাঙালদের মধ্যে যেভাবেই হোক কিছু একটা করবার দুর্নিবার ইচ্ছা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল, তাদের কাছে কোনো বাধাই আর বাধা থাকল না, থাকল না লজ্জা-সঙ্কোচের বালাই। মাস্টারের ছেলে বাড়ি বাড়ি পেন্সিল বিক্রি করতে বেরোলেন, কেই বা চেনে তাঁকে ওই বিশাল জন-অরণ্যে, তাই না? গামছা, ধূপকাঠি, অ্যালুমিন্যিয়ামের বাসনপত্র, এইসব নিয়ে সরাসরি খদ্দেরের কাছে পৌঁছে যাবার এই পুরানো প্রচেষ্টা নতুন করে জোরদার হয়ে উঠল বাঁচার তাগিদে। “মনে রেখো, তোমার বাপ-ঠাকুর্দারা করেনি এসব!” – এককালের এই বহু-উচ্চারিত সতর্কবাণী কালের গভীরে চাপা পড়ে গেল, প্রচলিত সব ধ্যান-ধারণাকে তাচ্ছিল্য করে বাঙাল পৌঁছে গেল নদীয়া, মূর্শিদাবাদ, চব্বিশ পরগনার গ্রামে-গঞ্জে। চাষবাসের কাজে জোয়ার এল, জমির চেহারা পাল্টাতে লাগল, পতিত জমি, দাঙ্গা জমি, খাল-বিল সবকিছু সবুজ হতে লাগল – কোনো অদৃশ্য জাদুবলে নয়, প্রচণ্ড জেদী এবং বাঁচতে চাওয়া মানুষদের মেহনতী ঘামে। মানকচু, চালতা, নলতে শাক, কচুর লতি, কচুর শাক, শালুক ফুল/ডাঁটা(যাকে কলকাতার ঘটিরা তখন ‘কয়েল’ বলে ঠাট্টা করতেন) – এসব বাজারে এল পণ্য হয়ে, হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল ফুটপাথের তরকারি বাজারে। কিন্তু চাহিদা ও যোগান দুটোই বেড়ে গেল ওইসব হাস্যকর শাক-সব্জির, কারণ এখানে মাঠে-ঘাটে-গাছে তারা বেওয়ারিশ হয়ে পড়ে থাকত অবহেলায়, তাদের কোনো মালিকানা ছিল না – তাই বেশ সস্তায় বিক্রি হত বলে ভুখা বাঙাল খরিদ্দারও খুব খুশি মনে ঘরে আনতে লাগলেন তাদের। এই কৃষিকাজে লিপ্ত মানুষদের আলাদা করে বসতি গড়ে উঠতে লাগল গ্রামের পরিচিত সীমানার বাইরে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত খাসজমিতে। ঢাকা ও টাঙ্গাইলের বিস্তীর্ণ অঞ্চলের তন্তুবায় গোষ্ঠীর লোকজন চলে গেলেন শান্তিপুর, ফুলিয়া-সহ নদীয়া ও মূর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন অঞ্চলের আনাচে-কানাচে। জলবায়ু ও পরিবেশগত কারণে সেখানে আগে থেকেই ওই সম্প্রদায়ের মানুষজন সুনামের সাথে কাজ করতেন, পূর্ববঙ্গের বস্ত্রশিল্পীদের সাথে সেই অঞ্চলের শিল্পীদের নিরবিচ্ছিন্ন যোগাযোগও ছিল। প্রথম প্রথম ছিন্নমূল, কপর্দকহীন তাঁতশিল্পীরা মহাজনের কাছ থেকে বানী নিয়ে শাড়ি বুনতেন, পরে অনেকেই তাঁত বসিয়ে মাকু চালিয়ে বাড়িতে অন্যান্য জরুরি প্রাত্যহিকী বহাল রেখেও সবাই মিলে কাপড় বুনতে লাগলেন। বস্ত্রবাজারে, বিশেষ করে শাড়ির জগতে বাজিমাত করে দিল তাঁতের শাড়ি – ঢাকাই জামদানি, বালুচরী, নকশা পাড়, হাজার বুটি, বনেদীয়ানার শীর্ষে চলে এল ওপারের শিল্পীদের নিরন্তর সাধনা ও কারিগরী নৈপুণ্যে। লাল চওড়া পাড় সাদা খোলের শাড়ি বঙ্গনারীদের আধুনিকতার প্রতীক হয়ে উঠল, আটপৌরে মোটা সুতোর শাড়ির চাহিদাও ছিল আকাশচুম্বী, একটু খাটো হত সেসব শাড়ি কিন্তু দাম ছিল কম ও টেকসই ছিল খুব। একইসাথে শান্তিপুর ও কলকাতার মানিকতলায় হাট বসত ওইসব শাড়ির, হারানো মাটি খুঁজে পাওয়ার স্বাদ পেল ধীরে ধীরে বহু শ্রমজীবী উদ্বাস্তু সম্প্রদায়। তবে হইহই করে সাড়া ফেলে দিয়ে কলকাতার ফুটপাথে ক্রেতা-বিক্রেতার মিলন ঘটাল আরেকদল সর্বহারা। আগেই বলেছি, লাজলজ্জা-দ্বিধা-সঙ্কোচ সবকিছু খড়কুটোর মত ভেসে গেছিল তাদের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের ধাবমান স্রোতে। ঘরে বসে পরিবারের সবাই মিলে বাজারের চাহিদামত বানাতে লাগলেন ডালের বড়ি, ঘি, ধূপকাঠি, খবরের কাগজের ঠোঙা, কুলের আচার, আরো কত কি! এলাকা এলাকার ফুটপাথের বাজারে সেসব সামগ্রী নিয়ে পৌঁছে যেত বাপ-ব্যাটা, সবাই মিলে। খদ্দের স্থায়ী হতে শুরু হলেই জিনিসের গুণগত মান নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতার ইন্টার্যাকশন জমে উঠল, বিক্রেতা উৎসাহী হয়ে ক্রেতার চাহিদা ও পরামর্শকে বাস্তবায়িত করতে সচেষ্ট হলেন। কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই অল্প পুঁজির খুদ্র আকারের কুটিরশিল্পের এক নতুন দিগন্তের সূচনা হল। পাঠক অবাক হবেন জেনে যে পরবর্তীকালে এদের তৈরি বেশ কিছু সামগ্রী ব্র্যান্ডেড হয়ে কলকাতার বাজার দখল করেছে শুধু গুণগত মানের সুনামের নিরিখে। অপরদিকে, দূর-দুরান্তে যাদের পুঁজিপাটা একেবারেই কিছু ছিল না, তারাও হাল না ছেড়ে খেজুরের রস, তালের শাঁস, মাঠেঘাটে ছড়িয়ে থাকা সুষনি শাক, হিঞ্চে শাক, ফুল-বেলপাতা, কলাপাতা, কচুপাতা, শামুক, গুগলি – এসব বয়ে এনে বসে গেলেন বাজারে। শুধু বিক্রেতার ভূমিকাতেই নয়, আবার ক্রেতা হয়ে বাজার দখলে নামলেন আরেকদল পরিশ্রমী বাঙালের দল। বড়সড় চট অথবা লাল শালুর বস্তায় দাঁড়িপাল্লা, বাটখারা বয়ে নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ক্রয়-অভিযান চালালেন পুরনো খবরের কাগজ, বইখাতা, শিশি-বোতল, টিন-লোহা-অ্যালুমিনিয়াম, শাড়ি-জামাকাপড়, মায়ে প্লাস্টিকের চিরুনি কৌটো পর্যন্ত নিয়ে। PL ক্যাম্পে ভীড় কমতে লাগল, রাজ্যের অর্থনীতিতে রিফিউজিদের এই অগ্রগতি দেখে তখনকার কিছু মানুষ মনে হয় শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। এটা স্বাভাবিক ছিল, কারণ তাঁদেরও সন্তান-সন্ততির ভবিষ্যতের চিন্তা ছিল; স্বাভাবিকভাবেই আওয়াজ উঠল “হকার উচ্ছেদ”-এর। রাজনৈতিক বা যে কোনো কারণেই হোক, কম্যুনিস্টরা খেটে খাওয়া মানুষদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন, কংগ্রেসও অসহায় হয়ে চুপ করে রইল রাজনৈতিক জমি হারিয়ে যাবার ভয়ে।
বাঙালদের ফুটপাথ-অভিযান আরো গতিশীল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কলকাতার চতুর্দিকে, নানা পরিসরে। উপায় না দেখে প্রতিষ্ঠিত বণিক-কূল নতুন করে নিজ সামগ্রী ফুটপাথে সাজিয়ে দিলেন সেই হকারদের হাত ধরে। বড়বাজারের গদির ঠিকানায় উদ্বাস্তু হকার পৌঁছে গেল কালের আহ্বানে, কাজেই অল্প হলেও কিছু সর্বহারাদের সামনে বিনিয়োগের সমস্যা আপাতত রইল না। পরিশ্রম, মেধা ও সর্বোপরি সততার কারণে অনেকেই দুটো পায়ের নীচের মাটি শক্ত করে নিতে পারলেন এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে, আবার হারিয়েও গেলেন অনেকে। শিয়ালদা স্টেশন পেরিয়ে বউবাজার স্ট্রীট ধরে বাঁয়ে কোলে মার্কেট, ডাঁয়ে পাইকারি মাছের বাজার পেরিয়ে অ্যামহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে এসে ফিকে হত ফুটপাথের ৩৬৫ দিনের জনজোয়ার। পরে সোনাপট্টি পেরিয়ে রূপম সিনেমা ও ছানাপট্টি হয়ে প্রায় লালবাজার পর্যন্ত ছিল কাঠশিল্পে যুক্ত পূর্ববঙ্গের বহু মানুষের কর্মকেন্দ্র – অসংখ্য শিল্পী কাজ করতেন ছোট ছোট দোকানঘরে, ফুটপাথে বসে পালিশ করতেন খাট, আলনা ইত্যাদি সব আসবাব। এঁরা থাকতেন চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন গ্রামগঞ্জে, নৈহাটি পেরিয়ে হালিশহর ও বারাসাত পেরিয়ে হাবড়া পর্যন্ত প্রতিদিন আসা-যাওয়া করতেন, টিফিন-ক্যারিয়ারে আসত দুপুরের খাবার। খাট-পালঙ্কে নতুন নতুন নকশার আবির্ভাব ও রুচি পরিবর্তনের হাওয়া উঠল ফার্নিচার-শিল্পে, মালিকানার হাত-বদলও হতে দেখা গেল ওইসব দোকানের পরবর্তী সময়ে।
স্বর্ণশিল্পে যুক্ত বহু মানুষ কলকাতা ও তার আশেপাশে আপন বৃত্তি-সন্ধান করে নিতে পারলেন, যারা পারলেন না, তাঁদের কেউ কেউ বর্ধমান, মূর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পৌঁছে গেলেন কোনো না কোনো যোগসূত্র ধরে – জীবিকায় প্রতিষ্ঠিত হলে এঁরা পরিবারের লোকজনকে নিয়ে আসতেন নতুন ঠিকানায়। জীবিকাভিত্তিক কাজ ও ব্যাবসার পরিসর এবং পরিধির উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি ঘটার সাথে সাথে PL ক্যাম্পের চেহারা যেমন কৃশ হতে লাগল, ঠিক তেমনই কলকাতা ও শহরতলির খালে-খন্দে, মাঠে-ঘাটে, জবরদখল নেওয়া এলাকার বাঙালদের ঘরবাড়ির চেহারাও বদলাতে শুরু করল – ছিটে বেড়ার জায়গায় ইঁটের পাঁচিলে ঘেরা পড়ল নারকেল গাছের সারি আর প্লাস্টারবিহীন টিনের চালের ঘরে ঘরে রাতে মিটমিট করতে দেখা গেল ইলেক্ট্রিক ল্যাম্প। আমার ঠাকুরদা, বাবা, বয়স্ক সব গুরুজনদের দেখতাম ‘PL’ শব্দটি শুনলে মনে বেশ কষ্ট পেতেন তাঁরা, কারো liability হয়ে বেঁচে থাকাটা তাঁদের কাছে খুব অসম্মানের ছিল, সেটা বুঝতে পারতাম। ধীরে ধীরে এই ধারণার ব্যাপ্তি সমাজের পটে চিত্রিত হয়ে উঠতে থাকল উদ্বাস্তুদের অর্থনৈতিক উত্থানে। এখন এই PL অ্যাক্টের অস্তিত্ব আছে কিনা বুঝতে পারি না, কিন্তু একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি যে “বাঙালেরা বহু কষ্ট করে তবেই বাঙাল” হতে পেরেছে। মনে হয় আগামীর ইতিহাসে নিশ্চয়ই তাদের এই সংগ্রামী বিবর্তনের কথা লেখা থাকবে ও প্রেরণা যোগাবে যেকোনো প্রতিকূলতার মধ্যে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার।
উদ্বাস্তু সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রমজীবিরা যত শীঘ্র ও সহজে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, বুদ্ধিজীবিদের ক্ষেত্রে সেটা করতে কিছুটা দেরি হয়েছে নানা কারণে – তাঁরা শুরু করেছিলেন প্রাইভেট ট্যুইশনকে আপাতকালীন হাতিয়ার করে। ধীরে ধীরে তার বিস্তৃতি ঘটতে থাকে, টিউটরদের গুণগত মানের পরিচয় তাদের নতুন নতুন ঠিকানার সন্ধান দিতে থাকল। সব থেকে উল্লেখ্য হল, ওইসময়কার মাস্টারমশাইদের প্রভূত সম্মান ছিল – বেশভুষা, চেহারা বা ভাষা দিয়ে তাঁদের কেউ মূল্যায়ন করতেন না, পড়ানোর ফাঁকে চা-মুড়ি-বিস্কুট থাকতই থাকত যখন যেমন। তারও পরে কলকারখানায়, সরকারী চাকরিতে, সওদাগরী অফিসে অল্পস্বল্প সুযোগ আসতে লাগল, আশায় বুক বাঁধতে লাগলেন তাঁরা, রেজিস্টার্ড রিফিউজিদের জন্য জব রিজার্ভেশনের আওয়াজ উঠতে লাগল। আরো কিছুকাল অতিক্রান্ত হলে স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি, কোর্ট, জরুরি গভর্নমেন্ট অফিসের অলিন্দে প্রবেশ ঘটতে লাগল তাঁদের।
দেশ বিভাজনের সন্ধিক্ষণে সবথেকে টালমাটাল অবস্থায় ছিল ছাত্রসমাজ, তারা পঠন-পাঠনের বাইরে এসে অনিশ্চয়তার ঘেরাজালে বন্দি হয়ে রইল, কারণ সীমানা পেরিয়ে এসে প্রথমেই উদরপূর্তির তাগিদে পরিবারের পূর্ণবয়স্ক মানুষেরা ছোটাছুটি করতে লাগলেন, আর অসহায় হয়ে থাকা নানা পাঠক্রমের ছাত্রছাত্রীরা অচেনা-অজানা নতুন পরিমণ্ডলে নিজেদের অবস্থান ঠাহর করতে পারল না। কিন্তু অচিরেই তাদের মনে একটা ধারণা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হয়ে উঠল যে, এই পরিবেশ থেকে একমাত্র পড়াশোনাই তাদের মুক্তি দিতে পারে, দ্বিতীয় কোনো পথ আর নেই। তাদের সংকল্প হল, “পড়ব কিম্বা মরব,” আর এই সংকল্পের জোয়ারে নতুন দিগন্তের সূচনা হল লেখাপড়ার জগতে – স্কুল কলেজে উপচে পড়ল বিবর্ণ, ছিন্ন পোষাক-আষাকে দোয়াত-কলম হাতে আসা নতুন ছাত্রদের ভীড়।
তখনকার কলকাতায় বুনিয়াদি শিক্ষার ভালই চল ছিল, কর্পোর্যাশনের তত্তাবধানে প্রায় সব এলাকাতে ছিল প্রাইমারি স্কুল। এদের নাম শুনে মনে হয় বিত্তবান ও হৃদয়বানদের দানে গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো, যেমন “শশীভূষণ দে অবৈতনিক বিদ্যালয়,” পাশেই ছিল “রাজ রাজেশ্বরী বালিকা বিদ্যালয়”…এইরকম আর কি। ছেলে ও মেয়েদের স্কুল ছিল আলাদা, বিনা বেতনের এই স্কুলগুলিতে পঠন-পাঠনের মান ছিল সেইসময়ের নিরিখে খুবই উৎকৃষ্ট, নিয়মিত হোমটাস্ক থাকত, বই পাওয়া যেত বিনামূল্যে কিংবা স্বল্পমূল্যে। “বর্ণপরিচয়,” “ধারাপাত,” “আদর্শলিপি,” ছিল মূল পাঠ্যপুস্তক, “গল্পলহরী” থাকত র্যাপিড রিডিংয়ের প্রয়োজন মেটাতে। শিক্ষকেরা ছিলেন ছাত্র-নিবেদিতপ্রাণ, নিজের ক্লাসের সব ছাত্রের নাড়ি-নক্ষত্র জানতেন তাঁরা, মেধাবী ছাত্রেরা ছুটির দিনে চলে যেতে পারত মাস্টারমশাইয়ের মেসবাড়িতে, অভিভাবকদের সাথেও তাঁদের নিয়মিত যোগাযোগ থাকত। এই পরিবেশকে মূলধন করে চটজলদি হাতেখড়ি সাঙ্গ হতেই সীমানা পেরিয়ে আসা কচিকাঁচাদের দলকে দাদু কিংবা বাবা গিয়ে ভর্তি করে দিয়ে আসতেন। আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নপূরণের অভিযানের শুরু এখানেই, চতুর্থ শ্রেণীর গণ্ডি পেরিয়ে এবার হাইস্কুল – মেট্রোপলিটান, বঙ্গবাসী, কলিন্স, হেয়ার, হিন্দু, বেথুন, সংস্কৃত – মেধা অনুসারে হাইস্কুলে দাখিল হতে খুব একটা অসুবিধা হত না। মুশকিল হত স্কুল ফীস নিয়ে, সকলের তা দেওয়ার সামর্থ্য থাকত না, কিন্তু মেধাবী ছাত্রেরা আবেদন করলেই স্কুল ফীস মকুব হয়ে যেত কোনো রকম সুপারিশ ছাড়াই, পুরনো বইখাতা সহজেই যোগাড় হয়ে যেত। আবার বিভিন্ন ক্লাব, সোসাইটি অনুষ্ঠান করে দরিদ্র মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষার ফলের ভিত্তিতে উৎসাহিত করে নতুন ক্লাসের পাঠ্যপুস্তক হাতে তুলে দিত। বউবাজারের শ্রীনাথ পাঠাগার ও মুচিপাড়া এলাকার শান্তি ইন্সটিটিউটে ওইরকম অনুষ্ঠানে প্রতি বছর যেতাম। হাইস্কুলেও পড়াশোনার মান ছিল ভাল, নির্দিষ্ট শিক্ষকের উপস্থিতিতে যেকোনো শিক্ষক, এমনকি হেডমাস্টারও চলে আসতেন ক্লাস নিতে, প্রাইভেট ট্যুইশনের প্রয়োজন হত না। হিন্দু-হেয়ার-বেথুন-সংস্কৃত ছিল ভাল ছেলেমেয়েদের স্বপ্নের স্কুল, তবে বউবাজার ট্রেনিং স্কুলের হাইবেঞ্চে কান ধরে দাঁড়িয়ে, মেট্রোপলিটানের হেডমাস্টার নকুল রায়ের বেতের বাড়ি খেয়ে ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হয়েছে, গবেষণার কাজে বিদেশে গেছে, এমন কৃতী বাঙালের সংখ্যা কিন্তু নেহাত কম ছিল না। “পড়ব কিম্বা মরব” সংকল্প নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও হতদরিদ্র বহু মেধাবী উদ্বাস্তু যুবককে উজ্জীবিত করে সফলতার শীর্ষে নিয়ে গেছে, তাদের সাফল্য আজও ওই পরিবারের উত্তরসূরিদের কাছে দৃষ্টান্তমূলক প্রেরণার জীবন্ত দলিল হয়ে আছে।
৪
আহার ও আশ্রয় ছাড়াও আরো একটা জিনিসের অভাব খুব বোধ হতে লাগল সময়ের প্রভাবে, ফেলে আসা সমাজ জীবনের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, লোকাচারকে মরিয়া হয়ে খুঁজতে লাগলেন সব শ্রেণীর মানুষজন। সকলেরই তো কিছু না কিছু ছিল, যা হারিয়ে গেলে জীবনের ছন্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। ভিটেমাটি হারানোর শোক একটু ফিকে হতে লাগল যেই, হারিয়ে যাওয়া জীবনের অন্যান্য রসদের তাগিদ অনুভূত হতে লাগল বেশি করে। কথায় আছে না, “খেতে পেলে শুতে চায়…”, বাঙালদের হল তাই – এবার এটা চাই ওটা চাই করে কলতান উঠল PL ক্যাম্পের এখানে সেখানে, এ ক্যাম্প থেকে সে ক্যাম্পে, ক্যাম্প থেকে ছড়িয়ে পড়ল চাহিদার বার্তা পরিচিতদের ছড়ানো ছেটানো ঠিকানায়।
রিফিউজি ক্যাম্পগুলো মূলতঃ গড়ে উঠেছিল বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী এলাকাসংলগ্ন ২৪ পরগনা, নদীয়া ও মূর্শিদাবাদ জেলার পড়ে থাকা বিস্তীর্ণ খাসজমিতে, যদিও তখনকার কলকাতার মূল ভূখণ্ডের কিছুটা বাইরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকা ছোট পরিসরের খাসজমির দখল চলে এসেছিল উদ্বাস্তু মানুষজনের হাতে। সরকারকে ভর্তুকি দিয়ে ক্যাম্প চালাবার দরকার পড়েনি সে সব এলাকায় – দমদম, উল্টোডাঙার রেলপথের বিস্তীর্ণ দু’পারে, টালিগঞ্জ পেরিয়ে গড়িয়া পর্যন্ত খালপারের দীর্ঘ ভূভাগ ও এইরকম আরো কিছু অঞ্চল, কিন্তু ঘটিরা ওইসব জায়গাকে বাঙালদের জবরদখল ক্যাম্প বলেই চিহ্নিত করতেন। তবে এটা ঠিক যে পরিত্যক্ত ও মালিকানাবিহীন ওইসব জমি নিয়ে কখনো কোনো বিতর্ক সেসময়ে ছিল না, সেখানে শেয়াল ডাকত প্রহরে প্রহরে, ছিল ভুতের ভয় খুব। রাণাঘাট ও ধুবুলিয়াতে ছিল উল্লেখ করার মত কিছু PL ক্যাম্প, ধুবুলিয়ার ক্যাম্পের পরিসর ছিল সবথেকে বড়, এখনকার NH 34 সড়ক বরাবর ধরে কৃষ্ণনগর পেরিয়ে পলাশীর দিকে যেতে ডাঁয়ে বিশাল চত্বর এখনো সেই ক্যাম্পের স্মৃতি বহন করে আছে। সেখানে গড়ে উঠেছিল উদ্বাস্তু পরিবারদের এক বিশাল মেলা প্রাঙ্গণ, ক্যাম্পে ছিল টিনের চাল দেওয়া বড় আকারের অনেকগুলো শেল্টার। ধীরে ধীরে সেগুলির পরিকাঠামো উন্নীত হয়েছিল সাময়িক বসবাসের উপযোগী করার লক্ষ্যে। তড়িঘড়ি করে তোলা “Refugee Relief and Rehabilitation” বিভাগে সরকারী হাতে গোনা কিছু কর্মী থাকতেন ক্যাম্পের পরিচালনার দায়িত্বে, ক্যাম্পে থাকা সকলে পালা করে প্রয়োজনীয় প্রাত্যহিকী সবরকম কাজকর্ম করতেন। gruel কিচেন থাকত আবাস ছাউনি থেকে সামান্য দূরে, দুবেলা খিচুড়ি ছাড়া আর কিছুই বিশেষ পাওয়া যেত না, প্রাতঃকৃত্য সমাধানের জন্য অস্থায়ী স্যানিটারী ব্যাবস্থা থাকলেও ক্যাম্পে বসবাসকারী লোকজনের তুলনায় তা ছিল খুবই নগণ্য। মাঝে মাঝে ঝড়-জলে পরিবেশ হয়ে উঠত বসবাসের অযোগ্য, প্রবীণ ও শিশুদের কষ্ট ছিল সীমাহীন। ক্যাম্পে কোনো স্থায়ী স্বাস্থ্যকেন্দ্র বা ডাক্তার না থাকায় তাদের আপাতকালীন কোনো চিকিৎসা সম্ভব ছিল না। বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াকেই শীর্ণ চেহারার ধুঁকতে থাকা অতি-বৃদ্ধেরা শ্রেয় মনে করতেন, অপুষ্টিতে রিকেটি চেহারার শিশুদের দেখলেই আকালের আভাস উপলব্ধ হত, অন্তঃসত্তা রমণীর দু’বেলা খাওয়া খিচুড়ির খাদ্যগুণেই পুষ্ট হতে থাকল গর্ভে থাকা আগামীর স্বপ্ন। সরকারী চিকিৎসক আসতেন বটে কিন্তু অনিয়মিত, রোগ ও রোগী উভয়কেই অন্তহীন প্রতীক্ষা করতে হত অচেতন ঘোরের মধ্যে থেকে। কিশোরী থেকে যুবতীতে সদ্য রূপান্তরের সদর্প ঘোষণা প্রস্ফুটিত হয়ে থাকত ছিন্ন পোষাকের ফাঁকফোকরে, মায়ের শাণিত দৃষ্টি আগলে রাখত চতুর্দিকের লোলুপ অজস্র চাউনি থেকে লজ্জাকে আড়াল করতে। স্কুল-কলেজের ঠিকানা ছিল না ধারেকাছে, তবুও মুখে মুখে চলত ছন্দে গাথা অক্ষর – পরিচয়ের স্বরলিপি, “অ-এ অজগর আসছে তেড়ে…” আর ধারাপাতের “একে চন্দ্র দুয়ে পক্ষ…”। পড়ন্ত বিকালের শেষে, দুই প্রজন্ম মুখোমুখি বসে, আঁধার আরো একটু ঘন হলে শব্দ ও ছন্দের পালাবদল ঘটে পরিবেশ মুখরিত হত “হরে কৃষ্ণ…” ধ্বনিতে, কুপির মিটমিটে আলোতে, করতালের সুরঝঙ্কারে, হরিধ্বনি-উলুধ্বনির মূর্চ্ছনায় আর খিচুড়ির ভেসে আসা গন্ধে রাতের আগমনবার্তা সূচীত হত আরেকটা ভোরের অপেক্ষায় – বাঙাল কিছুতেই মরে না, মরতে চায়ও না। একটু বড় হয়ে, বাঙালদের ব্যাবসা ও প্রতিপত্তির শ্রীবৃদ্ধিতে হতাশ বীরভূমের এক সহপাঠীর মুখে শুনেছিলাম সুন্দর একটা প্রতিপাদ্য, “শালা বাঙালরা ভাই কিছুতেই মরে না, শ্যাওলার জাত শালা, এই দেখবি বৈশাখে শুকিয়ে মরে পড়ে আছে, মানুষের পায়ের চাপে মাটিতে ধুলো হয়ে গেল, ধুত্তেরি! আবার বর্ষার জল পেলেই সবুজ রঙ গাঢ় হতে থাকে…”। জানিনা এটা শুনে টিকটিকি তিনবার ডাকত কিনা, কিন্তু কথাটা ভয়ঙ্করভাবে সত্যি।
ভাইবোনদের সংখ্যাবৃদ্ধি ও আরো কিছু অসুবিধার কারণে ১৩ নম্বর জেলেপাড়ার দোতলার ঘর ছেড়ে ৪৭ নম্বর বাঞ্ছারাম অক্রূর লেন-এর একতলায় দু’কামরার বাড়িতে চলে আসতে হল, মালপত্তর তেমন কিছুই ছিল না। ঠাকুরদা ও ঠাকুমা যেখানে মারা গেছিলেন, সেখানে দুটো লম্বা লোহার পেরেক পোঁতা ছিল কেন জানিনা। আসার সময় পেরেক দুটো কপালে স্পর্শ করে বাবা ডুকরে কেঁদে উঠলেন দেখলাম। একতলার দুই কাকিমা, জ্যেঠিমা ক্রন্দনরত মা’কে চাপা গলায় বললেন, “চিন্তা কোরো না বউমা, পাশেই থাকবে, যেমনটি আমরা ছিলাম তেমনটিই থাকতে পারব।” বুঝতে অসুবিধা হল না, ডাল-তরকারির বাটি ও রাধেশ্যামের প্রসাদের থালা যথাপূর্বং চলাফেরা করবে। আসলে অবিশ্বাস্য শোনালেও, দুটো বাড়ির দূরত্ব ছিল একটা জায়গায় চার থেকে পাঁচ ফুট, আমাদের ঘর থেকে বাড়িওয়ালার লম্বা করিডর পেরিয়ে সোজা একটা সরু গলির সামনে এলেই পৌঁছে যেতাম একতলার কাকিমার জাল লাগানো দুটো জানলাতে। কাকাবাবুও মাঝে মাঝে ডেকে দাদাকে লম্বা লম্বা বিদ্ঘুটে সাইজের কালো কালির দাগ লাগা কাগজ দিতেন খাতা বানিয়ে লেখার জন্য, উনি তরুণ প্রেসে প্রুফরিডার ছিলেন, নিজের সন্তানদের লেখাপড়ার সাথে সাথে দাদার খেয়ালও রাখতেন। আর দাদা ছিল মেট্রোপলিটানের ক্লাস টেনের ফার্স্ট বয় – এলাকার কাউন্সিলার, কংগ্রেস-কম্যুনিস্ট নেতা, তেলেভাজার দোকানের উড়িয়া ঠাকুর, ছোটবড় সবাই, বিশেষ করে জোব চার্ণকের কলকাতার আদি বাসিন্দা জেলেপাড়ার কৈবর্ত সম্প্রদায়ের চোখের মণি ছিল দাদা। হাফপ্যান্টের সাথে র্যাশনের দোকান থেকে কেনা ছিটের জামা, পায়ে সাইকেলের টায়ার দিয়ে তৈরি চটি, সকাল সাতটা থেকে প্রাইভেট ট্যুইশন করে ছুটত এপাড়া-সেপাড়া। বাড়ি ফিরে গরম ভাতের সাথে কুমড়ো-আলু দিয়ে সেদ্ধ ডালে কাঁচা তেল দিয়ে মেখে খেয়ে সোজা স্কুল, চারিদিক থেকে শুধু প্রাইজ আনত ঘরে – রুপোর কাপ, পেন, বই – কতকিছু। প্রতি রবিবার সকালে সামনের বাড়ির রোয়াকে বসে বহু ক্লাস নাইন-টেনের ছাত্রকে পড়াশোনাতে প্রয়োজনীয় সাহায্য করত, টেস্টপেপার একপাশে খোলাই থাকত দেখতাম। নতুন বাড়িতে এসে আরো কাছের হল দীনবন্ধু, দীনুদা বলে পাড়ার সবাই ডাকত, আমরাও ডাকতাম, আর তার স্ত্রীকে সবাই বউ বলে সম্বোধন করতাম। সদর দরজার পাশেই ছিল ঠাকুর-দেবতার ছবিতে ঢাকা ঘরটা, ওই বাড়িতেই তাদের পাঁচ-ছটা গোরু নিয়ে একটা খাটাল ছিল। বউ তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখত কে কখন ঢুকছি বেরোচ্ছি, ঢোকা ও বেরনোতে অসঙ্গতি বা সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লে বাবাকে তা জানিয়ে দিত দীনুদা। আর দোতলায় থাকতেন যে দাদা-বৌদি, তাঁরা আপন সন্তানের মতই স্নেহ দিয়ে আগলে রাখতেন আমাদের সবাইকে। সন্ধ্যা হলে বইখাতা নিয়ে চলে যেতাম তাদের একটা ফাঁকা ঘরে, প্রয়োজনে সাহায্য করতেন দাদা হোমওয়ার্ক শেষ করতেন। ফেরার সময় প্রতিদিন দেখতাম দীনুদা আর বউ ঢাকাই পরোটা খাচ্ছে মচমচ শব্দ করে ভেঙে, বেশ মজা লাগত আমার ওই দৃশ্য দেখতে। বাবা সকাল-বিকাল অফিস নিয়ে ব্যাস্ত থাকতেন, কিন্তু বাড়ি ফিরে হাত-মুখ ধুয়ে চা-মুড়ি খেয়ে ডাক দিতেন সবাইকে। যে যার বই, খাতা, স্লেট, পেন্সিল নিয়ে বাবাকে সামনে রেখে অর্ধচন্দ্রাকারে বসে যেতাম। পালা করে পড়া ধরতেন, টাস্ক দেখতেন, কিন্তু পড়া না হওয়া পর্যন্ত রাত্রের আহার জুটত না। যত রাতই হোক না কেন অথবা আলো নিভে যাক না কেন, যতই দীর্ঘ হাই তুলতাম না কেন আমরা, ক্ষমা ছিল না। ছুটির দিনে বাবা খুব সস্তায় সব্জি বাজার করতেন কোলে মার্কেট থেকে, দু-তিন ভাই মিলে যেতাম বাবা’র সাথে সব্জি বয়ে নিয়ে আসার জন্য। মাসের প্রথমে একবার জানবাজারে যেতাম মুদি বাজার করতে, দূরে বসে থাকা চেনা দোকানী একটা কাঠের বারকোষের ওপর চারমিনার আর দেশলাইয়ের বাক্সটা রেখে ঠেলে দিতেন ডাল-মশলার টিনের ওপর দিয়ে, বাবা বেঞ্চে বসে সুখটান দিতে দিতে ফর্দ আউড়ে যেতেন। মা ছিলেন সংসারের বাকি সব দায়িত্ব সামলাবার জন্য, একবার শুনলেই মনে রাখতেন কার কী জরুরি দরকার। দাদার ম্যাট্রিক পরীক্ষার আগে মা একটা চিরকুট লিখে বীরেনদার র্যাশনের দোকানে নিয়ে যেতে বললেন, বীরেনদার কথামত পরদিন সকালে গিয়ে একঝোলা খুচরো আধুলি, সিকি বয়ে এনে মা’কে দিলাম। সেদিন ছিল দাদার ম্যাট্রিক পরীক্ষার ফর্ম ফিল আপের শেষদিন। উদ্বাস্তু জীবনের প্রবাহে সব বাধা ছিল বালির বাঁধের মত, বাঁকের মুখে ভেঙে যেত বারে বারে।
সেই যে, খেতে পেলে শুতে চাওয়া বাঙালের দল! কিছু একটা জীবিকার সন্ধান পেলেই এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে যেতে লাগল সবাই ক্যাম্পের গ্লানিময় জীবন থেকে মুক্তি পেতে, কিন্তু তাদের আত্মিক বন্ধন অটুট থাকত সেসময়ে। পরবর্তী সময়ে সভাসমিতি তৈরি করে আলোচনা করতেন, কিভাবে নতুন বাংলায় পুরনোকে সাজিয়ে রাখা যায়, তার কল্পিত রূপরেখা নির্ধারণ করতে। আমাদের বাড়ি ছিল যশোর জেলার নড়াইল মহকুমার ‘কালিয়া-বেন্দা’ গ্রামে, দুটি ভিন্ন হলেও যমজ বোনের মত ছিল গ্রাম দুটি, একটাকে বাদ দিয়ে অন্যটার অস্তিত্ব ভাবা যেত না, মামাবাড়ি ছিল খুলনা জেলার সেনহাটি গ্রামে। কোনো এক রবিবারে কালিয়া-বেন্দা সম্মেলনে বাবার হাত ধরে পৌঁছে যেতাম ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউট হলে, মনে হল নিজের কারো বিয়ের অনুষ্ঠানে এসেছি, হইচই আর কিছুতেই থামে না। হাতে একটা বড় সাইজের ছাপা বই এল, গ্রামের পরিবার-সমূহের বংশপঞ্জি, আরো অবাক হলাম দাদু’র নাম থেকে নিচে নামা পংক্তির শেষের আমাদের ভাইদেরও ছাপা নাম দেখে। বিরাট আকারের একটা বাতাসা আর ছোটবড় অনেক মিষ্টি খেয়ে, ফ্যামিলি ট্রীয়ের বইটাকে বগলদাবা করে বাড়ি ফিরলাম। পরে শুনেছিলাম বেহালাতে ‘চ্যাটার্জ্জী কলোনি’ ও তার অনতিদূরে ‘সেনহাটি কলোনি’ গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। পরিণত বয়েসে ওইসব স্মৃতিবিজড়িত পুনঃস্থাপিত সাধের এলাকা ঘুরে এসেছিলাম বিভিন্ন পারিবারিক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। হাবড়াতে সরকারী বাসস্থান গড়ে উঠেছিল ‘স্কীম ওয়ান,’ ‘স্কীম টু,’ এইভাবে। নিজেদের গ্রামের স্মৃতিরক্ষার চেষ্টা করেও ধরে রাখতে পারেনি পুনর্বাসিত PL ক্যাম্পের লোকজন, তবে কলকাতা ও শহরতলির নতুন এলাকা ফেলে আসা স্মৃতিফলকে গড়ে উঠেছে। গ্রামের দূর্গাপুজো কলকাতায় নতুন করে শুরু করার সংকল্পে বাবাকে দেখতাম এখানে ওখানে কাকা, জ্যাঠাদের বাড়িতে যেতে। তখন ছেলে-মেয়ের বৈবাহিক প্রস্তাবে গ্রাম ও পরিবারের কর্তার নামই যথেষ্ট ছিল, আমন্ত্রণ-পত্রেও তার উল্লেখ অল্প কিছুদিন আগেও দেখেছিলাম। ধীরে ধীরে চাষবাস, ব্যাবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, সাহিত্য, নাটক, সিনেমা, শিল্পকলা, সর্বক্ষেত্রেই প্রবেশ ঘটিয়ে বাঙাল পায়ের নীচে মাটি শক্ত হতে শুরু করল “উড়ে এসে জুড়ে বসে,” খুব শোনা এই আওয়াজকে নিঃশব্দে হজম করে। কিন্তু যে যাই হল না কেন, সবাই কিন্তু ‘বাঙাল’ হয়েই থাকা পছন্দ করল। অবস্থান মর্যাদায় আমরা খুব একটা ভাল বাঙাল ছিলাম না, বিক্রমপুরের মেয়ে আমার জ্যেঠিমা আমাদের বলতেন, “তোরা আবার বাঙাল হইলি ক্যামনে? তোরা তো ট্যাঁশ!” অর্থাৎ ভারতের সীমান্তবর্তী যশোর জেলার মানুষকে বাংলাদেশের বাকি জেলার অধিবাসীরা ‘খাঁটি বাঙাল’ বলে মেনে নিতে পারতেন না। সেদিন খুব কষ্ট হয়েছিল জ্যেঠিমার কথা শুনে।
দাদা প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করাতে খুব একটা অবাক হল না কেউ, আর.জি.কর মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল এসে বাবার সাথে কথা বলে সেখানে বিনা বেতনে M.B.B.S. পড়ার উদ্দেশ্যে দাদাকে ভর্তি করে দিলেন তাঁর ছেলের সাথে, সে দাদার সহপাঠী ছিল মেট্রোপলিটান স্কুলে। কিন্তু আর.জি.কর থেকেও উদ্বাস্তু হতে হল দাদাকে, সেকেণ্ড ইয়ারে উঠতেই ভদ্রলোক হৃদরোগে মারা গেলেন, বিনা বেতনের সুপারিশের ওপর ভরসা রাখা গেলনা, I.S.C. ওখান থেকেই হয়ে গেল প্রথম বিভাগে। B.Sc.-তে ভর্তি হয়ে আর্থিক দায়িত্বের বোঝা তার মাথায় চেপে বসল, ট্যুইশনের সংখ্যা গেল বেড়ে, কলেজ থেকে দু-তিনটে ট্যুইশন সেরে বাড়ি ফিরতে রাত দশটা বেজে যেত। বাড়িওয়ালা ইলেক্ট্রিকের মেইন সুইচ বন্ধ করে দিতে লাগলেন ঠিক রাত দশটায়, কারণ দাদা রাত জেগে পড়াশোনা করত। সব পরীক্ষার আগে দাদার কথামত ইউনিয়ন ফার্মাসিতে গিয়ে রিটেইলিন কিম্বা মেথিডিন নামের খুদে খুদে ট্যাবলেট কিনে আনতাম। দাদা সাথে করে আমাকে দোকানে নিয়ে গিয়ে সব বলে এসেছিল, কোনো অসুবিধা হত না কখনো। তাই খেয়ে দাদা রাত জেগে পড়ত, সারাদিনের হাড়ভাঙা খাটুনিতে খুব ঘুম পেত ওর। তারপর থেকে পড়ার ঠিকানা হয়ে গেল ওয়েলিংটন স্কোয়্যারের মাঝখানে জোরালো আলোর নীচে কাঠের বেঞ্চে, চারিপাশে মুটিয়া-মজদুরেরা গামছা পেতে ঘুমোতেন, তারা ঘুমোতে যাবার আগে গামছা দিয়ে বেঞ্চটা ভাল করে ঝেড়ে রেখে দিতেন। বৃষ্টি পড়লে শুনেছি তারাই দাদার বইখাতা নিয়ে দৌড়ে যেতেন পার্কের ক্রিক রো-য়ের দিকের কোণে গোল সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো আচ্ছাদিত চত্বরে, ঠিক ওখানেই ছিল মস্ত একটা কদম গাছ, আর বর্ষাতেই গাছ ভরে থাকত কদম ফুলে। আমার শৈশব কতবার যে ওখানে হারিয়ে গেছে, কে জানে! ঠিক ওই সময়েই বাবা চলে গেলেন সামান্য কয়েক মাস পেপ্টিক আলসারে ভুগে, দাদার আরো একটা অগ্নিপরীক্ষা ছিল বাবাকে বাঁচানোর অসামান্য প্রয়াস – ন্যাশনাল হসপিটাল, ব্লাডব্যাঙ্ক, ব্যার্থ সার্জারি, আবার তিরিশ বোতল রক্ত, আইস প্যাকিংয়ে ঢাকা শরীর, সব শেষে শ্মশানযাত্রা ও পারলৌকিক কাজ। উইপোকাতে কাটা বাবা’র একটা ফ্রেমে বন্দি ছবি আছে এখনো আমাদের বাড়িতে আরো অনেক বাড়ির মত সযত্নে টাঙানো, বাবার তেতাল্লিশ বছরের জীবনের একমাত্র ছবি – শ্মশানে সস্তা খাটে সাদা চাদরে ঢাকা, চিরনিদ্রায়, পাশে দাদা বসে, কয়েক মাসের কঠিন লড়াইয়ে ক্লান্ত, শ্রান্ত, অবসন্ন চেহারা, দুটি চোখ যেন আগামীর চিন্তাতে মগ্ন।
জেলেপাড়ার কাকাবাবু, কাকিমা-জ্যেঠিমা, নতুন বাড়ির দীনুদা, দোতলার দাদা-বৌদি, র্যাশনের দোকানের বীরেনদা, আর.জি.করের সেই প্রিন্সিপাল, ওয়েলিংটন স্কোয়্যারের খেটে খাওয়া মুটে-মজদুরের দল, আমার দাদা – কেউ এরা বিচ্ছিন্ন কোনো চরিত্র নয় – মানুষের বাঁচার লড়াইয়ে সবাই এরা এক একটা প্রতীক মাত্র। দেশভাগের পর সেই উদ্বাস্তু মিছিলের সাথে শতসহস্র এরকম চরিত্র কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে পায়ে পায়ে পথ চলেছে নতুন ঠিকানার খোঁজে, কত কান্না, কত আর্তনাদ, কত ব্যাথা, কত লজ্জা, কত ভয়, কত শোক, কালের প্রভাবে বাতাসে বিলীন হয়ে গেছে সেই পথ চলায়। ছিন্নমূল মানুষের লড়াই শেষ হয়না কখনো, শুধু লড়াইয়ের ময়দান পরিবর্তিত হয় মাত্র।
শ্মশান থেকে আমার দাদার যাত্রা আবার তাই নতুন পথে শুরু হয়েছিল, সাদা থান আর কঙ্কালসার চেহারার মা’কে পাশে নিয়ে, পরিবারের আটজন প্রাণীর সব যোগান অব্যাহত রেখে। B.Sc., লোয়ার ডিভিশান ক্লার্কের চাকরি, W.B.C.S., বীরভূমের গ্রামে গ্রামে বৈপ্লবিক হাই-ইল্ডিং ধানচাষের রূপকার, “তাইচূন সাহেব,” আমেরিকাতে চাষবাসের বিশেষ শিক্ষা এবং কোনো একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের খুব উঁচু পদ থেকে অবসর ছিল সেই পথের আরেক বাঁকে পৌঁছে যাওয়া। না, অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানেই শেষ হলনা বাঙালদের সংগ্রামের ঠিকানা, অবসরের বেশ কিছু সময় পর ষাটোর্ধ বয়সে অর্থনীতির জটিল একটা বিষয়ে গবেষণা করে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আচার্য্য, রাজ্যপালের হাত থেকে Ph.D-র দলিলখানি নিলেন ও সেই ঐতিহাসিক দৃশ্যের ফোটোর পেছনে লিখলেন, “Sky may not be your limit,” আর পাঠিয়ে দিলেন ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পরিবারের এই প্রজন্মের উত্তরসূরি প্রত্যেকের কাছে, কেউ বাদ পড়েনি।
পঁচাত্তরে পদার্পণের লগ্নে পৌঁছে আজও সেই উদ্বাস্তু যুবক সমানে লড়াই করিয়া চলিতেছে নিত্যনতুন রণাঙ্গনে, শুধুমাত্র প্রমাণ করিতে যে, “বাঙাল মরিয়াও মরে নাই।”
(চলবে)


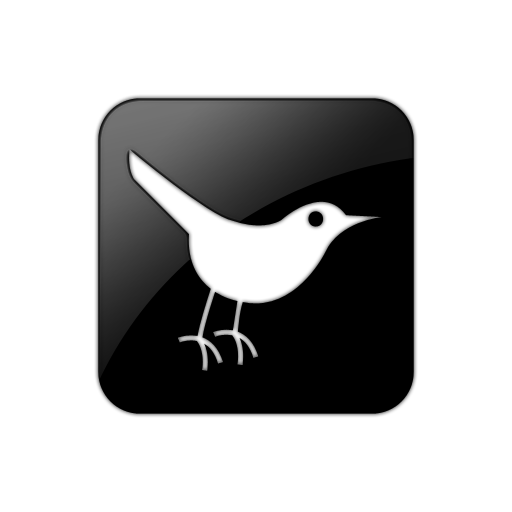
Sutapa Sen said
asambhab sundar lekha…pratiti akhkhar bastab…ei lekhar jano aro anek pai…
Aranya Lahiri said
Tothyonistho othocho prosadgune bhorpur , agagora jhorjhore ekta mormosporshi lekha. Amar babar mukhe sona amar udbashtu pitamoher kolkatar jibon songramer kahinir sathe onek mil khunje peye chomotkrito holam. “PoRbo kimba morbo ” ei kothata je ninmodhyobitto udbastu bangal-jibone koto boro songramer hatiyar hoye uthechhilo seta lekhoker boyeshi protiti bangal-i harRe haRe janen. Osadharon ! Lekhok ke kurnish janai.
Tithi said
Jibon samparke notun kore vabte sekhalo ei lekha…sotti.. pore mone hai amader doinondin jiboner kato chhoto chhoto samosya ke amra kato baro kore vabi..jibon sangram-er ei bastob chitra chokhe angul diye dekhiye dei je – ei sangramer kachhe amader ei chhoto chhoto samosya gulo kato nagonno..
parer sankhya-r jonno utsuk roilam..
Trisha said
Amader sekorer khoje porte bosechilam, porte porte chokhe jol elo, sotti ekei bole bacha. ki bhalo lekha Rabida, anek aenk avinandan. Aro porte chai.
Balaka
বাঙালনামা said
বাঙালনামার পক্ষ থেকে দেশভাগের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বা oral history সংগ্রহ করার একটা উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আপনাদের অনুরোধ, আপনারা এতে অংশ নিন। আপনাদের পরিবার পরিজনদের জবানবন্দী লিখিত ভাবে, মৌখিক ভাবে, তথ্যচিত্রের আকারে আমরা সংরক্ষণ করতে চাই। বিস্তারিত জানতে দয়া করে ইমেলে যোগাযোগ করুন – bangalnama@gmail.com।
deepak bose said
ghum theke uthe lekha t pore choke jol ashe galo . darun
monalisa debnath said
“bangalra moriyao more nai…” otyonto sohoj o sadharon kore lekha kintu awsadharon.. mon chhuye jay
Maniparna Sengupta Majumder said
অসম্ভব সুন্দর একটা লেখা… !
অমৃতা ঘোষাল said
এই জীবনটা আমরা পাইনি। পেয়েছিলেন ঠাকুরমা-ঠাকুরদা আর তাদের সেই আগলে রাখা পরিবার। ঠাম্মার মুখে এই কথাগুলো শুনছি প্রায় পাঁচ বছর বয়স থেকেই। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলো যেন তীব্র থেকে তীব্রতম ঠেকতে থাকে। এগুলো সত্যি। নির্মম সত্যি। আপনার লেখাটি পড়ে আবার শিহরিত হলাম।