তেভাগা – দিশা ও উত্তরাধিকার
Posted by bangalnama on June 1, 2010
– লিখেছেন তপন বন্দ্যোপাধ্যায়।
যুক্ত বঙ্গে তেভাগার আন্দোলন ও সংগ্রাম ছিল অনস্বীকার্যভাবে ঔপনিবেশিক ভারতের সর্ববৃহৎ কৃষক সংগ্রাম। শুধুমাত্র কৃষকদের সংগঠিত, ব্যাপক অংশগ্রহণের জন্যেই নয়, পরন্তু, একই সঙ্গে এই আন্দোলন সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা ও ঔপনিবেশিক শাসনের ঝুঁটি ধরে নাড়া দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বহু যত্নে লালিত নানা সামাজিক সংস্কার, বিকৃতি এবং আজন্মচারিত মানসিক ব্যাধির উপসর্গগুলোকেও, অন্ততঃ কিছুটা হলেও, ঘর ছাড়া হতে বাধ্য করেছিল। নানাভাবে, নানাদিক থেকে তেভাগার সংগ্রামকে দেখা হয়েছে, ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তার বেশিরভাগই মূল্যবান সঞ্চয়।
কিন্তু ইতিহাস থেকে নতুন করে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয় বারবার, অদ্যতন বর্তমানকে বোঝার জন্য তো বটেই, নতুন দিশা এবং উত্তরাধিকারের খোঁজেও।
শুরুর শুরু
১৯২৮ সালে ‘বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইন’ সংশোধিত হয়, প্রধানতঃ গরহাজিরি জমিদারতন্ত্রের প্রবল চাপ ও কংগ্রেস এবং ইংরেজ শাসক – উভয়কেই আনুগত্যদানের শর্তে। এর ফলে ধনী কৃষক ও জোতদার শ্রেণী আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৯২১-৩২ কালপর্বে কৃষক ও ক্ষেতমজুরের সংখ্যা বিগত তিন দশকের থেকে দ্বিগুণিত হয়, আর পরবর্তী পাঁচ-ছয় বছরে তা আরো বেড়ে যায়। আসল কারণ ছিল প্রজাস্বত্ব আইনের দাখিল খারিজ ফি’র স্থিরতা এবং ভূসম্পত্তি কেনার পরও অধিকারের (হাল-হকিকত) স্বীকৃতি না পাওয়ার অবসান। মনে রাখা দরকার এটা বিশ্বব্যাপী আর্থিক মন্দা ও বাজারি ধ্বসের সময়। এ সময়ে ধনবান চাষীদের মধ্যে জমি কেনার হিড়িক পড়ে যায়। ফলে গরীব চাষী – গরিবতর হল – এর বেশিরভাগই ভূমিহীন হতে বাধ্য হল।১
লিখিত ও জানিত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন দেখি না। যেটা বলার দরকার আছে সেটা হল তদানীন্তন কংগ্রেস, ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা পার্টি ও বিংশ শতাব্দীর মধ্য তিরিশের দশক থেকে মূলতঃ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত কৃষক সভার কথা। ১৯৩৬ সালে জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে জওহরলাল নেহরু সভাপতির ভাষণ দেন। যেটা উল্লেখযোগ্য, সেই প্রথম কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে সরাসরি ‘সোশ্যালিজম’-এর কথা শোনা গেল। প্রসঙ্গত বলে রাখি যে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ‘সমাজতন্ত্রী’ একটা গোষ্ঠী তখন কাজ করতে শুরু করেছে। আচার্য্য নরেন্দ্র দেবের উৎসাহে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত নেহরুর বক্তৃতাটির মুসাবিদা করে দিয়েছিলেন।২
১৯৩৬ সালের ১২ এপ্রিল লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস চলাকালীন স্বামী সহজানন্দ সরস্বতীর সভাপতিত্বে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় – লক্ষ্য ঃ কৃষক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াস। সংগঠনের নাম রাখা হয় ‘কৃষক কংগ্রেস।’ ওই বছরই কলকাতার অ্যালবার্ট হলে (বর্তমান কফি হাউস) কুড়িটি জেলার প্রতিনিধিদের সম্মেলন থেকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার পত্তন হয়। উল্লেখ্য হল যে ওই সম্মেলনে দু’শো প্রতিনিধি এসেছিলেন যাঁদের বেশিরভাগ এখনকার বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত; সভাপতিত্ব করেছিলেন মুজফফর আহমেদ। এর পরের বাৎসরিক অধিবেশন বসে বাঁকুড়ার পাত্রসায়র-এ।
বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষকসভার মূল লক্ষ্য ও দাবী ছিল ঃ (ক) ক্ষতিপূরণ ছাড়াই জমিদারী প্রথা বিলোপ, (খ) মহাজনী ঋণ সর্বাংশে মকুব, (গ) গ্রামীণ মানুষের মধ্যে নিঃশর্ত জমি (উদ্ধারকৃত এবং সরকারের হাতে আসা) বন্টন, (ঘ) দ্রুত ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান এবং জনগণের হাতে ক্ষমতা প্রত্যার্পণ, ইত্যাদি। কৃষকসভার এই প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধানতঃ গরীব চাষী, ভাগচাষী, টংক ও মাঝারি চাষীর কিছু অংশ এবং ধনী চাষীদের একটা ক্ষুদ্র অংশ প্রভাবিত হয়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক সমাজেও বিত্তের দ্বান্দ্বিক চেহারাটা ফুটে উঠেছিল — মাঝারি চাষী ও ধনী চাষীদের (ক্ষুদ্র অংশ হলেও) যোগদান এটাই প্রমাণ করছিল। জমিদাররা যে সকল ক্ষমতার উৎস – গ্রামীণ সমাজে এটা সুপরিস্ফূট ছিল বেগার, আবোয়াব, দাখিল খারিজ কি দাখিল ও যথেচ্ছ খাজনা বৃদ্ধি, হাটতোলা, ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে। মধ্য ও একটু উচ্চবিত্ত জোতদার বা ধনী চাষী এগুলোর উচ্ছেদ চাইত, কিন্তু জমিদারতন্ত্রের অবসান ব্যতিরেকেই।৩
অপরদিকে (প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গের জেলাগুলোতে) জমিদার, লাটদার, ধনী ও বিত্তশালী মাঝারি কৃষক – ফজলুল হকের নেতৃত্বে গঠিত কৃষক-প্রজা পার্টির মধ্যে সংগঠিত হয়। এদের মূল লক্ষ্য ছিল জমিদারী শাসন-শোষণকে খানিকটা সহনীয় করে তোলা।৪
ফজলুল হক মন্ত্রীসভা বিলেত থেকে স্যার ফ্রান্সিস ফ্লাউডকে চেয়ারম্যান করে বাংলার ভূমি ব্যবস্থা সম্পর্কে এক তদন্ত কমিটি গঠন করে। ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা গেল যে তখন (১৯৪০ সাল) জমিদারী মহাল ছিল ১,০২,৮২৫, যার মধ্যে ৯৪,২৩০ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তাধীন, অস্থায়ী ছিল ৪,০৫৮ আর সরকারী খাস-তালুক ৪,৫৩৭টি। এই সব মহাল থেকে রাজস্ব খাতে আদায় হত ৩,১৬,৮৮,৪০৮ টাকা, চাষীদের থেকে জমির খাজনা বাবদ ১৭,৩১,০৫,৫৩২ টাকা, এবং সেস্ আদায় ছিল আরো ৯,৫৪,২১,৯৪২ টাকা।
এই সময়ে অকৃষক জমির মালিক ৫২,১৯,৫০০, রায়ত ও অধীনস্থ রায়ত ৮৮,৭৭,৭৫০, বর্গাদার ৩৭,৭৮,০০০ ও ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ৬৬,৩৭,২০০ (আদমসুমারী ১৯৪১)।
উপর্যুক্ত পরিসংখ্যানের প্রেক্ষাপটে দেখা যেতে পারে তেভাগা আন্দোলনের তাৎপর্য্য ও তার পরবর্তী বিকাশ ও উত্তরাধিকারকে।
“হরিকান্ত সরকার, ফকরুদ্দিন চাটি মহম্মদ, কালাচাঁদ, দীনদয়াল আজও বেঁচে আছেন কিনা জানিনা। বেঁচে থাকলে কি নিয়ে আছেন তাও জিজ্ঞাস্য। একটি দু’টি কিংবা দশ-বিশটি গ্রামের মধ্যেই তাঁদের কর্মক্ষেত্র সীমিত ছিল, নিজেদের অপরিসর মাটিকে আঁকড়ে ছিলেন মহীরুহের মত। মাটির গভীরে যে শিকড় চালিয়েছিলেন তা তাঁদের কঠিন সংগ্রামে অশেষ রসসিঞ্চন করেছে, তেভাগার দ্বিতীয় পর্যায়ের রক্তাক্ত সংগ্রামে প্রতিরোধের শক্তি যুগিয়েছে।”৫ এটা ১৯৪৬ সালের শেষদিনগুলোর কথা। এরও অনেক আগে, ১৯৪৩-তে একবার, এমনকি তারও আগে, ঠিক তেভাগা না হোক, জমি/জমির উৎপাদনের ভাগ নিয়ে ছোটখাটো সংগ্রাম হয়ে গিয়েছে যুক্ত বঙ্গে। সেগুলো ছিল ইতিহাস গড়ার সিঁড়ি।
ফ্লাউড কমিশন তার ভূমি, ভূমি-সম্পর্ক ও ভূমি-রাজস্ব সম্পর্কিত কাজকর্ম করে চলছিলেন, তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগেনি বা লাগলেও তার আঁচ আমাদের অবিভক্ত ভারতে এসে পৌঁছয়নি, সে সময়। সেই ১৯৩৯ সালে অনেকাংশে পূর্বতন উত্তরবঙ্গের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে হাটের তোলা বন্ধের জন্য এক লড়াই শুরু হল। এখনকার বাংলাদেশের দিনাজপুর, রংপুর, এপারের দিনাজপুরের জলপাইগুড়ি এমনকি মালদহ জেলা জুড়ে সে এক অভূতপূর্ব উন্মাদনা। সেই আন্দোলন এমন এক শক্তি সঞ্চয় করেছিল যে ছড়িয়ে পড়েছিল ওদিককার ময়মনসিং, যশোর সন্নিহিত চব্বিশ পরগনা জেলাগুলোতেও। এর সঙ্গে সঙ্গে বা কিছু পরেই শুরু হয়ে যায় মেলার ওপর ট্যাক্স বন্ধ আন্দোলন – প্রধানতঃ পূর্ববঙ্গস্থিত উত্তরবঙ্গে।
হাট তোলা বা মেলা ট্যাক্স আসলে ছিল জমিদার বা জোতদারদের অধিকৃত জায়গায় বসা হাটগুলোর ওপর বা পরব, বৎসরান্তিক মেলার ওপর বসানো একপ্রকার ‘তোলা’ বা খাজনা – যেগুলোর কোনো সরকারী হিসেব বা শিলমোহর ছিল না। গরীব চাষী বা ভাগচাষী কে মারবার কায়দা-কানুন সবই তো নথিভুক্ত ছিল না, তবু কতক হিসেব তো পাওয়া যায়ই। যেমন আধিয়ার প্রথা – অর্থাৎ জমির মালিক ফসলের অধিকার আর ভাগচাষী অর্থভাগ পাবে, কিন্তু ব্যাপারটা তো এতটাই সোজা-সরল ছিল না। চাষের খরচ-খরচা, হাল-বলদ সবই চাষীর, সেচের, সারের খরচও চাষীর, তবু অধিকার যা ভাগচাষী পেত – তিনভাগের একভাগ, আর মালিক দু’ভাগ। এছাড়াও মাড়াই বা ক্ষেত-পাহারার খরচ, মাঠে বিড়া (আঁটি) গিনতি, মহুরীর জোহরী, গোলা-পুজা, ছেলে-মেয়ের বিয়ের, কি পালা-পার্বণের মানত, এমনকি পোষা জন্তুর খোরাকি বাবদও তোলা নেওয়া হত এবং সবই ফসলে। কার্যত চাষের শেষে ঋণ-কর্জ না ধরেও আধিয়ারের ঘরে উৎপাদিত ফসলের বেশী হলে একের-তিন থেকে একের-চার ভাগ উঠত, বাকি যেত মালিকের খামারে। উত্তরবঙ্গে এই আন্দোলন ‘আধিয়ার আন্দোলন’ নামে পরিচিত হয়। এখনকার পশ্চিমবঙ্গে একমাত্র মেদিনীপুর জেলার মহিষাদলে এই আন্দোলন খানিকটা দানা বেঁধেছিল। উভয়ক্ষেত্রেই অনেকটাই সাফল্যও অর্জিত হয়েছিল। যদিও মনে রাখবার কথা ফ্লাউড কমিশনের রায় তখনও বেরোয়নি।
ইতিমধ্যে, ময়মনসিং জেলার সুসঙ্গ পরগণায় টংক বিরোধী আন্দোলন এক অভূতপর্ব সাড়া জাগায়। কেননা, অঞ্চল দুরধিগম্য, টংক প্রথা প্রায় সনাতনী এক শোষণ-পদ্ধতি, ওই তল্লাটের বহিরাঞ্চলে এর পরিচিতি জানে এমন ব্যক্তিও বিশেষ ছিল না সেকালে – জমিদারীতে কর্মচারী হিসেবে নিযুক্ত বাঙালীবাবুরা ছাড়া। (অপ্রাসঙ্গিক হলেও বলে রাখি, আমার দাদু দীর্ঘকাল এক রাজাবাহাদুরের সর্ব্বোচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন, ফলে তাঁর কাছে আর আমার বাবা’র কাছেও ছোট ছোট গল্পকথা শুনেছি – সেসব হয়তো উল্লেখযোগ্য নয়, কিন্তু স্মৃতিকে খুঁচিয়ে তোলার শ্রুতি)। টংক বিরোধী আন্দোলন দীর্ঘদিন ধরে চলেছিল শুধু তাই নয়, জমিদারী পাইক-বরকন্দাজ-লেঠেল-হাতি বাহিনী ছাড়াও ইংরেজ পুলিশ-বাহিনীও বছরের পর বছর ধরে অত্যাচার চালিয়ে ছিল টংক-প্রথা বিরোধী আন্দোলনকারী এবং হাজংদের বিরুদ্ধে।
এই প্রসঙ্গে মনে হয় (খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক – কেননা, তেভাগা নিয়ে আলোচনার সময়ে প্রায়শয়ই দেখি যেকোনো একদিকে ঝোঁকা কিছু মত পরিবাহিত হতে – তবু) ত্রিপুরার রিয়াং বিদ্রোহকে একটু ছুঁয়ে না গেলে ১৯৪০-৫০-এর দশকের কৃষক আন্দোলনকে অন্ধের হস্তীদর্শনের মতই বোঝা হয়ে যাবে, নয়তো শুষ্ক তত্ত্বের আড়ালে প্রকৃত তথ্য হারিয়ে যাবে, যেমন হারিয়ে গেছে সরস্বতী, দৃষাদ্বতী বা গঙ্গাহৃদি।
১৯৪৩ সাল, যুদ্ধ তখন আমাদের এই সুপ্রাচীন দেশের ভেতর প্রবেশ করে গেছে, যতটা না সৈন্য-সামন্ত নিয়ে, তার চেয়েও বেশি, ইংরেজী শাসককুলের সমরায়োজনের জন্য বিপুল পরিমান খাদ্য, বস্ত্র, তেল, দেশলাই, ক্যানভাস (ত্রিপল) সংগ্রহের জন্য (এর অনেকটাই তথ্য হিসেবে পাওয়া যায় – যেমন ধান-চাল বা বস্ত্রের হিসেব, বাকী শুনেছি আমার বাবা’র কাছ থেকে, সেই বাল্য যোগসূত্রটা খুঁজে পাইনি – প্রথম চিড়িয়াখানা দর্শনের মত বিচিত্র লাগত, গপ্পো হিসেবে – তখন ভালোই লাগত!) দেশের লোকের খাদ্য-বস্ত্রে টান পড়ল। যারা স্বভাবতই গরীবের থেকেও গরীব, তাদের প্রতিদিনই মর-মর অবস্থা। এই সময়ই ত্রিপুরার রিয়াং উপজাতিরা রাজ-প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তখন ত্রিপুরার সামন্তরাজ ছিলেন বীর বিক্রম মানিক্য বাহাদুর। সে সময় জুমিয়া রিয়াংদের ‘রায়’ ছিলেন নিজেদের সম্প্রদায়ভুক্ত দেব সিং। এই সরল প্রজাতির ব্যক্তিটি সামন্ততান্ত্রিক জুলুম-অত্যাচারের বিরোধী ছিলেন। কারণ যাই হোক — জুলুম-জবরদস্তি করে ফসল ইংরেজ মনিবদের হাতে তুলে দেওয়া অথবা একজন ‘রায়’ (সর্দার) শাসক ও শোষণের হাতিয়ার হতে পারছে না, সেটা সহ্য করতে না পারা। দেব সিংকে সরতে হল, তার জায়গায় স্থলাভিষিক্ত হলেন খগেন্দ্রনাথ রায় – তিনি জোর-জুলুমে সিদ্ধহস্ত। এর ফলে রায় ও তাঁর অনুগামী চৌধুরী – স্থানীয় বিচারকদের ওপর রিয়াং জনতা ও গ্রামের প্রধানরা খাপ্পা হয়ে উঠল। চৌধুরীদের মধ্যে অধিকাংশই নবনিযুক্ত ও খগেনের আত্মীয়-পরিজন, তাই সাহসও বেশি। চৌধুরীরা তাদের নব নব-অত্যাচার-উন্মেষশালিনী-প্রতিভাবলে অচিরেই গ্রামস্থ জনতা এমনকি বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকদের ওপরও অত্যাচার শুরু করল। অত্যাচারের ধরণ ছিল চিরাচরিত এবং বেদবিহিত, যেমন – “স্থানীয় জনসাধারণকে বাধ্যতামূলক ‘বেগার’ খাটানো, গৃহনির্মাণ, বাড়ি পরিষ্কার, প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া গৃহস্থালীর সমস্ত কাজই তাহাদের করিতে হইত।…তাঁহার গ্রামের আশেপাশের আবাদী জমিগুলি হইতে রিয়াং কৃষকদের জোরপূর্বক উচ্ছেদ করিয়া তিনি জমি দখল করিতে আরম্ভ করেন। এইভাবে এক বিরাট জনতা জমি হইতে উচ্ছেদ হইয়া সর্বহারাতে পরিণত হয়।”৬
বর্তমান বাংলাদেশের রাঙ্গামাটি (কুমিল্লা) অঞ্চলে, নোয়াতিয়া উপজাতির উপ-সম্প্রদায়-ভুক্ত রতন মুনি ধর্মের নামে রিয়াং উপজাতিদের মধ্যে নিজের স্থান করে নেন। রতন মুনি সন্ন্যাসীর নেতৃত্বে রিয়াংরা বিদ্রোহ ঘোষণা করল, এবং অনেক চৌধুরীদের ধরল। ফলতঃ ত্রিপুরা-রাজ ইংরেজদের যুদ্ধের জন্য সৈন্যবাহিনী (বলপূর্বক সংগঠিত) পাঠিয়ে, রতনমুনি পরিচালিত এই কৃষক বিদ্রোহ দমন করতে মা-বোনদের গুলি করে মারতেও দ্বিধা করেননি। বীর দাবা রায় ও রতনমুনিকে রাজবাড়িতে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয়।
রিয়াং ও টংক বিদ্রোহের কথা এ জন্যই উঠল যে, তেভাগা বললেই আমাদের মনে একটা রোম্যান্টিক ধারণা স্বপ্নের আকারে ধরা দেয় যে, দিনাজপুর/রংপুর/জলপাইগুড়ি/কাকদ্বীপ এই হচ্ছে কৃষক বিপ্লবের পীঠস্থান। কিন্তু এই ধারণার বশবর্তী হলেই শুধু একদেশদর্শিতায় আক্রান্ত হয় তাই নয়, অবিভক্ত বঙ্গের কৃষক-উত্থানের কাহিনীও পক্ষপাতদুষ্ট হয়। আজ কি হচ্ছে, তাই দিয়ে ইতিহাসের সম্যক ব্যাখ্যা যেমন অনিবার্যভাবে ভুল পথে নিয়ে যায়, তেমনি ইতিহাসের অর্ধব্যাখ্যা বা অর্ধতথ্য ভবিষ্যতের পথ কন্টকিত করে – শুধু কাঁটার জ্বালাই নয়, পছন্দমতো তথ্যটুকু নিয়ে সারসত্য লেখার দায়িত্ব নিয়ে ফেললে লেখকের ভুল সিদ্ধান্ত অপরিমেয় ক্ষতিসাধন করে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে… ইতিহাস গবেষকদের।
প্রশ্ন উঠতেই পারে, ‘তেভাগা’ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এসব বাখানির দরকার কি? আসলে, ইতিহাসে কোনও কালপর্বই ফানুসের মতো হঠাৎ উঠে হঠাৎ ফুরিয়ে যায় না – তার যেমন পর্ব পর্বান্তরে যাত্রা থাকে (কালান্তর আসার আগে), তেমনি তার পর্বচ্ছেদের পরও একটা বহমানতা (চোরাস্রোত হলেও) থেকেই যায়। তেমনি ‘তেভাগা’কে পারম্পর্যহীন একটা ঘটনা ভাবলে বিরাট ভুল হবার সম্ভাবনা, তারই নজির মেলে একই তথ্যের ভুল তাত্ত্বিক ব্যাখ্যায় এবং তার ফলে উদ্ভূত পরবর্তী সমস্যায়। তাই শুরুর এই আদিকান্ডকে ছুঁয়ে যাওয়া।
তেভাগার দান
তেভাগার বিচার্য বিষয় বহুধা বিস্তৃত, সব আলোচনার পরিসর এখানে নেই, অন্ততঃ আমি প্রস্তুত নই, তবু, কয়েকটি দিক না দেখিয়ে আলোচনা শেষ করা যায় না।
এটা সকলেরই জানা, তেভাগা আন্দোলনের পথ বেয়েই এ’দেশে (অর্থাৎ যুক্তবঙ্গে) কতকগুলো ব্যাপার ঘটেছিল যার সুদূরপ্রসারী ফল আমরা, অন্ততঃ এ-বঙ্গে, ভোগ করছি এখনো। প্রথমতঃ বলা যাক আন্দোলনের সামাজিক প্রভাব নিয়ে-
(ক) আজকের দিনে বিভক্ত ভারত ও বিভক্ত পাকিস্তানেও যে সমস্যা সত্যিই উগ্রতম রূপ নিয়েছে, সেই সাম্প্রদায়িকতা কেমন রূপ নিয়েছিল তেভাগার সময় ঃ “একজায়গায় কয়েকজন মুসলমান জোতদার চেষ্টা করলো মুসলমান আধিয়ার আর হিন্দু আধিয়ারদের মধ্যে দাঙ্গা বাধাতে। তাদের বললো- হিন্দু আধিয়াররা যখন ধান কাটতে আসবে, তাদের ঠেকাও, তোমাদের আমরা বেশি ভাগ দেবো। তারা জবাব দিল- ওসবে আমরা নেই, তখন জোতদাররা এক মেলায় গিয়ে মুসলমান ব্যবসায়ীদের বললো- তোমাদের ঘর আমরা পুড়িয়ে দেবো, ক্ষতি যা হবে তাও পূরণ করে দেবো, তোমরা শুধু বলবে হিন্দুরা তোমাদের দোকান পুড়িয়েছে। দোকানীরা করজোড়ে বললো-ওসবে আমরা নেই।”৭
“প্রায় দশটায় রঙপুর পৌঁছুলুম বিকেলে ভোমার বিলে এলুম; আসার পথে দিনাজপুরে কমরেড রূপনারায়ণের (রূপনারায়ণ রায়- ১৯৪৬এ যে তিনজন কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে নির্বাচিত হয়েছিলেন তার অন্যতমই নন, সর্বাধিক ভোটে জেতা কমিউনিস্ট প্রার্থী; অন্যদুজন ছিলেন জ্যোতি বসু ও রতনলাল ব্রাহ্মণ- লেখক) সাথে দেখা। রামপুরে একজায়গায় পুলিশ গিয়েছিল কৃষকের ওপর বীরত্ব ফলাতে, কৃষক-রমণীরাই দিল তাদের ঠেঙিয়ে বেশ ভালো করেই। ”৮
(খ) কৃষক ও অন্তঃপুরচারিণীদের অংশগ্রহণ ঃ সঠিক অবস্থান ও আহ্বান যে নারীকেও পুরুষের সমান আসন নিতে প্রেরণা দেয়- সহস্র বৎসর লালিত সংস্কারকে উপেক্ষা করতে এ তার একটা তুচ্ছ উদাহরন মাত্র (মরিচঝাঁপিতে যাঁরা প্রথম বসতি স্থাপন করতে যান এবং প্রাণ দেন, তাঁদের অনেকেও কিন্তু ছিলেন মহিলা – লেখক)
(গ) আদিবাসী সমাজের বিপুল অংশগ্রহণ। ১৮৮৫’র প্রজাস্বত্ত্ব আইনের পর সাঁওতালদের মধ্যে একটা বিদ্রোহী মনোভাব গড়ে উঠছিল। মূল কারণটা ছিল, জমির মালিকরা এদের দিয়ে জমি চাষ করালেও স্বত্ত্ব দিতনা। দিনাজপুর ও মালদহ জেলার বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে থাকা এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ওপর বিভিন্ন ও উদ্ভট করের বোঝাও চাপানো হতো। যেমন আবোয়ার, ধলতা, গোলাপ পূজা, মাঙ্গল, থিয়েটার, বরকন্দাজী ইত্যাদি। ১৯৩৮ সালে ১৪ দফা দাবীর ভিত্তিতে কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় ও কৃষকসভার সার্বিক অংশগ্রহণে তেভাগার সংগ্রামে সাঁওতালরা বিপুলভাবে যোগদান করে।
সামাজিক অবস্থানহেতু এই জনগোষ্ঠী প্রায় সর্বদাই যূথবদ্ধ জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিল; তেভাগার সময় এই একতা গাঢ়তর ও দৃঢ়তর হয়। এদের মধ্যেও কিন্তু মেয়েরা ছিল অগ্রণী বাহিনী। রানি সরকাইল থানাতে ভান্ডনি বর্মণের নেতৃত্বে সাঁওতাল রমণীরা পুলিশের বন্দুক কেড়ে নেয়, চাঁদের হাটের ইউনিয়ন বোর্ডের অফিসে সারারাত ধরে পুলিশকে আটকে রাখে। চিরির বন্দরে নিজ খিলানে ধান তোলার সংগ্রামে আদিবাসীরা ব্যাপকভাবে অংশ নেয়, শিবরাম ও আমিরুদ্দিন শহীদ হন। ১৯৩৮-৩৯ সালে চিরির বন্দরে জোতদারের হাটের বদলে সাঁওতাল ও রাজবংশীরা নিজেদের হাট বসায়। আরেকজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দিয়ে এ প্রসঙ্গে ইতি টানবো- ‘আন্দোলনের ফলে জোতদাররা ক্ষেপে যায়। এক মাড়োয়ারী জোতদার লোক জোগাড় করার যথেষ্ট চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে নিজেই লাঠি হাতে বাড়ির কয়েকজন লোক নিয়ে অতর্কিত আক্রমণ করে মণিদা এবং অপর কমরেডটিকে আহত করেন। আক্রমণের সময় মণিদা (কমঃ মণিকৃষ্ণ সেন – বর্তমান প্রতিবেদক) স্থানীয় এক আধিয়ারের বাড়িতে ভাত খেতে বসেছিলেন। মণিদাকে যখন লাঠি দিয়ে আঘাত করে, তখন বাইরে এক বৃদ্ধা কৃষকরমণী (বাবুরি বর্মণের মা) গাইন (ধান ভানবার জন্যে যে কাঠের লাঠি ব্যবহার হয়) হাতে আততায়ী মাড়োয়ারীকে প্রচন্ড প্রহার দেয়।’ …… ‘আজ বাবুরি বর্মণের মায়ের একটা স্কেচ নিলাম, জিজ্ঞেস করলুম-“মাড়োয়ারীকে মারতে গেলেন, আপনার ভয় করলনা?” তিনি বললেন- “ভয় কেনে? আমার ছাওয়ালগুলোকে ডাঙাইচে (মারছে) আমি ডাঙামু না?”১০
“……১৯৪৪ সাল। দুর্ভিক্ষ চলছে। এবারে আন্দোলন করলাম কম্বল চাই।….. দেবীগঞ্জ থানার অফিসার চিঁড়াগুড় দিলেন। রাত্রে ফিরে এলাম বুড়িমার বাড়ি। …… ১৯৪৪ সামে বুড়িমা ধান কাটার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন, পাঁচ-ছয়শত মহিলা নিয়ে এবং অনেক পুরুষ নিয়ে সুরেন রায়ের (সুন্দরদি ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট) জমি থেকে ধান কাটেন। তিনদিন আগেই আমার উপর সুরেন রায় ও পুলিশের দারোগা প্রচন্ড মারধর চালান। বুড়িমা মহিলাদের যোগাড় করে খাহিল নিয়ে (ঢেঁকির ডান্ডা বা মুলোই), ঝাঁটা নিয়ে পুলিশ ক্যাম্প ঘেরাও করে।….. এরা পাঁচশ’ বিঘের ধান কাটেন দু’দিন ধরে, এই সংগঠন বুড়িমার জন্যই সম্ভব হয়। ১৯৪৩ সাল থেকেই কৃষক সমিতির কাজে অগ্রণী ছিলেন বুড়িমা।”১১
১৯৪০ সালেই ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট বেরিয়ে যায়। কমিশনের সুপারিশগুলো ছিলঃ (ক) মধ্যস্বত্ত্ব প্রথার বিলোপ, (খ) মধ্যস্বত্ত্বভোগীদের নিট্্ আয়ের দশগুণ ক্ষতিপূরণ, (গ) ওয়াকফ, দেবোত্তর প্রভৃত ন্যাসভুক্ত জমিদারীর ক্ষতিপূরণসহ অধিগ্রহণ*, (ঘ) মেছোঘেরি অধিগ্রহণ, (ঙ) রায়ত কৃষকদের প্রজাবিলি জমিতে উপস্বত্ত্ব বাজেয়াপ্ত করা, (চ) উপযুক্ত সংশোধনের মাধ্যমে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ত্ব আইনে (বেঙ্গল টেন্যান্সি অ্যাক্ট) বর্গাদারদের রায়তি স্বত্ত্ব প্রদান।
[* কৃষকসভা, বঙ্গীয় প্রাদেশিক সভা ও কমিউনিস্ট পার্টি (অবিভক্ত) ক্ষতিপূরণের যেমন বিরোধী ছিল, তেমনি বর্গাদারদের সম্পর্কেও উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা গ্রহণ করেনি।]
যেটা উল্লেখ্য তা হলো কংগ্রেস, কৃষক-প্রজা পার্টি ও মুসলিম লিগের সঙ্গে এসময়ে কৃষক সংগঠন, আন্দোলনগুলির সম্পর্ক কেমন দাঁড়িয়েছিল, বলাই বাহুল্য। নেহেরুর আচরণের দ্বিচারিতা, বুর্জোয়া লিব্যারেলদের দর্পণ ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, আচার্য কৃপালনি বা তাদের অনুগামীরা সকলেই জমিদারদের বিরুদ্ধে যে কোনও ধরণের আন্দোলনের বিরোধী। গান্ধীজী কৃষক সংগঠন গড়ে তোলার বিরোধী বরাবরই (যদিও একথা অনস্বীকার্য যে তিনিই প্রথম এবং একমাত্র জাতীয় নেতা যিনি ভারতের গ্রামীণ অধিবাসীকে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সমাবিষ্ট করে তুলতে পেরেছিলেন), অহিংসা ও অসহযোগ আন্দোলন না শেষ পর্যন্ত সহিংস হয়ে ওঠে এই দুশ্চিন্তার নির্মোকে। স্বভাবতঃই হিন্দু জমিদার ও জোতদাররা কংগ্রেসে অনুপ্রবিষ্ট হয় তাদের উপার্জিত ও অনুপার্জিত জমি- বিষয়আশয় রক্ষার তাগিদে। মধ্যবিত্ত হিন্দু-মুসলমান জমি-মালিকরা প্রথমদিকে আধিয়ার হেকে তেভাগা আন্দোলনে যোগ দিলেও যেই ‘নিজ খামারে ধান তোল’ শুনল, তখনই কংগ্রেস বা লীগের দিকে ঝুঁকলো। যেহেতু ফজলুল হক নেতৃত্বাধীন কৃষক-প্রজা পার্টি মন্ত্রিত্ব পাওয়ার জন্য মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, ফ্লাউড কমিশন গঠন করা সত্ত্বেও, তাঁদের সম্পর্কটা কৃষক বিশেষ করে গরীব চাষী, ভাগ চাষী, বর্গাদার ও ক্ষেতমজুরদের সঙ্গে বিরোধিতার অবস্থানেই ছিল।
আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয়- সেরকম ভাবে উঠে আসেনা যে যুক্তবঙ্গের যেসব জায়গায় তেভাগা ও উল্লিখিত কৃষক আন্দোলনগুলি (বিশেষ করে জমির স্বত্ত্বের, খাজনা বৃদ্ধি-বিরোধী বা হাট-তোলা বিরোধী এবং মহাজনী ঋণ মকুব বা ভাগচাষীর ঘরে তিনভাগের দু’ভাগ ফসল তোলার) গড়ে উঠেছিল, সেগুলোর বেশির ভাগ অংশই বাংলাদেশের অন্তর্গত বা এদেশেও তারই সন্নিহিত অঞ্চল। রাঢ় বঙ্গে এ আন্দোলন একেবারেই প্রায় গড়ে ওঠেনি। এর সঙ্গে নিশ্চয়ই রায়ত প্রথা ও বর্গাদার প্রথার একটা যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে- পরবর্তী প্রজন্মের যাঁরা এসব নিয়ে ভাবছেন তাঁরা নির্মোহে এসব নিয়ে অনুসন্ধান চালাবেন আশা রাখি।
আজ ‘অপারেশন বর্গা’ নিয়ে প্রায় রামায়ণী কথা চলতেই থাকে। অবশ্যই এর সাফল্যকে ছোট করছিনা, সুন্দরবন, বিশেষ করে কাকদ্বীপের আন্দোলন তো সত্যি সত্যিই কিংবদন্তীর পর্যায়ে পৌঁছেছিল। কিন্তু সেটা স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের আন্দোলন। অপারেশন বর্গা আজ স্তিমিত কেননা, “বর্তমান অবস্থায় ভূমি সংস্কার আন্দোলনে আর অতীতের মত আবেগ সঞ্চারিত হয় না এবং গতিবেগ আসা সম্ভব নয়। যে সমস্ত জায়গায় এখনও কিছুটা ভূমি ও খাস জমি বন্টনের সুযোগ আছে সেখানে কৃষক আন্দোলন ও প্রশাসনিক উদ্যোগে ভূমি বন্টনের কাজ চলছে। কিন্তু এ প্রশ্নে ক্রমশ সীমাবদ্ধতা আসছে ও আসতে বাধ্য।”১২ আসলে এ সময়টা থেকেই তো বামেদের, বিশেষ করে সিপিএম-এর ভাবনায় বা কাজে বৃহৎ পুঁজির জন্য জমি সংগ্রহের (হাতানোর!) পর্ব শুরু হয়ে গেছে।
দিশা ও উত্তরাধিকার
এই নাতিদীর্ঘ আলোচনার (যার প্রায় সবটাই আন্দোলনের কর্মী, নেতৃবৃন্দ এবং কিছু গবেষকের ইতিহাসচারণার থেকে নেওয়া) থেকে আমরা দেখতে পাই যে মূলতঃ কমিউনিস্ট কর্মী (মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে উঠে আসা, যাঁদের অনেকেই ছিলেন পুরোনো বিপ্লবী বা কংগ্রেসী), কৃষকসভার স্থানীয় নেতৃবৃন্দ (যার অধিকাংশই ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির গোপন কর্মী) এবং অসংখ্য-সহস্র সাধারণ কৃষক, ভাগচাষী, বর্গাদার, বিপুল সংখ্যায় ক্ষেতমজুর সেদিন এক অসাধ্য-সাধন ক্রিয়ায় নেমেছিলেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফল হয়েছিলেন, অবশ্যই অজস্র প্রাণের বিনিময়ে; ক্ষেতে-মাঠে-হাটে বহু রক্ত ঝরানোর পর এরই ফল হিসেবে আমরা পাই কাকদ্বীপের আন্দোলন। সেটা অনেকটা ছোট অঞ্চল জুড়ে একটা বিরাট সশস্ত্র সংগ্রামের চেহারা নিয়েছিলো, কিন্তু আমরা যুক্তবঙ্গের তেভাগা নিয়ে ভাবছি বলে সে কথা থেকে বিরত হলাম।
কংগ্রেসীরা দাবী করেন যে তেভাগা থেকে উঠে আসা প্রশ্নগুলোর সাংবিধানিক সমাধান তাঁরাই করেছেন। একথা সত্য যে ১৯৫০ সালে ‘পশ্চিমবঙ্গ বর্গাদার আইন’ প্রণীত হলেও, বর্গাদার/ভাগচাষীদের মূল দাবীই সেখানে উপেক্ষিত থেকে গেছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে সমকালীন বিধানসভা উক্ত আইনে নিম্নোক্ত সাবধানী ধারাটি যোগ করতে ভোলে নিঃ ‘এই আইনে কোনও কিছুই মালিক ও বর্গাদারের মধ্যে জমিদার ও প্রজার সম্পর্ক হিসাবে বিবেচিত হবেনা, এবং এই আইনে কোনও কিছুই মালিকের জমিতে বর্গাদারের চাষের উত্তরাধিকার অথবা বিনিময়ের অধিকার অর্পণ করছে না।’১৩
এ অবস্থাটা কেন রয়েই গেল তার তথ্যানুন্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সমাজমানসের, এমনকি, বিপ্লবী ও কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দের সামাজিক অবস্থান ও মানসিকতারও গভীর অনুশীলনের প্রয়োজন রয়েছে।
ফ্লাউড কমিশনের রিপোর্ট বেরোয় ১৯৪০-এর মার্চে। ১৯৩৯ সালে বঙ্গীয় কৃষক সভা কমিশনের কাছে যে স্মারকলিপি পেশ করেছিল তাতে বর্গাদারদের/ভাগচাষীদের কথা উল্লেখিত হয়নি। শুধু তাই নয়, কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বঙ্কিম মুখার্জী বলেছিলেন “…… বাংলাদেশের ২৫টি জেলায় কিষাণসভার ৫০০০০ সদস্য আছে। সদস্যদের মধ্যে রায়ত, অধীনস্থ-রায়ত ও বর্গাদারদের প্রতিনিধিত্ব কার তা যাচাই করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি কিশোরগঞ্জ মহকুমায় একটি সমীক্ষা করা হয়, তাতে দেখা গেছে রায়তরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ, অধীনস্থ-রায়ত ও বর্গাদারদের সংখ্যা তুলনায় খুবই কম।”১৪, মৌখিক প্রশ্নের উত্তরে কমঃ মুখার্জী বলেন- তিনি বর্গা প্রথারই অবসান চাইবেন- কিন্তু যদি কোনও প্রজা বর্গাদারকে চাষের জমি দিয়ে থাকে তাহলে সে জমি চাষ করার অধিকার (মালিক) প্রজারই থাকবে এবং যদি (মালিক) প্রজা চাষ করতে অস্বীকার করে, কেবল তাহলেই চাষ করার অধিকার বর্গাদারের পাওয়া উচিত।১৫
এ তো গেল বর্গাদার/ভাগচাষীদের কথা, ক্ষেতমজুরদের সম্পর্কে তেভাগার ষাট বছর পরে বামপন্থীদের অবস্থানটা কি একটু দেখে নেওয়া যেতে পারে। “রাজ্যে ভূমি সংস্কারের মাধ্যমে ২৩ লক্ষ ভূমিহীন মানুষ কিছু জমি পাওয়ায় ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যাবৃদ্ধির হারটি তুলনায় কম। কিছু ক্ষুদ্র কৃষক ও বর্গাদারদের একাংশ নিজের জমির কাজ সেরেও কিছুটা সময় গ্রামীণ মজুর হিসেবে কাজ করছেন। দেশব্যাপী তীব্র সংকট ও নিঃস্বকরণের প্রক্রিয়া চালু থাকায় ভূমিহীন ক্ষেতমজুরের সংখ্যাবৃদ্ধির প্রশ্নটা স্বাভাবিক।” মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন।১৬
“যখন তেভাগা আরম্ভ হয়…… ভূমিহীনরা ও দিনমজুরেরা ব্যাপকভাবে যোগ দিয়েছিল, অথচ এই শ্রেণীটির রাজনৈতিক দাবি আমাদের প্রত্যক্ষ কর্মসূচিতে বিশেষ কিছু ছিল না।…… আমরা, এমন কি আধিয়ারেরাও ভাবতে পারেনি দিনমজুরেরা এভাবে জঙ্গী মনোভাব নেবে। দিনাজপুরে যে চার বার গুলি চলে এবং প্রায় চল্লিশজন মারা যায়, তাদের নেতাদের বেশিরভাগ ছিল ভূমিহীন কৃষক।”১৭
“ক্ষেতমজুরের মজুরির ভূমিকা (দাবি) বড়ো কথা ছিল না। কিন্তু তারা এই আন্দোলনের প্রথম সারিতে ছিল। This is a weakness on the part of the movement, তারা ভাগ ও পায় নি, তাদের জমির কথাও ছিল না। অথচ তারা maximum fight করেছে। …… পরে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে ক্ষেতমজুরদের জমি দিতে হবে এ Realization আমাদের এসেছে।”১৮
‘রিয়েলাইজেশন’ কি সত্যিই হয়েছে?
—-
তথ্যসূত্রঃ
(উদ্ধৃতিগুলোর বানান যথা সম্ভব মূলানুগ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে বলে একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন চেহারা দেখা যাবে)
১) দেবেশ দাশ, ভারতে কৃষক আন্দোলনের ধারা (১৯৩০-৪০), মূল্যায়ন শারদীয় সংখ্যা, ১৩৮০ (ইং ১৯৭৩-৭৪)
২) অধ্যাপক নরহরি কবিরাজের সঙ্গে বর্তমান লেখকের সাক্ষাৎকার (১৯ জানুয়ারী, ২০১০)
৩) দেবেন দাশ (ঐ)
৪) তদেব
৫) সোমনাথ হোর, তেভাগার ডায়েরি, কৈফিয়ৎ, সুবর্ণরেখা, ১৯৯১
৬) অঘোর দেববর্মা, ত্রিপুরা রিয়াং বিদ্রোহ, মূল্যায়ন, বর্ষ ১৭, সংখ্যা ১, ১৩৮৮ (ইং ১৯৮১)
৭) সোমনাথ হোর (ঐ)
৮) তদেব
৯) শচীন্দু চক্রবর্তীর সাক্ষাৎকার, বর্তিকা, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০০৩
১০) সোমনাথ হোর (ঐ)
১১) মাধব দত্তের সাক্ষাৎকার, বর্তিকা
১২) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য, একবিংশতম সম্মেলন, ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)ঃ রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রতিবেদন (পৃঃ ৩৭), ৯-২২ ফেব্রুয়ারী, ২০০৫
১৩) প্রণব দে, ভূমি সংস্কার আন্দোলনের পরম্পরাঃ বর্গাদার, অনীক, মার্চ ২০০৭
১৪) তদেব
১৫) মৈত্রেয় ঘটক, ১৯৪৬-৪৭ এর তেভাগা আন্দোলনের কয়েকটি দিক ও কিছু প্রশ্ন, বর্তিকা
১৬) পঃবঃ রাজ্য ২১তম সম্মেলন ভাকপা(মা), পৃঃ ১৩২
১৭) অবনী লাহিড়ীর সাক্ষাৎকার, বর্তিকা
১৮) হেমন্ত ঘোষালের সাক্ষাৎকার, বর্তিকা
এছাড়া, দীপঙ্কর ভট্টাচার্যের গবেষণাগ্রন্থ ‘Peasant Movements in Bengal and Bihar’ (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত), ১৯৯২, থেকে বহুতর সাহায্য নেওয়া হয়েছে।


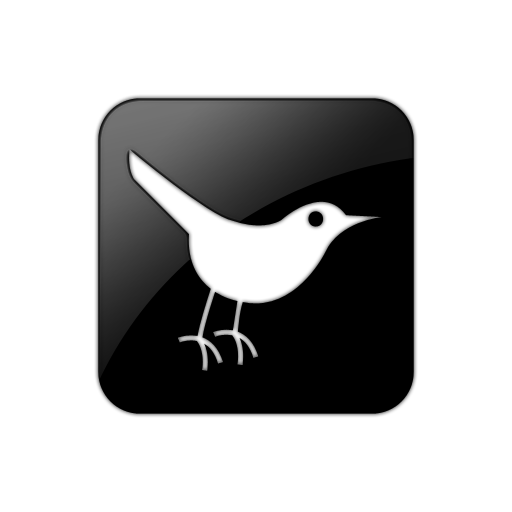
Leave a comment