সেই সময়ের গল্প – পর্ব দুই
Posted by bangalnama on September 13, 2010
– লিখেছেন সন্তোষ কুমার রায়
শৈশব কৈশোরের অনেকটা সময়ই কাটিয়েছি মামার বাড়িতে। সেখানে থাকার কারণ ছিল। আমি যখন বছর তিনেকের বা তার একটু বেশী তখন আমার পরের ভাই হল। পাবনার একান্নবর্তী পরিবারের সব কাজ সামলে দু’টি সন্তানকে দেখাশোনা করা মায়ের পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। এছাড়া আমার মামার বাড়িতে তখন ছিল একটা শিশুর অভাব। মামারা সবাই প্রায় বড় হয়ে গেছেন আর তাঁদের সন্তানসন্ততিও হয়নি। সুতরাং আমাকে আনা হয়েছিল। তখন আমার বয়স পাঁচ বছর বা তারও কম। মাঝে মাঝে পাবনায় আসতাম কিছু দিনের জন্য।
অক্ষর পরিচয় হয়েছিল দাদু (দাদামশায়)র কাছে আর প্রাথমিক শিক্ষা গ্রামের পাঠশালায় – যার নাম ছিল ‘রামসুন্দরের পাঠশালা’। রামসুন্দরবাবু ছিলেন ঐ পাঠশালার ‘বড়মাস্টার’। তাই ঐ নাম।
মাতৃস্নেহ আর দিদিমার স্নেহ একত্রে পেয়েছিলাম দিদিমার কাছ থেকে। তিনি দিদিমা অপেক্ষা ‘দিদিমনি’ ডাকটাই বেশী পছন্দ করতেন। তাই তিনি আমার দিদিমনি ছিলেন এবং দ্রুত উচ্চারিত হওয়ার কারণে অচিরেই দিদিমনি ‘দিয়ানি’ হয়ে গেলেন।
দিয়ানি ছিলেন সেই কালের মহিলা যাঁরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় পাঠশালার শেষ শ্রেণীর বেশী এগোতে পারেননি। কিন্তু তিনি অনেক কিছু পড়তেন এবং এক মামার কাছে শুনেছি তিনি তাঁর একটি খাতায় রোজনামচাও লিখতেন, আর সে লেখা একেবারে হেলা ফেলা করার মত ছিল না।
সে সময় কলকাতা থেকে একখানা খবরের কাগজ যেত ডাকে (দিন তিনেক বাদে পৌঁছত)। দাদুর পড়া হয়ে গেলে দিয়ানি সেখানা নিয়ে মগ্ন হয়ে পড়তেন মনে আছে। কাগজখানা সম্ভবত ছিল ‘সত্যযুগ’ অথবা ‘লোকসেবক’, সঠিক মনে নেই।
দিয়ানি আমাকে একটা খুব ভাল জিনিষ শিখিয়েছিলেন। সেটা হল চিঠি লেখা। কায়দামাফিক চিঠি লেখাটা পরে শিখেছিলাম স্কুলে, কিন্তু ভিত্তিটা গড়া হয়েছিল দিয়ানির হাতেই। মামার বাড়ি থেকে অপটু হস্তাক্ষরে মাকে চিঠি লিখতাম পাবনায়।
কলকাতায় আসার পর মনটা আনচান করত মামার বাড়ির কথা ভেবে। তখন চিঠি লিখতাম দিয়ানিকে। ওখানকার খবর নিতাম, আমাদের খবর দিতাম।
এই প্রসঙ্গে আর একজনের কথা না বললেই নয়। দিয়ানিকে লেখার সময় তাঁকেও লিখতাম একখানা পোস্টকার্ড। তাঁর নাম হায়াত আলি মিঞা, ঐ গ্রামের বাসিন্দা।
আমার ৯/১০ বয়সে হায়াত ভাই (ঐ নামেই ডাকতাম) ছিলেন আমার friend, philosopher and guide । বয়সে আমার চেয়ে বেশ বড়; কি করে আর কেনই বা দুই অসমবয়সীর বন্ধুত্ব হয়েছিল তা বলতে পারব না। তবে আমার অতবড় শুভাকাঙ্ক্ষী বাড়ির মানুষ ছাড়া আর কেউ ছিলেন না।
আগে যারা সমঝে কথা বার্তা বলত, দেশভাগের পর তাদের অনেকেরই হাবভাব কিছুটা পালটে গিয়েছিল সে সময়। নানাভাবে তাদের ঔদ্ধত্য প্রকাশ পেত। হায়াত ভাই সে সময় আমাকে নিজের ভাইয়ের মত আগলে রাখতেন। কলকাতা আসার পর তাঁকে নিয়মিত চিঠি লেখার একটা অভ্যাস হয়ে গেছিল। আমিও অপেক্ষা করে থাকতাম ‘পূর্ব পাকিস্তান’ ছাপমারা মেটে রঙের পোস্টকার্ডের আশায়।
এরপর যা হয় আর কি। উভয় পক্ষ থেকেই চিঠির সংখ্যা কমে এল আস্তে আস্তে। কলকাতার জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া আর ব্যস্ততার মধ্যে চিঠি লেখার সেই ব্যাপারটা ক্রমশঃ তলিয়ে গেল।
আমি পাকাপাকি চলে আসার সময় এই মানুষটি দুটো জিনিষ উপহার দিয়েছিলেন। হয়ত চেয়েছিলেন, যেন আমি তাকে মনে রাখি। প্রথমটা হল একটা ছোট্ট নোটবুক, যার মলাটে একটা ছোট ডিম্বাকৃতি আয়না আটকান ছিল। এটা এখনও আমার কাছে সযত্নে রাখা আছে। অপরটি হল প্ল্যাস্টিকের তৈরী ছোট একটা খাঁচা, যার মধ্যে ছিল একটা টিয়া পাখী। এটাকে রাখা যায় নি, আর তা সম্ভবও ছিল না। মাঝে মাঝে মনে হয় খাঁচার পাখীটা আমার ভবিষ্যত জীবনের ইঙ্গিতবাহী ছিল হয়ত।
কলকাতায় আসার অনেকদিন পরে পরিচিত ছাপ মারা একখানা খাম আসায় একটু বিস্মিতই হয়েছিলাম, কেননা সাধারণত পোস্টকার্ডই আসত আমার নামে। দেখি তার মধ্যে শ্মশ্রুগুম্ফধারী হায়াত ভাইয়ের একখানা ফটো। জীবনে যত আনন্দময় মুহূর্ত এসেছে এটা তার মধ্যে অন্যতম ছিল। ছবিটা আমার ছবির অ্যালবামে রাখা আছে এখনও।
হায়াত ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ কেন রাখিনি বা রাখতে পারিনি সেই নিয়ে এখন বিস্তর আফশোষ হয়। উনি এখন কোথায় কিভাবে আছেন জানি না। তবে উনি যেখানেই থাকুন আমার মনের মণিকোঠায় পাকাপাকি স্থান দখল করে রয়েছেন আর থাকবেনও চিরকাল।
দাদুর (দাদামশায়ের) একটা লাইসেন্সপ্রাপ্ত দো’নলা বন্দুক ছিল। সেটা দাদুর তো বটেই গ্রামের সকলেরও কতকটা বলভরসা ছিল। মাঝে মাঝে গ্রামের মানুষের ছোটখাটো প্রয়োজনে তাঁকে সেটা ব্যবহারও করতে দেখেছি। একদিন বিকেলের দিকে খেলাধুলো করে ফিরে এসে বাইরের কাছারি ঘরের সামনে জটলা দেখে দাঁড়ালাম। সেখানে দুজন অন্যরকম পোষাক পরা লোক চেয়ারে বসে কিছু কাগজপত্র নাড়াচাড়া করছে আর সামনের টেবিলের ওপর বন্দুকটা রয়েছে। ছোট বলে সেদিন ওখানে দাঁড়াতে দেওয়া হয় নি আমাকে। তবে পরে বড়দের কথাবার্তা শুনে বুঝেছিলাম বন্দুকটা বোধ হয় সরকারী ভাবে হাতছাড়া হয়েছিল সেদিন।
দাদু ছিলেন ‘গ্রামের মাথা’র মত। তাঁর অনুমোদন ছাড়া কোন কাজ হত বলে আমার মনে হয় না। সমস্ত কাজেই তাঁর একটা মতামত থাকত। বন্দুকের ব্যাপারটার পর দাদু নিজেকে ক্রমশঃ গুটিয়ে নিতে থাকেন। দিয়ানির সাথে কথাবার্তার মধ্যে তাঁর অসহায়তা প্রকাশ পেত। এটা আমি সেই বয়সেও বুঝতে পারতাম। আমাকে নিয়েও তাঁর চিন্তা ছিল খুব, ‘পরের ছেলে’কে তার বাপমায়ের কাছে পাঠাবার জন্য তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন সে সময়। যদিও এরপরও বেশ কিছুদিন আমি ওখানে ছিলাম।
কলকাতায় আসার পর একটা ব্যঙ্গোক্তির সাথে পরিচিত হলাম। কথায় কথায় পাড়ার বন্ধুবান্ধব বা স্কুলের সহপাঠীদের অনেকেই জিজ্ঞেস করত – তোরা কোথাকার জমিদার ছিলিরে? বলেই হি হি করে হেসে উঠত। প্রশ্ন আর হাসির কারণ জিজ্ঞেস করলে আরও হাসত ওরা।
পরে ব্যাপারটা বুঝলাম। আসলে তৎকালীন পূর্বপাকিস্তান থেকে যাঁরা উদ্বাস্তু হয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে উচ্চ এবং মধ্যবিত্তেরা বেশ সচ্ছল অবস্থাতেই ছিলেন, এটা আমাদের পরিচিতদের দেখেই বুঝতে পারতাম। এঁরা হঠাৎ করে এপারে এসে সহায় সম্বলহীন অবস্থায় দিশেহারা হয়ে পড়তেন। এবং কথা প্রসঙ্গে স্থানীয় মানুষের কাছে নিজেদের ছেড়ে আসা সচ্ছলতার কথা বলে আক্ষেপ করতেন। ভাবপ্রবণ হয়ে অনেকেই লাগামছাড়া হয়ে পড়তেন। এর থেকেই ‘জমিদারি’ কথাটা। আর তা নিয়ে বিদ্রুপ।
আমি যেখানে থাকি (রূপনারায়ণপুর, বর্ধমান) সেটা লাল কাঁকুরে মাটির দেশ। সেকালে প্রচুর উদ্বাস্তু মানুষ এ অঞ্চলের রেলের কারখানায় চাকুরি করতে আসেন। চাকুরি থেকে অবসর নেওয়ার পর অনেকেই এখানে বাড়ি করেছেন এবং অনেকেরই বাড়ি-সংলগ্ন কিছুটা করে জায়গাও আছে।
এখানকার কাঁকুরে মাটিতে ফলপাকুরের চাষ করা রীতিমত কষ্ঠসাধ্য। কিন্তু হলে কি হবে, প্রায় প্রত্যেকেই ঐ জমিতে আমকাঁঠালের আর অন্যান্য ফলের গাছ লাগিয়েছেন। আমার সব থেকে আশ্চর্য লাগে এই দেখে যে এঁরা এখানে নারকেল গাছও লাগিয়েছেন, যা কিনা হওয়া প্রায় অসম্ভব। কিন্তু বাস্তব ঘটনা হল এটা যে এখানে প্রচুর নারকেল গাছ হয়েছে এবং সবাই না হলেও অনেকেই সেই গাছের ফল খেয়ে চলেছেন। নারকেল গাছ পূর্ব বঙ্গের মানুষের কাছে একটা অবসেশন।
অবসর নেবার পর যে সব মানুষ এখান থেকে অন্যত্র চলে গেছেন অন্ততঃ বছর বিশেক আগে, তাঁরা এখন এ জায়গা দেখে অবাক হবেন – হঠাৎ করে পূর্ববাংলার কোন গ্রাম ভেবে বসতেও পারেন। ঘরছাড়া এইসব মানুষ এঁদের ফেলে আসা শৈশব কৈশোরের দিনের কথা ভুলতেই পারেন না। ভোলা যায়ও না বোধ হয়। নিজেকে দেখেই তো বুঝতে পারছি।
আমার মামারা ছিলেন পাঁচ ভাই। বড়মামা আর ছোটমামা ছাড়া মাঝের তিনজন ছিলেন যথাক্রমে ফুলমামা, সোনামামা আর ভালমামা। ফুলমামা আর ভালমামার সাথে আমার জমতো বেশী। অন্যেরা চলে এলেও বড়মামার ছেলেরা ওখানে রয়ে গেছে এবং মনে হয় ভালই আছে। সম্প্রতি ভালমামা ইহলোক ত্যাগ করেছেন। শেষ বয়সে তাঁর ‘দেশের বাড়ি’ যাবার প্রবল ইচ্ছা হয়েছিল। রোগশয্যায় যতবার দেখা করতে গেছি ততবারই আক্ষেপ করেছেন দেশের বাড়ি যেতে না পারার জন্য। যখন প্রশ্ন করতাম যে আগে যান নি কেন,তখন আশঙ্কা প্রকাশ করতেন এই বলে যে, অনেক পরিবর্তন তো হয়েছে, যদি সে রকম না থাকে!
তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। সেখানে মামার বাড়ির একখানা ঘরের ছবি দেখলাম, যেটা একেবারেই আশা করিনি। বছর খানেক আগে ফুলমামার ছেলেরা বাংলাদেশ গেছিল পৈত্রিক ভিটা দর্শনে। ওরা ওখানকার কতকগুলি ছবি তুলে এনেছিল। ভালমামার দেশের বাড়ি নিয়ে আকুতির জন্য তাঁর প্রিয় অনেক কিছুর সঙ্গে তাঁর প্রিয় ঐ ঘরের একখানা ছবিও রাখা হয়েছিল।
দাদুর তৈরী এ ঘরখানা এখন থেকে প্রায় আশি বছর, হয়ত বা তারও আগেকার। দোতলা ঘর। এ ঘরের বৈশিষ্ট্য হল সব কিছুই কাঠ আর টিন দিয়ে বানানো। এমন দোতলা ঘর সেকালের নিরিখে একটু অবাক করা ঘটনাই ছিল বোধহয়। সিঁড়ির উচ্চতম প্রান্তে একটা দরজা ছিল যাকে বলা যায় চাপা দরজা। এটি বন্ধ থাকলে ওপরের মেঝের সঙ্গে একাকার হয়ে যেত। এ অবস্থায় দোতলায় ওঠা একরকম অসম্ভবই ছিল। ঘরখানা সবারই প্রিয় ছিল। আমার শৈশবের বেশ কয়েকটা বছর কেটেছে ঐ দোতলা ঘরে। বর্তমানে ছবিটা দেখে চিনতে অসুবিধা না হলেও মনটা দমে গেছিল। কারণ কালের নিয়মে ঘরটার এখানে সেখানে কিছু কিছু পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী ছিল এবং সেটা হয়েছেও। এসব পরিবর্তন মানতে মন চাইছিল না।
বড়মামিমা একবার ফোনে বলেছিলেন – একবার আসতে পার না! কত মানুষেই ত আসা যাওয়া করছে। মনে মনে সুপ্ত ইচ্ছা ছিল যে কোনও দিন গেলেও একবার যাওয়া যেতে পারে। ছবিটা দেখার পর ভালমামার সেই কথা মনে পড়ল – যদি সে রকম না থাকে!
হায়াত ভাইয়ের কথাও মনে পড়ল। ওঁর সাথে যোগাযোগ করার কথা ভেবেছিলাম একবার। কিন্তু এখন ভাবতে হচ্ছে – সত্যি, যদি সব সে রকম না থাকে! সুতরাং…
সুতরাং সেই সময়ের সব কিছুর স্মৃতিটুকুই থাক না শুধু !
(শেষ)


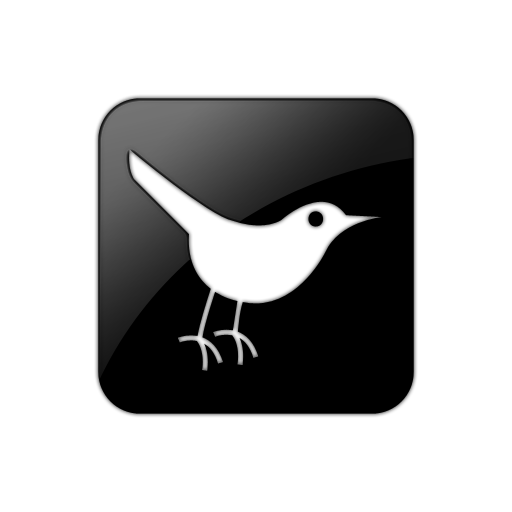
brishti said
সন্তোষ কুমার রায়ের সেই সময়ের ‘গল্প’ যা আসলে জীবন থেকেই নেয়া, পড়ে কেমন একটা স্মৃতি-মেদুর ভালোলাগায় মন ভরে গেলো…বিশেষ করে শেষ অংশটুকু…সত্যি তো ,প্রতিদিন ই ‘সময় ‘ যেভাবে দ্রুততম অশ্বের গতিতে এগুচ্ছে……সেখানে
‘সেই সময়ের ‘সব কিছুর স্মৃতিটুকুই থাক না শুধু 🙂