সেই সময়ের গল্প – পর্ব এক
Posted by bangalnama on December 31, 2009
সাবেক পুর্ব পাকিস্তান থেকে প্রথম দফায় যাঁরা ভারতে এসেছিলেন আমি তাঁদের দলের। সেই ১৯৫১ সালের আগস্ট (শ্রাবণ) মাসে বছর দশেক বয়সে পুর্ববঙ্গ ছেড়েছি। সেই বয়সের স্মৃতি প্রায় ষাট বছর পর মনে থাকাটা মুশকিলই বটে। তবে ভুলে যাওয়াও হয়ে ওঠেনি।
পাবনা শহর থেকে আমাদের পরিবারের সবাই ১৯৪৮এ কলকাতা চলে এলেও আমার আসা হয় নি। কারণ ঐ সময় আমি মামার বাড়ি ছিলাম। তাই পরে আসা।
ছোট বয়স থেকে নিরিবিলিতে থাকতে অভ্যস্ত আমি প্রথমেই ঘাবড়ে গেছিলাম রেলগাড়ীতে চড়ার জন্য উদগ্রীব মানুষের সংখ্যা দেখে। প্ল্যাটফর্মবিহীন একটা হল্ট স্টেশনে গিসগিস করছে লোক । দূর থেকে ইঞ্জিনের আলো দেখামাত্র সবাই যে যারমত প্রস্তুতি নিতে শুরু করাতে আমার মনে যে কি চাঞ্চল্য জেগেছিল সেটা আজও মনে আছে। বেশ মনে আছে আমাকে জানালা দিয়ে কামরায় ঢুকিয়েছিলেন বড়মামা আর কেউ একজন টেনে নিয়েছিল। স্টেশনের নাম ছিল সম্ভবত ভাঙ্গুরা।
শুধু আমাকেই নয়, আমার ছোট তিন ভাই বোনকেও একই কায়দায় কামরায় ঢোকানো হল। তারপর আর কিছু দেখতে পাই নি, মা আর বড়মামা যে কখন কিভাবে ঢুকলেন তা জানতে পারিনি।
ঠাসাঠাসি করে কোন রকমে মায়ের গায়ে ঠেস দিয়ে বসে গাড়ীর দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কখন তা জানিনা। কোন এক সময় হঠাত ঘুম ভেঙে দেখলাম অন্যরকম পোষাক পড়া কয়েক জন লোক সবার জিনিষপত্র ওলটপালট করে দেখছে। পরে জেনেছিলাম যে ওরা সরকারি লোক, সার্চ করছে। তখন বুঝিনি, এখন বুঝি কে, কেন সার্চ করত গাড়ীতে গাড়ীতে।
অনেকক্ষন পরে গাড়িটা ছেড়েছিল সেদিন। আবার ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মানে ঘুমিয়ে পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম, সার্চের নামে সেই লন্ডভন্ড কান্ড দেখতে দেখতে। ভয়ে চোখ বুজে চুপ করে মায়ের গায়ে লেপ্টে ছিলাম। কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। পড়ে জানতে পারি যে ওটা ছিল সীমান্ত স্টেশন, নাম দর্শনা। অনেক দুর্দশার সাক্ষী।
সেই থেকে একটা ভয় ঢুকে গিয়েছিল মনে। এখনো সেই মানসিকতা কাটে নি। টেলিভিশন বা সিনেমায় কোন হিংস্রতা, অত্যাচার –এসব কিছু দেখতে পারিনা এখনো। পড়ি না কোন এমন বিবরণও।
মাতৃভূমি ত্যাগের প্রথম চরণের সেই রেলগাড়ীতে চড়া আর দর্শনার অভিজ্ঞতার সামনাসামনি যেন আর কখনো পড়তে না হয়।
মায়ের ঠেলা খেয়ে আর ‘এখন নামতে হবে’ শুনে জেগে উঠলাম, গাড়ী থেমে আছে আর জানালার পাশ দিয়ে অনেক মানুষ হেঁটে চলেছে এক দিকে। আমরাও নেমে পড়লাম,সবার সাথে সেই দিকেই হাঁটতে শুরু করলাম।
রাস্তায় নেমে এলাম। অজস্র মানুষ জন, গাড়ী ঘোড়া দেখে যাকে বলে হতচকিত অবস্থা। এই তাহলে কলকাতা! সেই ছোট্ট বয়সে কত কথাই না শুনেছি এর সম্বন্ধে!
বড়মামা ঘোড়ার গাড়ী ঠিক করে ফেললেন একটা। নারকেলডাঙার ফুলবাগান মোড়ের কাছাকাছি আসার কথা আমাদের। মনে আছে ভাড়ার পরিমান ছ’আনা, না আট আনা তা নিয়ে অনেক বচসা হয়েছিল।
শেষ পর্যন্ত কত ভাড়া হয়েছিল তা আর মনে নেই আজ।
পাড়ার মোড়ে গাড়ী থামলে কিছু কৌতুহলি মানুষ ‘বাঙালবাড়ী’তে আবার লোক এল—এমন মন্তব্য ছুড়েছিলেন। মানে মাঝে মাঝেই এমনি লোকজন আসে এ বাড়ীতে।
নম্বর খুঁজে বাড়ীতে ঢুকতে সবাই ঘিরে ধরল। সবার দৃষ্টিই বিশেষ করে আমার দিকে। কারণ সকলেই আমাকে দেখছে বছর পাঁচ বা তারও বেশী সময় পরে, কেননা ঐ সময়টা আমি ছিলাম মামার বাড়ীতে। কেন ছিলাম সেটা পরে কখনো বলা যাবে।
মামার বাড়ীর খোলামেলা বড়সড় বাড়ীতে থাকার অভ্যাস হয়ে গেছিল , তাই ছোট বাড়ীতে অনেক মানুষের ভিড়ে কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেলাম।
পাবনা শহরে আমাদের বাড়ীটাও মোটামুটি খোলামেলাই ছিল যদিও সেখানে থাকার অভিজ্ঞতা আমার কমই ছিল। সুতরাং প্রাথমিক অস্বস্তি হওয়ার কথা ছিলই বোধ হয় এখানে। ‘অনেক মানুষদের’ সবাই যে আমার নিজের মানুষ,এটা ক্রমশঃ বুঝতে শিখলাম। একান্নবর্তী বৃহত পরিবারে থাকার মজাটা নতুন করে বুঝলাম। পরের বছর এক শীতের সকালে দাদুর(ঠাকুরদা) সঙ্গে গিয়ে চতুর্থ শ্রেনীতে ভর্তি হলাম স্থানীয় হাইস্কুলে।
সে সময়ে পরিবারের সব কিছু দেখার দায় ছিল বয়োজ্যেষ্ঠের। সেই হিসেবে বাড়ীর ছেলেমেয়েরা কোথায় কি পড়বে বা কি করবে তার দেখাশোনা করতেন দাদুই। আমাদের জেঠতুতো, খুড়তুতো, পিসতুতো ভাই বোন মিলে আমরা ছিলাম প্রায় দশবারোজন। পঁচাত্তর ছিয়াত্তর বছর বয়সে এসব করা চাট্টিখানি কথা নয়। তাছাড়া করতই বা কে! বড়রা সবাই ত’ ভোরে অন্ধকার থাকতে বেড়িয়ে পড়তেন শিয়ালদা’র উদ্দেশে। ডেলি প্যাসেঞ্জারি করতে হত যে বাবাকাকাদের।
ভোরে বেড়িয়ে যাওয়ার কথাটা কত সহজে বলে দিলাম। অথচ বাবাকে দেখে যে কি খারাপ লাগত আমার। তাঁর একটা পুরনো ফটোগ্রাফ দেখে বুঝেছিলাম কি দারুন শৌখিন ছিলেন তিনি। আমার ধারণা তিনি স্বপ্নেও কোনদিন ভাবেননি যে বাড়িঘর ছেড়ে সপরিবারে এমন আতান্তরে পড়তে হতে পারে।
ব্যারাকপুর অঞ্চলে অল্প বেতনের চাকরি ছিল তাঁর, ছেলেমেয়েদের সব খরচ মেটানো যেতনা তা দিয়ে। তবে চাকরিটা ছিল সরকারি,সময়মত মাইনেটা পাওয়া যেত।
দাদুর কথা বলছিলাম। তিনিই কি কখনো ভেবেছিলেন বৃদ্ধবয়সে বিদেশবিভূঁইতে নাতি নাতনিদের ভবিষ্যত চিন্তায় দৌড়াদৌড়ি করতে হবে ! সত্যি কথা বলতে কি, তাঁর সংগ্রহ করা একখানা কাগজ যা উদ্বাস্তু পুনর্বাসন দফতর থেকে পাওয়া যেত, সেটা না থাকলে আমার লেখাপড়া হত না।শুধু আমিই বা কেন বাড়ীর সব পড়ুয়াদেরই অসুবিধায় পড়তে হত। ওটা থাকাতে ‘উদ্বাস্তু ভাতা’ পাওয়া যেত পড়াশোনা করার জন্য। আমি I.Sc. পড়া পর্যন্ত ওটা পেয়েছি।
আমাদের পাবনার বাড়ীটা ছিল একটা হট্টমেলা। থাকার জায়গা থাকুক না থাকুক, রাতবিরেতে যখনই কেউ আসত তাকে ফেরান হত না। কত ধরনের মানুষ যে দেখেছি! বড়পিসিমা হঠাত গত হলে পিসেমশায়কে তাঁর তিন ছেলে নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে দেখেছি। বিধবা ফুলপিসিমা তাঁর তিন সন্তান নিয়ে থাকতেন। বাড়ীর কাজের লোক তার ছেলে গজাননদাকে নিয়ে থাকত। এরকম আরও অনেকেই থাকত, সবার কথা মনে নেই। কেউ এলেই দাদু তাকে আমন্ত্রণ জানাতেন কদিন থেকে যাবার জন্য। তখনকার দিনে গ্রামের স্কুলগুলির ম্যাট্রিক পরীক্ষার সীট পড়ত পাবনা শহরে। শুনেছি চেনাজানা পরীক্ষার্থিদের অনেকেই ভিড় করত আমাদের বাড়িতে। আমার মামারাও ছিলেন এঁদের মধ্যে।
বাড়ির অন্দরমহলের ব্যাপারগুলো সামলাতে হত মা আর ফুলপিসিমাকে। দাদু কাউকে থাকতে বলেই ছুটতেন বাড়ির ভেতরে, থাকার লোকের কিছু ব্যবস্থা করা যাবে কিনা সেটা জানতে। পিসিমা বকুনি দিতেন খুব, কিন্তু আয়োজনও করতে হত। দাদু কথা দিয়েছেন যে!
নারকেলডাঙার বাড়িতেও একই ঘটনা ঘটত। এমন এমন মানুষ আসতেন আর কিছুদিন স্থায়ীভাবে থাকতেন যেটা বর্তমান প্রেক্ষাপটে ভাবাই যায় না। পূর্ববঙ্গ থেকে যেমন এসেছিলেন ফুলপিসিমার বিধবা বড় জা,তাঁর তিন প্রাপ্তবয়স্ক ছেলে নিয়ে দেশভাগের পর। মেজপিসেমশায়ও সপরিবার এসে উঠলেন কিছু দিনের জন্য। আর সেজপিসেমশায় ত স্থায়ীভাবেই রয়ে গেলেন সপরিবারে। এছাড়াও কিছু কিছু লোকের নিত্য আসাযাওয়া ছিল। এতে সংসার খরচে টান পড়ত’ত বটেই স্থান অকুলানও হয়ে পড়ত দারুনভাবে।
দাদুর কথা ভাবলে এখনও খারাপ লাগে।জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মাতৃভুমির আচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। খুঁজে খুঁজে দেশের চেনাপরিচিতেরা, যাঁরা কলকাতায় এসেছেন, তাঁদের বাড়ী যেতেন। কে কেমন আছেন জানার চেষ্টা করতেন, প্রয়োজনে সান্ত্বনা দিতেন, সাহায্য করার প্রয়াস করতেন। বয়সের কারণে একা যাওয়ার সাহস করতেন না। দু’একবার আমিও তাঁর সঙ্গে গিয়েছি। ১৯৫৫ এর এক ডিসেম্বরে তিনি আমাদের ছেড়ে পরলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।
পড়শিদের ‘বাঙালবাড়ীতে’ লোক আসা নিয়ে কটাক্ষ করার কারণটা কারণটা সুতরাং বুঝতে দেরি হয়নি। আত্মীয়স্বজনের, নানা জনের আসাযাওয়ার, থাকার কারনেই ওই কটাক্ষ।
প্রতিদিন গড়ে প্রতি বেলায় পঁচিশ থেকে ত্রিশজনের পাত পড়ত বাড়িতে, প্রতিদিনই উতসব বাড়ীর মেজাজ আর কি!
লোকসংখ্যার অনুপাতে আয়ের উত্স ত আর বাড়ে নি। তাছাড়া সেটা তেমন মজবুতও ছিল না। সেজন্য ব্যয় সংকোচের দরকার থাকলেও করা যায় নি। শুরু হল কৃচ্ছসাধন।
বাড়ির অন্য সকলের থাকলেও আমার কলকাতা আসার আগে রুটি কি তার ধারনাই ছিল না। সত্যি সত্যিই কান্না পেত রুটি খাওয়ার সময়। অথচ দুপুরে রেশনের চালের ভাত জুটলেও বাকি তিন বেলাই বরাদ্দ ছিল রুটি।
মামার বাড়ী থাকার সময় একদিন আমাকে ঘানি থেকে সরষের তেল আনতে পাঠালে দারুন খুশী হয়েছিলাম একটা কাজ করতে পেরে।
কলকাতা আসার পর আপনা থেকেই নানারকমের কাজ এসে গেল। সাপ্তাহিক রেশন আনতে হত বিশাল লাইন দিয়ে।চালগমের বড়বড় থলি আনতে হত ঘাড়ে করে। গম ঝাড়াই বাছাই হলে পরে তা ভাঙিয়ে আনার একটা ব্যাপার ছিল। আর ছিল কয়লা আনা। সে সময় কয়লার উনুনে রান্না হত। এক সাথে দোকান থেকে কিনতে হলে বেশী দাম পড়ত বলে খুচরো কিনতে হত। শিয়ালদা’র রেল লাইনের ধারে সস্তায় পোড়া কয়লা পাওয়া যেত। প্রায় প্রতি সন্ধ্যায়ই এটা করতে হত। বাড়ির আমরা ছোটরা মিলেমিশে এসব কাজকর্ম করতাম। অদ্ভুত লাগে এই ভেবে যে একদা কাজ করে আনন্দ পাওয়াটা আস্তে আস্তে একঘেয়ে বিরক্তিতে পরিণত হয়ে গেল।
কলকাতা এসে প্রথমদিকে ভাষা নিয়ে ভারি মুশকিলে পড়েছিলাম। বাঙালভাষায় কথা বলা নিয়ে বাড়িতে, পাড়ায়,স্কুলে–সব জায়গায় হাসির পাত্র হয়ে পড়তাম। একদিন মেজদাদার কানমলা খেয়ে বেশ শিক্ষা হল। এর পর থেকেই কলকাতার ভাষা আস্তে আস্তে শিখে ফেললাম। একেবারে যাকে বলে এক্সপার্ট হয়ে গেলাম। সেটা বুঝলাম স্কুলের একজন শিক্ষকমশায়ের কথায়। ‘উদ্বাস্তু ভাতা’র বিজ্ঞপ্তিতে আমার নাম দেখে তিনি মন্তব্য করেছিলেন,– তোকে ত এদেশী ভেবেছিলাম।
একটা ব্যাপার বোধ হয় চিরকাল চলে আসছে। র্যাগিং এর মতো ঘটনা সেটা। যে কেউ যেকোন নতুন পাড়ায় আসুক না কেন তাকে নিয়ে নানা ধরনের হাসিমজা করার লোভ পাড়ার লোক ছাড়তে পারে না। আমার বেলাতেও তার অন্যথা হল না। কিন্তু আস্তে আস্তে নতুন পাড়ায় নতুন মানুষের সাথে মিশে গেলাম, তাদের একজন হলাম।
পাড়ার ক্লাবে একজন দাদা ছিলেন। দারুন আমুদে মানুষ। ছেলেদের নানা কাজে জড়িয়ে থেকে নানা ভাবে উতসাহ দিতেন। একটু হুজুগেও ছিলেন। একবার বললেন যে ভোরে বেড়ালে শরীর ভাল থাকে। সে সময় বেলেঘাটা অঞ্চলে লেক(সুভাষ সরোবর) তৈরীর কাজ চলছিল।
একদিন ভোরে আমরা লেকে বেড়াতে গিয়েছিলাম।তখন ছিল শীতকাল। সে সময় সবসময় জুতো মোজা পরার অভ্যাস ছিল না। লেকের শিশির ভেজা ঘাসে খালি পায়ে হাঁটতে গিয়ে মনটা ভীষন খারাপ হয়ে গেল। মনে পড়ে গেল মামাবাড়ির গ্রামের কথা।
শীতকালই শুধু নয়, মনে পড়ে গেল সেখানকার সবকিছু। এমন হলে ঘোরটা ক’দিন কাটতে চাইত না।
ছোটবেলাটা দিদিমার সান্নিধ্যে কেটেছে, শুধু স্নেহযত্নই পেয়েছি তা নয় শিখেছি অনেককিছুই। তার মধ্যে চিঠি লেখা একটি।
সেই শিক্ষাটা কাজে লেগেছিল সেইসময়। তবে এসব কথা এখন নয়, পড়ে কোন সময় হবে।
একসময় হিন্দুস্থানের স্থায়ী নাগরিক হলাম।
দাদুর মৃত্যুর বছর তিনেকের মধ্যেই জ্যেঠামশায়ও চলে গেলেন। নানা কারনে আমাদের কলকাতা ছাড়তে হল। কোন্নগরে কয়েক মাস থাকার পর চন্দন নগর। সেই সময়টা আমি অবশ্য আবার কলকাতায় মামার বাড়ির বাসিন্দা ছিলাম পড়াশোনার খাতিরে।
পড়া শেষ করার পর চলে এলাম বর্ধমান জেলার প্রান্তসীমায় আধাসরকারি সংস্থায় চাকুরি নিয়ে। স্থিত হলাম সংস্থার কোয়ার্টারে। পরে সেখানেই একটা বাড়ি করে বুড়োবুড়ি আছি।
বয়স হয়ে গেছে। এভাবে থাকাটা কতটা যুক্তিসম্মত সেটাও ভাবার বিষয়। সুতরাং আবার কোন নতুন আস্তানার খোঁজে বেরোতে হবে কিনা কে জানে! যাযাবরবৃত্তির একশেষ।
কোথাও শিকড় গাড়া হল না।
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)
লিখেছেন – সন্তোষ কুমার রায়


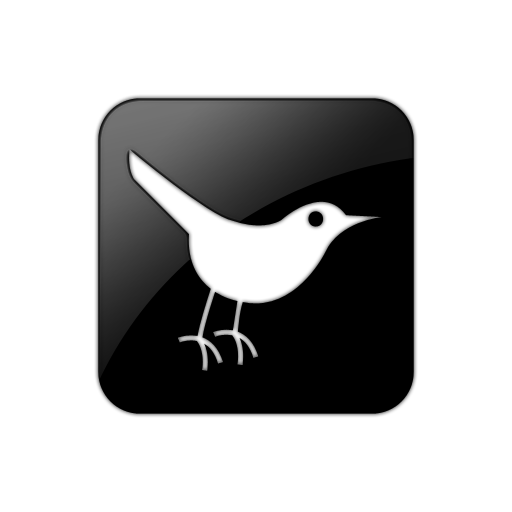
সরদার ফারুক said
আপনার লেখা পড়ে চোখে জল এসে গেল।যারা মানুষের শেকড় উপড়ে নেয়-তাদের জন্য আমার সবটুকু ঘৃণা।