উন্নয়ন, বিভাজন ও জাতি : বাংলায় নমশূদ্র আন্দোলন, ১৮৭২-১৯৪৭
Posted by bangalnama on August 31, 2009
১
জাতিবিভাগ, শ্রেণী আর ক্ষমতার সম্পর্কের মধ্যে প্রাক-ঔপনিবেশিক বাংলার সনাতন হিন্দু সমাজে যে ভারসাম্য ছিল (রায়, ১৯৮০, পৃঃ ৩২৪-২৫; সান্যাল, ১৯৮১, পৃঃ ১৯-২৬), ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকার নতুন নতুন সুযোগ-সুবিধা তৈরি করতে থাকলে তা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। সাধারণ ধারণা এই যে ভূমি বিক্রেয় পণ্যে পরিণত হলে, প্রথাবদ্ধ উৎপাদন সম্পর্কের জায়গা নেয় চুক্তিবদ্ধতা। নতুন পেশার সৃষ্টি হল, যার ভিত্তি ব্যক্তিগত যোগ্যতা। যে সব বণিক সম্প্রদায়ের বাণিজ্যকর্ম এতদিন আঞ্চলিকতার সীমায় আটকে ছিল, তারা এবার বিভিন্ন ইউরোপীয় কোম্পানির সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে বাণিজ্য করে অবস্থার উন্নতি ঘটানোর সুযোগ পেল। আর তা বিভিন্ন জাতির মধ্যে প্রাচুর্যের বন্টনকেও বিষমীকৃত করে। এরই পরিণতি, সামাজিক গতিশীলতার বৃদ্ধিতে সমাজে ক্ষমতার সম্পর্ক ভেঙে পড়ার উপক্রম। কিন্তু যদি আদমসুমারির পেশা-সংক্রান্ত তথ্যকে সমাজের কিছু সাধারণ পরিবর্তনের সূচক হিসেবে গ্রহণ করি, যদিও সামাজিক পরিবর্তনের নির্ভরযোগ্য ছবি এর থেকে আদৌ পাওয়া যায় না (কনলন, ১৯৮১), তাহলে আমরা দেখব যে বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও (১৯০১-১৯৩১) এই সামাজিক গতিশীলতা ছিল অত্যন্ত সীমিত, সমাজের একেবারে নিচের তলা থেকে কেউ ওপরে উঠে আসছে এ ঘটনাও দুর্লভ।
জনসংখ্যার এক বিশাল অংশ তখনও তাদের জাতিভিত্তিক পেশাতেই নিয়োজিত, অর্থাৎ ঔপনিবেশিক শাসনপর্বে সীমিতভাবে যে উন্নয়ন প্রক্রিয়ার শুরু তা গোষ্ঠীসাপেক্ষে স্বতন্ত্র প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্যভাবে দেখলে অর্থনীতি সমষ্টিগত উন্নয়নের গতি কখনো অর্জন করেনি বলেই একই জাতির মধ্যে তৈরি হয়েছে অন্য শ্রেণীরেখা। অর্থনীতির এই অসম সঞ্চালন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ এই ঘটনাটিই একদিকে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে – অন্যদিকে তা উনিশ শতকের শেষ আর বিশ শতকের আরম্ভে নিম্নবর্ণের জাতিগুলির সামাজিক আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কারণ হয়েই তার ওপর প্রভাব ফেলেছে।
বস্তুত এই সময় গোটা ভারতবর্ষেই প্রতিটি জাতির মানুষ ধর্মীয় মর্যাদার দিক থেকে একই অবস্থানে থাকলেও, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে বিভাজিত হয়ে পড়েছিল। কিছু কিছু তথ্যভিত্তিক আলোচনায় একথা উল্লিখিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই বিভাজন প্রক্রিয়ার সঙ্গে এইসব জাতিগুলির সামাজিক জাগরণ এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের সম্পর্কটি যে কি তা এখনও সম্যকভাবে বিশ্লেষিত হয়নি। এইসব আন্দোলনগুলিকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়েছে হয় অর্থনৈতিক উন্নতি কিংবা সামাজিক উচ্চাশার কারণ দেখিয়ে১, অথবা সামাজিক অত্যাচার এবং বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রতিফলন হিসেবে২। এইসব আন্দোলনের মধ্যে প্রতিবাদের যে ধারাটি ছিল প্রথমোক্ত ব্যাখ্যায় তা একেবারেই উপেক্ষিত। অন্যদিকে প্রতিবাদী দিকটিকেই যাঁরা বড় করে দেখেন তাঁরা দেখতে পান না যে প্রতিষ্ঠিত সামাজিক আদর্শবাদের চাপে এইসব প্রতিবাদী নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির কল্পনার জগত হয়ে পড়েছিল অত্যন্ত সীমিত। আবার তাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিরা প্রায়শই প্রতিপক্ষের সঙ্গে যোগ দেওয়ায় প্রতিবাদও হত অনেকাংশে নিষ্ক্রিয়।
অন্যভাবে বলতে গেলে, এই দুই ধরণের ব্যাখ্যাই একটি মূল ভাবনার উপর প্রতিষ্ঠিত। তা হল যে প্রতিটি জাতির মানুষেরা অন্তত চেতনার দিক দিয়ে এক এবং অভিন্ন ছিল। এই বিভেদহীন ‘সম্প্রদায়’-এর ধারণাটি সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে, কারণ এইসব আন্দোলনগুলির মধ্যে আমরা শুধুমাত্র সামাজিক উচ্চাশা অথবা শুধুমাত্র প্রতিবাদ দেখিনা। বরং এই দুটি ধারারই সম্মেলন দেখি যে কোন বিশেষ আন্দোলনের মধ্যে, এবং তা প্রতিফলিত হয় একই জাতের অন্তর্গত বিভিন্ন স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর চেতনায়। একমাত্র এই ধরনের সম্মিলন ঘটলেই ‘সম্প্রদায়’ গঠন এবং তার সামাজিক সীমারেখাগুলির চিহ্নিতকরণ সম্ভবপর হত। এটি একটি সর্বৈব জটিল প্রক্রিয়া, – এই সব বিভিন্ন সম্প্রদায় অন্তর্বর্তী ভিন্নতা সত্তেও ধর্মীয় বৃত্তে তাদের মর্যাদাহীনতাকেই নিজেদের সমতার ভূমি হিসেবে চিহ্নিত করে ‘সমষ্টিগত চেতনা’র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগ নেয়। আর এই ‘সমষ্টিগত চেতনা’কে রূপায়িত করতেই ‘সম্প্রদায়’ – নিজ গোষ্ঠীর অতীত উদ্ভাবন করে, ভ্রাতা ও গুরুর কল্পনা ক’রে তা নিয়ে গল্প-গাথা রচনা করে, ব্যবহৃত হতে থাকে ভাষিত বা ভাষাতীত প্রতীক। আসলে আত্মপ্রতিষ্ঠার সন্ধানে এইসব অবদমিত জাতির প্রথম কর্তব্য ছিল প্রতিষ্ঠিত সামাজিক সম্মানের বেড়াজালকে ভাঙা। ফলত, সম্মানিত সামাজিক অবস্থানের ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবর্গের সঙ্গে সহিংস বা অহিংস সংঘাত প্রায় বাধ্যতামূলকভাবেই ঘটে যেত। আর এইসব সংঘাতের মধ্যে দিয়েই ‘সম্প্রদায়’ সমাজের অন্যান্যদের থেকে স্বতন্ত্র বলে চিহ্নিত হতে থাকে।
কিন্তু এইসব সংঘাতের দৃষ্টান্তের উপরেই বেশি জোর দিলে ‘সম্প্রদায়’ গুলির ভেঙে পড়া, বা তাদের আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়া বা আপোস-বোঝাপড়ার অনাটকীয় মুহূর্ত থেকে মনোযোগ সরে আসতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে, কোনো একটি বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তে একটি জাতির অন্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠীর নানা ধরণের চেতনা তাদের উচ্চাশা অথবা অভিযোগ একই ধারায় এসে মিলে গেলেও অন্য কোনো অবস্থায় আবার যে পৃথকীকরণ ঘটবেনা অথবা ‘সম্প্রদায়’ ভেঙে পড়বেনা তার কোনো কথা নেই। সেই জাতির লোকজনের উপর অর্থনৈতিক উন্নয়ন-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধরণের প্রভাবের ফলে তা ঘটতে পারে, যে কারণে সাম্প্রদায়িক নেতৃত্ব আর তাদের আদর্শবাদ সবার ওপরে চাপিয়ে দিতে পারে না। আবার এটা ঘটতে পারে অন্য কোনো ধরণের সামাজিক-রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফলে, যে কারণে সামাজিক সীমারেখাগুলি নতুনভাবে চিহ্নিত হয় এবং একই জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের আত্মচেতনা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা যদি কোনো বিশেষ ঐতিহাসিক মুহূর্তের দিকে তাকাই তাহলে হয়ত কোনো জাতি বা সম্প্রদায়কে এক এবং অভিন্ন বলে মনে হতে পারে। কিন্তু যদি কোনো জনগোষ্ঠীকে দীর্ঘ সময় ধরে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে দেখা যায়, অথবা তাদের ঔপনিবেশিক যুগের বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার সম্মুখীন হতে দেখা যায়, তাহলেই একমাত্র সম্প্রদায় গঠনের উত্থান-পতনের সবদিকগুলি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। যে বিষয়টি বর্তমান প্রবন্ধে পরিষ্কার করে বলতে চাওয়া হয়েছে, তা হল এই ধরণের কোনো আন্দোলনই, বিশেষ করে ১৮৭২ সাল থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যে বাংলায় নমশূদ্র আন্দোলন, কখনওই এক ধারায় বয়ে চলেনি। এই আন্দোলনের মধ্যে যা আমরা দেখি তা’হল বিভিন্ন স্তরের চেতনা এবং বিভিন্ন ধরণের কার্যধারার সংমিশ্রণ।
২
সংখ্যার দিক থেকে নমশূদ্ররা ছিল পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে বড় হিন্দু জাতি, আর সমগ্র বঙ্গ প্রদেশে তাদের স্থান ছিল দ্বিতীয় (৯.৮ শতাংশ)। প্রধানত, পূর্বাঞ্চলের ছ’টি জেলায়, বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, ময়মনসিংহ, যশোর আর খুলনা ছিল মুখ্য নমশূদ্র বসতি; ১৯০১ সালে নমশূদ্র জনসংখ্যার (১,৮৫২,৩৭১) ৭৫ শতাংশই বাস করত এই ক’টি জেলায়। আর এই ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে আবার সবচেয়ে বেশি লোক বাস করত উত্তর-পশ্চিম বা খরগঞ্জ ও দক্ষিণ ফরিদপুরের জলা জায়গায় আর তার সংলগ্ন যশোর জেলার নড়াইল ও মাগুড়া মহকুমায় এবং খুলনা জেলার সদর ও বাগেরহাট মহকুমায়। সারা বাংলার নমশূদ্র জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেকই বাস করত এই নির্দিষ্ট অঞ্চলটিতে,৩ তাই সঙ্গত কারণেই এটিকে আমরা নমশূদ্র-প্রধান বসতি অঞ্চল বলে চিহ্নিত করতে পারি। এই বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান, যার প্রধান কারণ সম্ভবত ছিল তাদের কৌম ইতিহাস৪, সম্প্রদায় হিসেবে তাদের শক্তির অন্যতম প্রধান উৎস ছিল। ১৯৪৭-এর দেশবিভাগের ফলে এই অঞ্চলটি পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে, এদের আন্দোলনও ভেঙে পড়তে থাকে।
বাঙালি হিন্দুদের মধ্যে নমশূদ্রের সামাজিক অবস্থান ছিল খুবই নিচের দিকে। এরা একসময় ‘চন্ডাল’ নামে অভিহিত হত এবং প্রাচীন শাস্ত্রমতে চন্ডালরা অস্পৃশ্য বলে পরিগণিত হত (ঝা, ১৯৮৬-৮৭, পৃঃ ১-৩৬)। কিন্তু সঠিক অর্থে অস্পৃশ্যতা বাংলার সমাজে কখনই খুব বড় সমস্যা ছিল না। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর পুরাণে বাংলার চন্ডালদের অন্ত্যজ এবং সংকরজাতি বলে বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু সত্যি সত্যি তাদের অস্পৃশ্য বলে অবজ্ঞা করা হত কিনা আর কোনো ইঙ্গিত নেই৫। এমন কি ষোড়শ শতকের বাংলার সবচেয়ে গোঁড়া স্মৃতিকার রঘুনন্দন-ও চন্ডালদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক এবং পংক্তিভোজন এড়িয়ে চলার কথা বলেছেন কিন্তু তাঁদের স্পর্শ সর্বতোভাবে এড়িয়ে চলতে হবে এমন কথা জোর দিয়ে বলেন নি (চক্রবর্তী, ১৯৭০, পৃঃ ৩৩, ২৫৬-৬১)। ষোড়শ-অষ্টাদশ শতকের মঙ্গলকাব্যগুলিতে উল্লেখ আছে যে চন্ডালরা গ্রাম বা নগরের মধ্যেই বাস করত। মনু যাদের অন্তেবাসী বলে বর্ণনা করেছেন–অর্থাৎ যারা গ্রাম বা নগর সীমান্তের বাইরে বাস করে–চন্ডালরা মোটেই তা’ ছিল না।৬ বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও বেশ কয়েকটি তথ্যানুসন্ধানে প্রকাশ পায় যে বাংলায় তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিগুলি ভারতের অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় কম যন্ত্রণা ভোগ করত।৭ এই কারণেই হয়ত অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় বাংলায় নিম্ন বর্ণের সামাজিক-আন্দোলনগুলিও ছিল অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর।
এতদ্সত্ত্বেও বাংলায় চন্ডালজাতির লোকেদের নানা ধরণের সামাজিক অবিচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে, আর এর ফলেই সুবিধাবাদী উচ্চবর্ণের লোকেদের সঙ্গে এই সব মানুষের এক বিরাট দূরত্ব তৈরি হয়ে যায়। উচ্চবর্ণের মানুষ কাজে না হলেও মুখে সর্বদাই অস্পৃশ্যতার পক্ষপাতী ছিলেন, বিশেষত সামাজিক প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্যই (পালিত, ১৯১৫, পৃঃ ২-৩) এই প্রচার তাঁরা চালাতেন। এই সামাজিক দূরত্ব আরও বেড়ে যেত এই সব অঞ্চলের বিশেষ শ্রেণী-বিন্যাসের জন্য। ১৯১১ সালে উপার্জনশীল নমশূদ্রের ৭৮ শতাংশ নির্ভর করত কৃষিকাজের ওপর। এই কৃষিজীবী মানুষদের মধ্যে মাত্র ১.১৫ শতাংশ নিজেরা খাজনা পেত; আর বাকিদের ‘কৃষি-শ্রমিক’, ‘চাষি’ অথবা ‘জনমজুর’ ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত করা হয়েছে আদমসুমারির রিপোর্টগুলিতে। অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ থেকেও জানা যায় এদের বেশির ভাগই ছিল প্রজাস্বত্বভোগী কৃষক, যাদের কারো দখলিস্বত্ব ছিল, কারোর ছিল না, আর বাকিরা ছিল ভাগচাষি বা বর্গাদার, ১৯২০-র দশকে যাদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। কিন্তু তার চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল এই অঞ্চলে জমির ওপর একচেটিয়া দখলদারি ছিল হয় উঁচুজাতের বর্ণ হিন্দু অথবা সৈয়দ মুসলমানদের হাতে। ঢাকা, রাজশাহী এবং চট্টগ্রাম ডিভিশনে, যেখানে নমশূদ্ররা প্রধানত বাস করত, সেখানে ‘খাজনাভোগী’দের ৮০-৮২ শতাংশ ছিল ওই দুই সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, আর মাত্র ৩.৭৮ শতাংশ ছিল নমশূদ্র। বাংলার কৃষিসমাজে সবচেয়ে বড় যে বিভেদ তা হল ‘খাজনাভোগী’ এবং ‘খাজনা প্রদানকারী’দের মধ্যে, আর এই ক্ষেত্রে তা নিখুঁতভাবে মিলে গিয়েছিল জাতিভেদের সঙ্গে। এই বিভেদ ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলত নানা ধরনের অত্যাচারের ফলে। তার মধ্যে ছিল মধ্যস্বত্বভোগীদের শোষণ, বেআইনি কর আদায়, খাজনার বৃদ্ধি এবং সর্বোপরি সহজ নগদ খাজনার বদলে উঁচুহারে শস্য-খাজনা আদায় করা। কিন্তু এই অবস্থা থেকে এটাও বোঝা যায় যে, সম্প্রদায়টির মধ্যে সামাজিক পৃথকীভবন ঘটছিল, কারণ একটি ছোট গোষ্ঠী সামাজিক মর্যাদার সঁিড়ি বেয়ে ক্রমশ ওপরে উঠছিল, প্রধানত এই অঞ্চলে ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে যে কৃষির সম্প্রসারণ ঘটছিল তার সুযোগ নিয়ে। এঁদের মধ্যেই কেউ কেউ মহাজনি ও অন্যান্য নানা ধরনের ছোট ব্যবসা শুরু করেন এবং পরে শিক্ষা এবং অন্যান্য পেশায় নিয়োজিত হতে শুরু করেন। তবে যদি আদমসুমারির বৃত্তি-সংক্রান্ত পরিসংখ্যানকে আদৌ বিশ্বাস করা যায়, তবে ১৯১১ সালে এই বর্ধিষ্ণু গোষ্ঠী গোটা নমশূদ্র জাতির ২ শতাংশেরও কম ছিলেন।৮
আমরা তাই সম্ভবত মনে করতে পারি যে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে আড়াআড়ি বিভাজনটা তখনও পর্যন্ত এমন কিছু তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠেনি যাতে তাঁদের আভ্যন্তরীণ ঐক্য ক্ষতিগ্রস্ত হয় অথবা একটি সাধারণ গোষ্ঠীচেতনার উদ্ভব ব্যাহত হয়। কৃষকেরা এই অঞ্চলের শোষণকারী উঁচুজাতের লোকেদের থেকে পৃথক হয়ে ছিলেনই, বর্ধিষ্ণু ব্যক্তিরাও সংখ্যার দিক দিয়ে ছিলেন এত খগ, অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ছিলেন এত দুর্বল এবং সামাজিক মর্যাদার দিক দিয়ে ছিলেন এত নিচের দিকে, যে তাঁরাও উঁচুজাতের ভদ্রলোকেদের সঙ্গে নিজেদের একাত্ম করে ভাবতে পারতেন না। আর সেই সঙ্গে এঁদের নবলব্ধ আর্থিক অবস্থা এঁদের সামাজিক মর্যাদার অসঙ্গতি সম্বন্ধে আরও বেশি সচেতন করে তুলেছিল। অন্যদিকে এই সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষদের মধ্যেও এক নতুন আত্মমর্যাদাবোধের সৃষ্টি হয়েছিল। কারণ একদিকে তাঁরা বিল অঞ্চলের বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে অনবরত যুঝতে যুঝতেই নিজেদের স্থিতিশীল কৃষক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। অন্যদিকে বেশ কিছু উদারপন্থী ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সংস্পর্শেও এসেছিলেন, যেমন গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় অথবা কর্তাভজা সম্প্রদায়, অথবা অষ্টাদশ শতকের স্থানীয় ধর্মগুরু শাহলাল পীর, যাঁরা সবাই জাতপাতের বাধা অস্বীকার করে সর্বমানবের মধ্যে সাম্যের বাণী প্রচার করে আসছিলেন (বেভারিজ, ১৮৭৬, পৃ. ২৬০-৬৫, যসিমুদ্দিন, ১৯৭৭, পৃ. ৩৬-৪২, ২৫৯, ২৬২)। কাজেই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে দুটি গোষ্ঠীর স্বার্থ ও আকাঙ্ক্ষা আলাদা হলেও উঁচুজাতের ক্ষমতা ও আধিপত্যকে অস্বীকার করা এবং চূর্ণ করার একটি সম্মিলিত অভিলাষ ছিল। এই অভিলাষই তাঁদের ক্রমশ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূলস্রোতের থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, কারণ বাংলায় এই রাজনীতিতে ছিল উঁচুজাতের হিন্দু ভদ্রলোকেদের একচেটিয়া প্রভাব। এই বিচ্ছিন্নতাবোধের উৎসে ছিল এমন এক আদর্শবাদ যা অতীত এবং বর্তমান বিষয়ে তাঁদের নিজস্ব ধারণার জাতক, অপরপক্ষে তা জাতীয়তাবাদী ধারণা থেকে সবিশেষ স্বতন্ত্র।
৩
নমশূদ্রদের এই সামাজিক আন্দোলন শুরু হয় ১৮৭২-৭৩ সালে ফরিদপুর-বাখরগঞ্জ অঞ্চলে। এই অঞ্চলের এক বিশিষ্ট নমশূদ্র গ্রামীণ নেতার মায়ের শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে উঁচুজাতের লোকেরা আসতে অস্বীকার করলে তাদের সঙ্গে সমস্ত রকম সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করা হয়। এই সামাজিক বর্জনের আন্দোলন প্রায় ছ’মাস ধরে চলে। এই সময়ে কৃষিকাজে, ঘর ছাউনি দেওয়ার অথবা অন্য কোনোরকম কাজে উঁচুজাতের লোকেদের সঙ্গে কোনোরকমভাবে সহযোগিতা করতে নমশূদ্ররা অস্বীকার করে (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৮৯, পৃ. ১৮৩-৮৪)। এই আন্দোলন অবশ্য বেশি দিন চালিয়ে নিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। আর এই প্রথম অসাফল্যের পরেই এদের মধ্যে উদ্ভব হয় এক সংগঠিত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের, যার নাম হল মতুয়া। এই সম্প্রদায় তার সামাজিক ধ্যান-ধারণা, রীতি-নীতি এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত ধারণা আহরণ করেছিল প্রচলিত বৈষ্ণব ধারা থেকে। কিন্তু তাদের চিন্তায় এই ধ্যান-ধারণাগুলি এমন এক নিজস্বতা লাভ করে যাতে এগুলির সাহায্যে প্রচলিত ক্ষমতার সম্পর্ককে সার্থকভাবে মোকাবিলা করা যায়। এদের প্রধান ধর্মগুরু শ্রীগুরুচাঁদ ঠাকুর, জন্মেছিলেন এক বর্ধিষ্ণু কৃষক পরিবারে। অন্যান্য বৈষ্ণবগুরুদের মতন তিনিও প্রচার করেছিলেন ব্যক্তিগত ভক্তি, জাতিভেদের অবসান ও সর্ব-সাম্যের মতাদর্শ। কিন্তু তার ওপরেও তিনি যা প্রচার করেছিলেন তা হল এক কর্মের নীতি যা একটি সামাজিক গতিশীল সম্প্রদায়ের উচ্চাশা পূরণে সহায়ক হতে পারে। বাঙালি ভদ্রলোক সমাজ যখন রামকৃষ্ণের প্রভাবে বেদান্তের কথা ভাবছে অথবা পার্থিব সম্পদ বর্জন করে আধ্যাত্মিক মুক্তির কথা ভাবছে, গুরুচাঁদ তখন তাঁর শিষ্যদের শিক্ষিত হয়ে অর্থ উপার্জন করে সম্মানীয় হয়ে উঠতে বলছেন। ‘হাতে কাম মুখে নাম’, অর্থাৎ পার্থিব দায়িত্ব পালনের মধ্যে দিয়েই মুক্তিলাভ, এই ছিল তাঁর ভক্তদের প্রতি গুরুর উপদেশ, যাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন জাতে নমশূদ্র। উঁচুজাতের বৈষ্ণবরা তাঁদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে অস্বীকার করলে মতুয়া ভক্তদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ ঐক্য আরও বেড়ে যায়। আর এই সংগঠন ও ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা আরও গুরুত্ব পায় গুরুর উপদেশে। ‘যার দল নেই তার বল নেই’, তাঁর এই শিক্ষায় সম্প্রদায় গঠন করে সমষ্টিগত প্রয়াস চালানর কথাই প্রকাশ পেয়েছিল। এই সম্প্রদায়ের একমাত্র নিত্যকর্ম ছিল কীর্তনগান। এই সমবেত কীর্তনগান এবং সম্মিলিত ভক্তি সম্প্রদায়ের সমষ্টিগত চরিত্রকে জোরদার করত। এছাড়াও অন্যান্য নিয়মিত সম্মেলন– যেমন বারুণী মেলা– ভক্তদের মধ্যে অদিকতর সামাজিক আদান-প্রদানের সহায়ক হত (সরকার, ১৯১৬ ; ম. হালদার, ১৯৪৩ ; ন. হালদার, ১৯৮৫, ১৯৮৬ ; পৃ. হালদার, ১৯৮৬)।
এই মতুয়া ধর্মসম্প্রদায়কে কেন্দ্র করেই ঊনবিংশ শতকের শেষে নমশূদ্রদের সামাজিক আন্দোলন শুরু হয় এবং গুরুচাঁদ ঠাকুরের পৈতৃক গ্রাম, ফরিদপুর জেলার ওড়াকান্দি হয়ে ওঠে এই আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্র। এই ধর্মসম্প্রদায় ছাড়াও ১৯০২ সালে একটি সমিতি গঠন করা হয় এবং জাতি-আন্দোলনের বার্তা ছড়িয়ে দেবার জন্য নিয়মিত ‘উন্নয়নী সভা’-র আয়োজন করা হতে থাকে। এছাড়া প্রচারের জন্য অন্যান্য মাধ্যমও ব্যবহার করা হত, যেমন যাত্রা-অনুষ্ঠান অথবা প্রতিটি পরিবার থেকে সাপ্তাহিক ‘মুষ্ঠি’ সংগ্রহ। এরপর ১৯১২ সালে প্রতিষ্ঠিত Bengal Namasudra Association ও তার জেলা শাখাগুলির মাধ্যমে এই আন্দোলন পুরোপুরিভাবে সংগঠিত হয়ে ওঠে।৯
এই আন্দোলন যত এগোতে থাকে ততই কিন্তু এর মধ্যে চেতনার দুটি স্তর এবং কার্যাবলীর দুটি ধারা প্রকট হয়ে উঠতে থাকে–এর একটি স্তর হল সম্ভ্রান্ত নেতৃবৃন্দের, আর অন্যটি হল তাদের কৃষক অনুগামীদের। নেতৃবৃন্দের প্রধান দাবি ছিল পুরোনো অসম্মানজনক ‘চন্ডাল’ নামের পরিবর্তে তাঁদের নতুন ‘নমশূদ্র’ নামের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন। ১৯১১-র আদমসুমারিতে শেষ পর্যন্ত এই চন্ডাল নাম মুছে যায়। এছাড়াও তাঁরা নানারকম সাংস্কৃতিক প্রতীক ধারণ করতে থাকেন, যাতে তাঁদের সামাজিক মর্যাদা সূচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, তাঁরা নিজেদের ব্রাহ্মণ বলে দাবি করতে থাকেন এবং তার স্বপক্ষে শাস্ত্রীয় প্রমাণ দাখিল করেন। পরিবারের মহিলাদের বাজারে যাওয়া বন্ধ করেন। এগার দিন অশৌচ পালন করতে থাকেন এবং সর্বোপরি উপবীত ধারণ করাও আরম্ভ হয়।১০ ‘Sanskritisation’ বা সংস্কৃতায়ণের সে তত্ত্ব আছে তা দিয়ে এই ব্যবহারকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায় না, কারণ এই তত্ত্বে প্রতিবাদের দিকটিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়ে থাকে। আসলে এই নিম্নবর্ণের লোকেরা যা করছিলেন তা হল ক্ষমতার প্রতীক কতগুলি চিহ্নকে ধারণ করে সেগুলিকে অর্থহীন করে দেওয়া। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সমাজে ক্ষমতার যে সর্বোচ্চ প্রতীক সেই উপবীত এই নিচু জাতের লোকেরা গ্রহণ করতে শুরু করলে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে বাঙালি ভদ্রলোকেরা একে ‘সিকি পয়সার সুতো’ বলে বর্ণনা করতে শুরু করেন (রায়, ১৯২৬, পৃ. ৪৯৩)। সম্ভ্রান্ত নমশূদ্রদের এই প্রতিবাদ কিন্তু পুরোপুরি সচেতনভাবে না হলেও, এক ধরণের সমঝোতা অথবা প্রচলিত আচার-ব্যবস্থাকে মেনে নেওয়ার মধ্যে দিয়ে শেষ হয়। নিজেদের বর্ধিত সামাজিক এবং ধর্মীয় পদমর্যাদাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে সব পৌরাণিক উপাখ্যানের অবতারণা তঁারা করছিলেন তার প্রত্যক্ষ উপাদান ছিল সেই হিন্দুশাস্ত্র। আর এই কাহিনীগুলিকে এমনভাবে রচনা করা হচ্ছিল যার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে সমাজে উঁচু-নিচু-র বিভেদ ঘুচিয়ে ফেলা অথবা আচার-বিচারের জগৎটাকে সম্পূর্ণ উল্টে ফেলার উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। প্রচলিত কাঠামোর মধ্যে নিজেদের উচ্চ সামাজিক পদমর্যাদার স্বীকৃতিটুকুই তাঁরা চাইছিলেন (বাঢ়োই বিশ্বাস, ১৯১১, পৃ. ৪৫-৫৩ ; শর্মা, ১৯১৩, পৃ. ৬-৯)।
আরও বৈষয়িক স্তরে নমশূদ্র নেতারা বুঝতে শুরু করেছিলেন যে সম্প্রদায়ের অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন হল শিক্ষা এবং চাকরি। কারণ এগুলিই হল সামাজিক মর্যাদার নতুন উৎস। উঁচু জাতের লোকেদের সঙ্গে অসম প্রতিযোগিতা এবং নানা ধরণের খোলাখুলি অথবা প্রচ্ছন্ন পক্ষপাতিত্বই ছিল শিক্ষা ও সরকারী চাকরিতে তাঁদের পিছিয়ে থাকার কারণ। কাজেই ১৯০৬ সাল থেকে ঔপনিবেশিক সরকার মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রতি যে পক্ষপাতমূলক সহায়তার নীতি চালু করেছিলেন তা নমশূদ্র নেতাদেরও ওই ধরনের সুযোগ ও সুবিধা দাবি করার ব্যাপারে উৎসাহিত করে তোলে। ১৯২০-র দশকে এবং ১৯৩০-এর দশকে গোড়ার দিকে এই ধরনের শিক্ষা ও চাকরি সংক্রান্ত কিছু সুবিধা-সুযোগ তাঁদের দেওয়াও হল। কিন্তু তাতেও তাঁদের সম্প্রদায়ের অবস্থার কোনো উন্নতি হল না, কারণ স্থানীয় আমলারা এই ধরনের নিয়ম-কানুন প্রায়শই অমান্য করতেন।১১
নমশূদ্র নেতৃত্বের অন্য অসন্তোষের কারণ ছিল প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে অংশগ্রহণ করতে না পারা। স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলিতে তাঁদের প্রতিনিধিত্ব খানিকটা বাড়লেও, প্রাদেশিক আইনসভায় তাঁদের প্রতিনিধিত্ব ছিল একেবারেই নগণ্য। একদিকে এই প্রতিনিধিত্বহীনতা ও অন্যদিকে ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা হস্তান্তর এইসব নেতাদের উঁচুজাতের স্বৈরাচারী শাসন সম্বন্ধে ভীত করে তুলল। অতএব, মন্টাগু-চেম্সফোর্ড সাংবিধানিক সংস্কার প্রস্তাব ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই ১৯১৭ এবং ১৯১৮ সালে দুটি সম্মেলনে তাঁরা ‘সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের’ দাবি তুললেন, যাতে পশ্চাদ্পদ জাতিগুলির ভবিষ্যৎ উন্নতি ব্যহত না হয়।১২ এর ফলস্বরূপ ১৯১৯ সালের সংস্কার আইনে বঙ্গীয় প্রাদেশিক আইনসভায় অনুন্নত শ্রেণীর একজন প্রতিনিধির মনোনয়নের নীতি স্বীকৃত হয়। কিন্তু এই একজন প্রতিনিধি ছাড়া, এই বিশাল অনুন্নত শ্রেণীর প্রতিনিধিত্বের আর কোনো উপায় ছিল না। নমশূদ্র অধ্যুষিত কেন্দ্রগুলি থেকে নির্বাচিত হতে থাকেন সেই বর্ণহিন্দু প্রার্থীরাই।
আর এইভাবে রাজনৈতিক উচ্চাশাপূরণে ব্যর্থ হলে নমশূদ্র নেতৃত্বের মনে ব্রিটিশ রাজের প্রতি একধরণের আনুগত্য জাগল আর সেই সঙ্গে সৃষ্টি হল জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সম্বন্ধে একটা সন্দেহ, কারণ এই আন্দোলন উঁচুজাতের হিন্দু ভদ্রলোকেদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠেছিল। তবে তাদের এই রাজনৈতিক অবস্থানের মূলে ছিল এক আদর্শবাদ, যা গড়ে উঠেছিল ঔপনিবেশিক শাসনের চরিত্র সম্বন্ধে তাদের ধারণা এবং নিজস্ব ইতিহাসবোধ থেকে, যা জাতীয়তাবাদীদের চিন্তাধারা থেকে একেবারেই আলাদা। জাতীয়তাবাদীরা ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠাকে দেখতেন এক স্বর্ণময় যুগের অবসান হিসেবে, আর নমশূদ্রদের চোখে বর্তমান শাসনব্যবস্থা ছিল সেই অতীতের চেয়ে অনেক বেশি উন্নত। কাজেই তাঁদের কাছে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে কোনো আন্দোলনই হয়ে ওঠে ইতিহাসকে পশ্চাদমুখী করে তোলার সামিল–ঘড়ির কাঁটাকে পিছনের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। এই আন্দোলনগুলিকে তাই তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের স্বার্থের পরিপন্থী বলে মনে করতেন।১৩ এই কারণেই তাঁরা স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধিতা করেছিলেন, হোমরুল আন্দোলনের সমালোচনা করেছিলেন, এমনকি গান্ধিজীর নেতৃত্বে গণআন্দোলনের যুগেও তাঁরা অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন ও ভারত ছাড় আন্দোলন থেকে দূরে সরে থেকেছেন, যদিও জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব, এমনকি গান্ধিজী নিজেও তাঁদের সমর্থন লাভ করার জন্য চেষ্টা করেছিলেন যথেষ্ট।১৪
৪
জাতীয়তাবাদী রাজনীতিকে পরিত্যাগ করার প্রবণতা শুধু যে সম্ভ্রান্ত নেতৃবৃন্দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, নিচের স্তরের মানুষদের মধ্যেও এই চেতনা সমানভাবে লক্ষ্য করা যায়, কারণ নেতারা সার্থকভাবেই কৃষকদের বুঝিয়েছিলেন যে জাতীয়তাবাদ হল উঁচুজাতের সামন্তশ্রেণীর একটি আদর্শবাদ মাত্র। স্বদেশী আন্দোলনকে এই ধরনের একটা আখ্যা দেওয়া মোটেই কষ্টকর ছিল না, কারণ এর নেতৃবর্গ ও সমর্থকরা সবাই ছিলেন ঐ শ্রেণীভুক্ত এবং তাঁরা তাঁদের ক্ষমতা যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ ক’রেই কৃষকদের এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন (সু. সরকার, ১৯৭৩, পৃ. ৩৫৫-৬০)। কৃষকেরা এই আচরণ মোটেই পছন্দ করেননি এবং এর ফলে যে বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছিল তা অসহযোগ, আইন অমান্য এবং ভারত ছাড় আন্দোলনের যুগেও একই গতিতে সক্রিয় ছিল।১৫ কিন্তু এই যোগ না দেওয়াটাকে, অথবা কখনও কখনও সক্রিয়ভাবে বিরোধিতা করাটাকে ব্রিটিশরাজের প্রতি তাঁদের আনুগত্যের প্রতিফলন বলে ধরে নিলেও ভুল করা হবে। বরং উঁচুজাতের জমিদাররা তাঁদের ওপর যে নানা ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবিচার চালিয়ে আসছিলেন এটা ছিল তার বিরুদ্ধেই এক ধরনের প্রতিবাদ, কারণ এই শ্রেণীর লোকেরাই ছিলেন রাজ-বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বে। বস্তুতপক্ষে সরকারের প্রতি নমশূদ্র কৃষকদের মনোভাব ছিল দ্ব্যর্থক। সাধারণভাবে তাঁরা কাছের অত্যাচারীদের চেয়ে দূরের শাসককেই পছন্দ করতেন বেশি, এবং প্রায়শই বাজার লুন্ঠন এবং গৃহে লুঠতরাজ চালিয়ে উঁচুজাতের ক্ষমতাশালী জমিদারদের ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন। কিন্তু সরকার যদি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার নামে জমিদারদের পক্ষ নিয়ে হস্তক্ষেপ করতেন, যেমনটি ঘটেছিল একাধিকবার ১৯০৯ সালে ফরিদপুর জেলায়, নমশূদ্র কৃষকেরা সেক্ষেত্রে পুলিশের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে দ্বিধা করেন নি। মনে রাখা দরকার, স্থানীয় কৃষকদের চেতনায় পুলিশবাহিনীই কিন্তু ছিল ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের একমাত্র প্রতিনিধি।১৬
নমশূদ্র কৃষকদের ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে যেটা সব সময়ই প্রকাশ পেত তা হল আর্থিক শোষণ মুক্তি আর সামাজিক সম্মানলাভের ঐকান্তিক ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা-পূরণের জন্য তাঁরা কখনও জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ নিয়েছেন, কখনও বা উঁচুজাতের হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলিমদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন–যেমনটা ঘটেছিল ১৯০৮-৯ সালে যশোর, খুলনা, ফরিদপুর এবং ময়মনসিংহ জেলার কিছু কিছু অঞ্চলে।১৭ আবার অবস্থান্তরে সম্প্রদায়ের সম্মান বজায় রাখার জন্য এই মুসলিমদের সঙ্গেই তাঁদের তীব্র সংঘাত ঘটেছে যার নিদর্শন আমরা দেখি যশোর, খুলনা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুর জেলার কিছু কিছু অঞ্চলে ১৯১১, ১৯২৩-২৫ এবং ১৯৩৮ সালে।১৮
নমশূদ্র কৃষকেরা তাঁদের সম্প্রদায়ের নেতাদের ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন কারণ এই নেতৃত্ব তাঁদের অভাব-অভিযোগগুলি কাজে লাগিয়ে একটি জাতি-ভিত্তিক আদর্শবাদ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। তাঁরা নিয়মিতভাবে উল্লেখ করতেন ‘নিচু জাতের কৃষকদের’ ওপর ‘উঁচুজাতের জমিদারদের’ অত্যাচার ও শোষণের কথা অথবা ‘ভদ্রলোক রাজনীতিকদের কর্তৃত্বের’ কথা এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন জনসভা ও আইনসভায় তুলে ধরতেন কৃষকদের নানা অভাব-অভিযোগের কথা।১৯ এই সমস্ত নেতারা, অন্তত মুখের কথায় হলেও, সামাজিক কর্তৃত্বের প্রচলিত কাঠামোটাকে বদলানোর কথা বলতেন ব’লে তঁাদের রাজনীতির স্বপক্ষে জনমতগঠনে তাঁরা সক্ষম হয়েছিলেন।
কিন্তু ১৯৩০-এর দশক থেকে এই নমশূদ্র নেতৃত্ব ক্রমশ তাঁদের কৃষক সমর্থকদের কথা ভুলতে শুরু করলেন। এই পরিবর্তনটা লক্ষ্য করা যায় ১৯৩০-এর খুলনা জেলা সম্মেলন থেকে, যাকে বর্ণনা করা হয়েছিল কৃষকদের নয়, তাদের শিক্ষিত ও পেশাদারি উত্তরসূরিদের সম্মেলন বলে। এই সম্মেলনেই তাঁদের নেতা গুরুচাঁদ ঘোষণা করলেন যে, সম্প্রদায়ের সামাজিক ও পার্থিব উন্নতির জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের একান্ত প্রয়োজন আছে এবং এই ক্ষমতা আদায়ের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা একান্ত জরুরি।২০ এরপর থেকে, কয়েকটি জনসভা, সরকারের কাছে একটি দুটি আবেদন অথবা আইনসভার কিছু প্রশ্ন ছাড়া,২১ এই বর্ধিষ্ণু নেতৃত্বের কর্মসূচীতে দরিদ্র কৃষকদের জন্য আর বিশেষ কিছু লক্ষ্য করা যায় না। জনসংযোগ এবং গ্রামভিত্তিক সংগঠনের ক্ষেত্রেও শিথিলতা দেখা দিতে শুরু করল। কারণ অধিকাংশ নেতাই কলকাতা-কেন্দ্রিক হয়ে গেলেন। যে সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক সুবিধা সুযোগ তাঁরা চাইছিলেন ১৯৩৫ সালের সাংবিধানিক সংশোধনে সেগুলি অনুমোদিত হলে এই সব নেতাদের কাছে জনবলের প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে যায়। ফলে সাধারণ সমর্থকদের অবহেলা করার প্রবণতাও বাড়তে থাকে, যা অত্যন্ত প্রকটভাবে চোখে পড়ে ১৯৩৭ সালের পরবর্তী পর্বে।
১৯৩০-এর গোড়া থেকেই নমশূদ্র নেতৃত্ব সাংবিধানিক রাজনীতিতে খুব বেশিভাবে জড়িয়ে পড়তে থাকেন। ‘সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা’-কে তাঁরা স্বাগত জানালেন, পুণা চুক্তিকে নিন্দা করলেন এই বলে যে তা ‘ড. আম্বেদকরের রাজনৈতিক ভুল’। আবার পরে, অকংগ্রেসী বর্ণহিন্দুরা এই চুক্তির সমালোচনা শুরু করলে, এর সমর্থনে তাঁরা ঐক্যবদ্ধ হন। তবে এই সমর্থন ছিল ‘প্রয়োজনের চাপে’, ‘স্বেচ্ছায় নয়’, কারণ এর ফলে তাঁরা পৃথক নির্বাচনের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছিলেন।২২ এইভাবে নেতাদের রাজনীতি ক্রমশ প্রতিষ্ঠান-ভিত্তিক হয়ে উঠলে তাঁদের মধ্যে গোষ্ঠী-দ্বন্দ্বও শুরু হয়ে যায় এবং ১৯৩২-এর পর থেকে আমরা দুটি সংগঠনকে নমশূদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব করতে দেখি। যে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা এই সংগঠনগুলি দাবি করছিল তাতে দরিদ্র গ্রামীণ শ্রেণীর উপকার হবার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম, কারণ সেগুলি কাজে লাগানোর মত বিদ্যা বা সঙ্গতি তাঁদের ছিল না। ফলে এই আন্দোলনের গণ-আবেদনও ক্রমশ কমতে থাকে।
এই সময় প্রজা আন্দোলন কৃষকদের জন্য এক শ্রেণীভিত্তিক কর্মসূচি তুলে ধরলে নমশূদ্র নেতৃত্বের জনসমর্থন আরও কমে যায়। বস্তুত ১৯২০-র শুরু থেকেই নমশূদ্র কৃষকেরা তাঁদের নিজস্ব দাবি আদায়ের জন্যে স্বাধীনভাবে নিজেদের সংগঠিত করতে শুরু করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে উঁচুহারের শস্য-খাজনাকে সহজ নগদ খাজনায় পরিবর্তনের দাবি,২৩ অথবা ১৯২০-র দশকে বর্গাদার বা ভাগচাষিদের তিন-চতুর্থাংশ ফসলের দাবি (ত. সরকার, ১৯৮৭, পৃ ৩৮-৪১)। এরপর আরও সুসংবদ্ধভাবে ফজলুল হকের নেতৃত্বে কৃষক প্রজা পার্টি এই সময়ে পূর্ববঙ্গের মুসলিম ও নমশূদ্র কৃষকদের সংগঠিত করতে শুরু করে। নমশূদ্র সম্প্রদায়ের কিছু নবীন নেতা, যেমন যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল অথবা বিরাটচন্দ্র মন্ডল এই নতুন প্রজা-আন্দোলনের জন্য নমশূদ্র কৃষকদের সমর্থন আদায়ের পেছনে ছিলেন। কিন্তু এই কৃষক প্রজা পার্টিও ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের প্রাক্কালে মুসলিম লীগের সঙ্গে মুসলিম ভোটের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সুবাদে তার তফসিলি জাতিভুক্ত সমর্থকদের পরিত্যাগ করেন।২৪ ফলে এবার সম্প্রদায়ের নেতৃত্বকে সমর্থন করা ছাড়া নমশূদ্র কৃষকদের সামনে আর কোনো রাস্তা ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও বেশ কিছু প্রতিষ্ঠিত নেতার ১৯৩৭-এর নির্বাচনে হেরে যাওয়া থেকেই প্রমাণ হয় যে নমশূদ্র কৃষকশ্রেণী তাঁদের নেতৃত্বের রাজনীতিকে পুরোপুরিভাবে এই সময়ে সমর্থন করছিলেন না। অন্য দিকে কংগ্রেসও এই অবস্থার সুযোগ নিতে পারেনি, কারণ ওই বছরে নির্বাচিত নমশূদ্রদের মধ্যে মাত্র একজনই ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। কিন্তু বাখরগঞ্জ জেলার নমশূদ্র অধ্যুষিত এক অসংরক্ষিত কেন্দ্রে যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল নির্দল প্রার্থী হিসেবে পরাজিত করেন কংগ্রেসের কায়স্থ প্রার্থী সরল দত্তকে, যিনি ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্তের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং সেই সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক উত্তরসুরি।২৫ তাঁদের নিজের জাতের কোনো নেতা যদি তাঁদের দুঃখের সমব্যথী হতেন, তবে তাঁকে সমর্থন করার জন্য নমশূদ্র কৃষকেরা যে কতখানি দৃঢ়সংকল্প ছিলেন, এই ঘটনা তারই প্রমাণ।
৫
প্রায় ১৯৩৭ পর্যন্ত নমশূদ্র আন্দোলন বাংলায় জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মূলস্রোতের থেকে উৎসারিত কোনো ধারা নয়, এক পৃথক সমান্তরাল চেতনার ধারা হিসেবেই চলে আসছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনকালের শেষ দশকে, ক্ষমতা হস্তান্তর যখন প্রায় নিশ্চিত হয়ে আসছে, তখন রাজনীতির মূলস্রোত সমান্তরাল এই ধারাগুলিকে আত্মস্থ করতে সচেষ্ট হয়। বাংলা যখন বিভক্ত হয় এবং ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে, নমশূদ্র আন্দোলন তখন তার পৃথগন্ন মনোভাব ছেড়ে এই প্রদেশের রাজনৈতিক মূলস্রোতের সঙ্গে মিশে গেছে। তবে এই আন্দোলনের মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন ধরণের চেতনার সহাবস্থান ছিল, এই মিশে যাওয়ার ঘটনাটিও তাই ঘটেছিল বিভিন্ন স্তরে এবং বিভিন্ন রূপে।
প্রাতিষ্ঠানিক স্তরে ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত নমশূদ্র নেতৃবৃন্দ কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব রেখেই চলছিলেন, তার প্রমাণ সে বছরের নির্বাচনী ফলাফল। তের জন সফল নমশূদ্র প্রার্থীর মধ্যে মাত্র একজন ছিলেন কংগ্রেস সভ্য এবং এইসব ‘নির্দল’ সাংসদরা ফজলুল হকের নেতৃত্বে মুসলিম লীগ-প্রজা পার্টির সম্মিলিত সরকারকে সমর্থনও জানিয়েছিলেন (বন্দ্যোপাধ্যায়, ১৯৯০ ক, পৃঃ ১৮১-৮২)। কিন্তু নতুন সরকার তফসিলি জাতির উন্নয়নের জন্য বিশেষ কিছু না করায় অচিরেই তাঁদের মোহভঙ্গ হয়২৬, এবং এই মন্ত্রীসভায় তাঁদের প্রতিনিধি মুকুন্দবিহারী মল্লিককে ১৯৩৮ সালের গোড়ার দিকে কাঁচরাপাড়ার এক জনসভায় প্রকাশ্যই সমালোচনা করা হয়২৭। কংগ্রেস এইবার এই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে তফসিলি জাতি আন্দোলনকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা শুরু করে, কারণ আইনসভায় তফসিলি জাতি সাংসদদের উপস্থিতি এবং প্রয়োজনীয়তা উপেক্ষা করার আর কোনো উপায় ছিল না। ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে গুরুচাঁদের মৃত্যু ঘটলে যে প্রভাব নমশূদ্র আন্দোলনকে কংগ্রেসি রাজনীতির থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিল তা অন্তর্হিত হয় এবং এই একই বছরে গঠিত ‘ক্যালকাটা শিডিউল্ড কাস্ট লীগ’ এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সেতুবন্ধনের কাজ শুরু করে। যে সমস্ত বিশিষ্ট নমশূদ্র নেতা এই নতুন সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে গুরুচাঁদের পৌত্র প্রথমরঞ্জন ঠাকুরের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে২৮। অন্যদিকে কংগ্রেসের পক্ষে যাঁরা এই নতুন মৈত্রীবন্ধনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন সুভাষ এবং শরৎ বসু-ভ্রাতৃদ্বয়। ১৯৩৮ সালের ১৩ই মার্চ অ্যালবার্ট হলের এক সভায় কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি সুভাষ বসু গুরুচাঁদকে বর্ণনা করেন ‘অতিমানব’ বলে, ‘যিনি বাংলার হিন্দু সমাজে এক নতুন প্রাণের সঞ্চার করে তাকে পুনর্জাগরিত করেছিলেন।’২৯ এই সভার তিনদিন পরে তফসিলি জাতির প্রায় কুড়িজন সাংসদ, যাদের মধ্যে ছিলেন প্রথমরঞ্জন ঠাকুর এবং যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, শরৎ বসুর বাড়িতে মিলিত হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করার এবং সম্মিলিত সরকারের প্রতি সমর্থন তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন৩০। তাঁরা একটি নতুন সংসদীয় দল গঠন করেন, যার নাম দেওয়া হয় Independent Scheduled Caste Party। যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল হলেন এর সচিব এবং এই দল ‘কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলবে’ বলে ঠিক হয়৩১।
১৯৩৮ সালের ১৮ই মার্চ কলকাতায় গান্ধীজীও কয়েকজন বিশিষ্ট নমশূদ্র সাংসদের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁর ব্যক্তিগত অনুরোধেই জুলাই মাসে প্রথমরঞ্জন ঠাকুর কংগ্রেস-শাষিত প্রদেশগুলি সফর করেন এবং সফর শেষে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান যে এইসব কংগ্রেসি সরকারগুলি তফসিলি জাতির উন্নয়নের জন্য যা করেছে তা দেখে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন৩২। এরপর আগস্ট মাসে হক মন্ত্রীসভার দশজন মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দশটি পৃথক কংগ্রেস-সমর্থিত প্রস্তাব আনা হয় আইনসভায়। নমশূদ্র মন্ত্রী মুকুন্দবিহারী মল্লিকের বিরুদ্ধে প্রস্তাবটি আনেন নমশূদ্র নেতা প্রথমরঞ্জন ঠাকুর এবং সমর্থন জানান আরেক নমশূদ্র নেতা যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। এই আস্থা ভোটে ভোটাভুটির নমুনা থেকে দেখা যায় যে এই সময় তফসিলি জাতিভুক্ত একত্রিশ জন এম.এল.এ-র মধ্যে অন্তত ষোল জন ছিলেন কংগ্রেস সমর্থক৩৩। নমশূদ্রদের ক্ষেত্রে এই রাজনৈতিক স্থান পরিবর্তন আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয় ১৯৩৯ সালের ২৯শে মে তমলুকের নিখিলবঙ্গ নমশূদ্র সম্মেলনে, যেখানে প্রথমরঞ্জন ঠাকুর তাঁর সভাপতির ভাষণে নমশূদ্র সম্প্রদায়কে ‘জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে’ উপদেশ দেন৩৪। পিতামহের রাজনৈতিক পৃথকীকরণের নীতির বদলে আসে পরবর্তী প্রজন্মের একীকরণের আশীর্বাদ। এদের সাহায্যই ১৯৪১ সালের অক্টোবর মাসে মুসলিম-লীগ সমর্থিত হক মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়ে ক্ষমতা দখল করে কংগ্রেস-সমর্থিত প্রগ্রেসিভ কো-অ্যালিশন সরকার, সাধারণভাবে যা ‘শ্যামা-হক মন্ত্রীসভা’ নামেই পরিচিত ছিল। রাজবংশী নেতা উপেন্দ্রনাথ বর্মন এই মন্ত্রীসভায় তফসিলি জাতির প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন (বর্মন, ১৯৮৫, পৃঃ ৮১-৮৪)।
তবে সব নমশূদ্র নেতাই যে কংগ্রেসের সঙ্গে একীকরণের নীতি মেনে নিয়েছিলেন তা নয়, বরং এই সময়ে তাঁদের আন্দোলনে একটা স্পষ্ট ভাগাভাগির চিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। যে সব নেতারা এই কয়েক বছর ধরে মুকুন্দবিহারী মল্লিককে ঘিরে সংগঠিত হচ্ছিলেন, তাঁরা তাঁদের ইংরেজ সরকারের প্রতি পার্থিব এবং নৈতিক সমর্থনের পুরোনো নীতিই ধরে রইলেন। আগের মতোই তাঁরা অধিক চাকরি এবং শিক্ষার সুযোগ দাবি করতে থাকলেন এবং মন্দিরের দ্বার উন্মোচন অথবা অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের মতো কংগ্রেসি আন্দোলনগুলির শূন্যগর্ভতা উন্মোচিত করার চেষ্টা করে চললেন৩৫। প্রস্তাবিত ক্রিপস মিশন এবং সাংবিধানিক সংস্কারের সম্ভাবনা সর্বপ্রথম মল্লিকগোষ্ঠীকে কংগ্রেস-সমর্থক ঠাকুরগোষ্ঠীর কাছাকাছি নিয়ে আসতে পেরেছিল। ১৯৪২ সালের ২৬শে মার্চ তাঁরা ঘোষণা করেন যে এক যৌথ দল দিল্লী গিয়ে স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস-এর কাছে তাঁদের দাবিদাওয়া জানাবে৩৬। কিন্তু ক্রিপস মিশন অসফল হলে এই দুই গোষ্ঠীর মধ্যে স্থায়ী সমঝোতার সম্ভাবনাও নষ্ট হয়ে যায়।
নতুন করে সন্ধিস্থাপনের সম্ভাবনা আরেকবার দেখা গিয়েছিল ১৯৪২-এর এপ্রিল মাসে, যখন কলকাতায় তফসিলি জাতির বেশ কিছু নেতা মিলিত হয়ে স্থাপন করলেন এক নতুন সংগঠন, যার নাম রাখা হল বেঙ্গল শিডিউল্ড কাস্ট লীগ, এবং যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল হলেন তার সভাপতি। প্রথম দিকে এই সংগঠন কংগ্রেস সমর্থনের নীতি বজায় রাখে এবং ভারত ছাড়ো আন্দোলনে গান্ধিজী গ্রেপ্তার হলে তার নিন্দা করে৩৭। তবে ইতিমধ্যেই সুভাষ-বসু বিতর্কের কারণে মন্ডল কংগ্রেস সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এই দূরত্ব আরো বাড়ে ১৯৪৩-এ তিনি মুসলিম-লীগ সমর্থিত নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভায় যোগদান করলে। কারণ আর সব তফসিলি নেতাই এই মন্ত্রীসভাকে ‘সম্পূর্ণ সাম্প্রদায়িক’ বলে বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন (বর্মন ১৯৮৫, পৃঃ ৮৪; মন্ডল ১৯৭৫, পৃঃ ৫১)। তবে নতুন মন্ত্রীসভায় ছিলেন আরো একজন নমশূদ্র নেতা, পুলিনবিহারী মল্লিক (মুকুন্দবিহারীর ভাই) এবং একজন রাজবংশী নেতা, প্রেমহরি বর্মা, আর মুকুন্দবিহারী হলেন নতুন সংযুক্ত দলের সহযোগী নেতা। এই অবস্থা থেকে নমশূদ্র নেতৃত্বের মধ্যে একটা স্পষ্ট বিভাজন সহজেই চোখে পড়ে। দুই মাসের মধ্যেই আম্বেদকর কর্তৃক ১৯৪২ সালে স্থাপিত সর্বভারতীয় তফসিলি জাতি ফেডারেশনের বঙ্গীয় শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। আম্বেদকর-রাজনীতিতে ইতিমধ্যেই গভীরভাবে দীক্ষিত যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল হলেন এই শাখার প্রথম সভাপতি। ১৯৪৫-এর এপ্রিল মাসে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জে অনুষ্ঠিত এই শাখার প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলনে যোগেন্দ্রনাথ তাঁর সভাপতির ভাষনে ঘোষণা করেন যে ফেডারেশনের প্রথম এবং প্রধান উদ্দেশ্য হবে তফসিলি জাতিগুলির জন্য এক পৃথক রাজনৈতিক আত্মপরিচয় প্রতিষ্ঠা করা৩৮। তবে এই সময় সমগ্র তফসিলি সম্প্রদায়ের মনের কথা তিনি বলেছিলেন একথা ভাবাটা বোধহয় ঠিক হবে না। কারণ অনেক বিশিষ্ট নেতাই এই সম্মেলন বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। একটি বর্ণনা অনুযায়ী এই সময় সমগ্র বাংলার ৩১ জন তফসিলি এম.এল.এ-র মধ্যে মাত্র তিনজন এই সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। আম্বেদকর সম্ভবত এই অবস্থার কথা জানতে পেরেই শেষ মূহুর্তে তাঁর সম্মেলনে যোগদানের কর্মসূচি বাতিল করেন৩৯।
এই সময়ে ‘সমন্বয়বাদী’রাই নমশূদ্র তথা বঙ্গীয় তফসিলি জাতি আন্দোলনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। এর সম্যক প্রতিফলন আমরা দেখি ১৯৪৬-এর নির্বাচনী ফলাফলে। এই নির্বাচনে তফসিলি জাতি ফেডারেশনের মাত্র একজন প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন – তিনি হলেন সভাপতি যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল। মুকুন্দবিহারী মল্লিক নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন তাঁর নিজস্ব কেন্দ্র খুলনা থেকে। কিন্তু অন্যদিকে কংগ্রেস-সমর্থিত তফসিলি প্রার্থীরা জয়ী হন ৩০টি সংরক্ষিত কেন্দ্রের ২৪টিতেই। রাজবংশী নেতা প্রসন্নদেব রায়কত এবং নমশূদ্র নেতা প্রথমরঞ্জন ঠাকুর নির্দল প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে জিতলেও৪০, পরে দুজনেই কংগ্রেসে যোগদান করেন। ১৯৪৬-র নির্বাচনের ফলাফলে তাই ১৯৩৭-র অবস্থার সম্পূর্ণ আবর্তন দেখি, কারণ ওই শেষোক্ত বছরে তফসিলি জাতির বত্রিশজন নির্বাচিত সাংসদের মধ্যে মাত্র সাতজন ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী। কংগ্রেস এতদিনে নমশূদ্র তথা তফসিলি জাতি আন্দোলনের মধ্যে ‘বিচ্ছিন্নতাবাদী’দের একঘরে করে এই আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে কুক্ষিগত করে নিয়েছে। আর ভোটাধিকার সম্প্রসারিত হওয়ায় এই নির্বাচনী ফলাফলকে সাধারণ মানুষের মনের প্রতিফলন হিসেবেও খানিকটা ধরা যেতে পারে।
তফসিলি জাতি ফেডারেশনের নির্বাচনী অসাফল্য সংবিধান সভা-র (Constituent Assembly) নির্বাচনেও প্রতিফলিত হল। এই সভার জন্য বঙ্গীয় আইনসভার সভ্যদের দ্বারা নির্বাচিত তফসিলি জাতির ৬জন প্রার্থীর মধ্যে একজনই মাত্র ছিলেন ফেডারেশনের প্রার্থী, তিনি হলেন বি.আর.আম্বেদকর, নিজের প্রদেশ মহারাষ্ট্রে নির্বাচনে অনিশ্চয়তার জন্য যিনি নির্ভর করেছিলেন তাঁর বাঙালি বন্ধুদের ওপর। বাংলার আইনসভার চেহারা থেকে অন্যান্য সফল প্রার্থীরা কারা হবেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। এঁরা সবাই ছিলেন কংগ্রেস প্রার্থী, আর অন্যদিকে পরাজিতদের মধ্যে ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল এবং মুকুন্দবিহারী মল্লিক। বস্তুতপক্ষে গোটা সংবিধান সভায় তফসিলি জাতি ফেডারেশনের একমাত্র নির্বাচিত প্রার্থী ছিলেন আম্বেদকর স্বয়ং। ফলে ব্রিটিশ সরকারও এই সংগঠনকে তফসিলি জাতির যথার্থ প্রতিনিধি ব’লে স্বীকার করতে অস্বীকার করে। ভারত সচিব হাউস অব লর্ডস-এ ঘোষণা করেন যে সংবিধান প্রণয়নী সভায় কংগ্রেসই তফসিলি জাতির প্রতিনিধিত্ব করবে৪১।
বাংলায় আম্বেদকরবাদীরা আরও একঘরে হয়ে পড়েন যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল সুরাবর্দীর নেতৃত্বাধীন মুসলিম লীগ মন্ত্রীসভায় যোগদান করলে এবং ১৯৪৬-র অগস্ট মাসে সংগঠিত কলকাতা-দাঙ্গার পর তিনি ও মুকুন্দবিহারী মল্লিক মন্ত্রীসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাবের বিরোধিতা করলে। দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা এক ‘খোলা চিঠি’তে মন্ডলের কাছে আবেদন জানায় লীগ মন্ত্রীসভার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে পূনর্বার জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন করার জন্য৪২। কিন্তু এ বিষয়ে তিনি মোটেই আগ্রহী ছিলেন না, বরং লীগের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব কাজে এল যখন ১৯৪৬-এর অক্টোবর মাসে জিন্না তাঁকে অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভায় বাংলা থেকে লীগের প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করলেন। তবে যে রাজনীতির স্বপক্ষে তিনি দাঁড়িয়েছিলেন সে রাজনীতিটাই ক্রমে অর্থহীন হয়ে পড়ে। কারণ ১৯৪৭-এর জুলাই মাসে একটি উপনির্বাচনে বম্বে কংগ্রেস সংসদীয় দল আম্বেদকরকে তাঁদের প্রার্থী হিসেবে মনোনীত করে। পরে তিনি সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তারও পরে স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম সরকারে আইনমন্ত্রী হিসেবে যোগদান করেন (জেলিয়ট ১৯৮৮, পৃঃ ১৯৩-১৯৪)। কংগ্রেস এইভাবেই তফসিলি জাতির আন্দোলনকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করে নেয়, যদিও এই প্রক্রিয়া নিম্নবর্গের চেয়ে ওপরের তলার মানুষদের মধ্যেই বেশি কার্যকর হয়েছিল বলে মনে হয়।
৬
১৯৩৮ সাল থেকে নমশূদ্র নেতারা মোটামুটিভাবে, যাকে বলা যায়, সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের রাজনীতিতেই নিমগ্ন হয়েছিলেন। ঠিক যেমন ক্রমবর্ধমান গতিতে তাঁরা কংগ্রেসের ছত্রছায়ায় আসতে শুরু করেন, ঠিক তেমনি ভাবেই গণআন্দোলনের ব্যাপারেও তাঁদের উৎসাহে ভাঁটা পড়তে থাকে। বেশির ভাগ নেতা এবং তাঁদের সংগঠনগুলি এই সময়ে হয়ে পড়েছিল কলকাতাকেন্দ্রিক। ক্কচিৎ-কখনও তাঁরা গ্রামে যেতেন ‘কৃষকদের অবস্থা সম্বন্ধে খোঁজ খবর নিতে৪৩’। এবং আরো কদাচিৎ তাঁরা কৃষকদের দাবি-দাওয়া নিয়ে কথা বলতেন – তাঁদের বিভিন্ন সভার অনুষ্ঠানসূচী থেকে অন্তত তাই মনে হয়৪৪। এই অবস্থা থেকে যেটা সহজেই বোঝা যায় তা হল নমশূদ্র নেতৃত্ব ও তাঁদের কৃষিজীবি সমর্থকদের মধ্যে এক দুস্তর মানসিক এবং পার্থিব ব্যবধান ক্রমশ তৈরি হয়ে চলেছিল।
১৯৩৭ সালের পর থেকে নমশূদ্র কৃষকেরা কি করছিলেন দলিল দস্তাবেজে তার সরাসরি হদিশ পাওয়া যায়না ব’লে আমাদের কিছুটা তা অনুমান করে নিতে হয়। একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে হিন্দু সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মানসিকতা তাঁরা হারিয়ে ফেলেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, ১৯৩৭-৩৮ সালে শ্রীহট্ট জেলার হরিগঞ্জ মহকুমার শিমুলঘর গ্রামে তাঁরা বর্ণহিন্দুদের উপস্থিতিতে জুতো পরে থাকার অধিকার আদায়ের জন্য এক দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন শুরু করেছিলেন, মাঝে মাঝেই যা হিংসার পথ ধরছিল৪৫। কিন্তু অন্যদিকে এমন প্রমাণও আছে যে তাঁরা ওই সময় হিন্দু সমাজের সঙ্গে অনেক বেশি করে একাত্মবোধ করছিলেন এবং এই হিন্দুয়ানি কখনও কখনও তাঁদের জাত-ভিত্তিক আত্মচেতনাকে ছাপিয়ে উঠছিল।
নমশূদ্র জনসাধারণের মধ্যে হিন্দুত্ববোধ জাগিয়ে তোলার পেছনে বিভিন্ন হিন্দু সংগঠনগুলির প্রচেষ্টাও ছিল। যেমন হিন্দু মিশন তিনের দশক থেকে এই ধরণের মানুষের মধ্যে কাজ শুরু করে এবং ১৯৩৮-এর পর তাদের কার্যগতি আরও বেড়ে যায়৪৬। এই সময় থেকে ভারত-সেবাশ্রম সঙ্ঘের স্বামী প্রণবানন্দ যশোর, খুলনা, ফরিদপুর এবং বাখরগঞ্জ জেলার নমশূদ্রদের মধ্যে কাজ শুরু করেন, যাতে তাদের সংগঠিত করে হিন্দু সমাজের শক্তি বৃদ্ধি করা যায়৪৭। কিন্তু এদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল সর্বভারতীয় হিন্দু মহাসভা। এই সংগঠন ১৯৩৯-৪০ সাল থেকেই তফসিলি জাতিভুক্ত কৃষকদের সংগঠিত করার কাজে বিশেষ উৎসাহী হয়ে ওঠে। ১৯৪৪ সালের মধ্যেই পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জেলায় এদের ৬৫টি, ঢাকায় ৫০টি, ফরিদপুরে ৪৩টি, যশোরে ২৯টি এবং খুলনায় ৩১টি গ্রামীণ শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। মুখ্য নমশূদ্র বস্তির যে সব অঞ্চলে এই শাখাগুলি খোলা হয়েছিল তার অনেকগুলি ইতিমধ্যেই নমশূদ্র আন্দোলনের জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেছে৪৮। এমন প্রমাণও আছে যে এই অঞ্চলগুলির কিছু তফসিলি নেতা তফসিলি জাতিভুক্ত জনগণকে সংগঠিত করার কাজে অর্থ সাহায্য পাচ্ছিলেন মহাসভার কাছ থেকে৪৯। ঢাকা নমশূদ্র সমিতির মতো সংগঠনও এই সময় মহাসভার সভাধিপতি শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল৫০।
নমশূদ্রদের মধ্যে হিন্দুত্ববোধ জাগিয়ে তোলার এই যে সুসংবদ্ধ প্রয়াস তার প্রতিফলন আমরা দেখি পরবর্তীকালে এঁদের সঙ্গে স্থানীয় মুসলিমদের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিভিন্ন ঘটনায়। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে দাঙ্গা আগেও হয়েছে; কিন্তু তা ছিল অধর্মীয় চরিত্রের। জমি নিয়ে বিবাদ অথবা মহিলা সংক্রান্ত এবং সম্প্রদায়ের মান রাখার জন্য সংঘাত ঘটেছে, যেখানে ধর্মের ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে কদাচিৎ। এবং সংঘাতের পাশাপাশি সহযোগিতার নিদর্শনও রয়েছে প্রচুর (বন্দোপাধ্যায়, ১৯৯০ খ)। কিন্তু ১৯৪০-র দশক থেকেই অবস্থাটা পাল্টাতে থাকে। হিন্দু মহাসভার প্রভাবে নমশূদ্ররা এবার মুসলমানদের মুখোমুখি হতে শুরু করে আগের মতো শুধুমাত্র নমশূদ্র হিসেবে নয়, হিন্দু হিসেবেও।
এই নতুন মনোভাব পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হতে থাকে ১৯৪১-এর ১৮-২১ মার্চের ঢাকা-দাঙ্গার পর থেকে, কারণ রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার এই নতুন জঙ্গী মনোভাব নমশূদ্রদেরও সমানভাবে প্রভাবিত করে। ঢাকা দাঙ্গার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ১৯৪১-এর ২০ মার্চ খুলনা জেলায় আরেকটি দাঙ্গা ঘটে, যাতে ‘একটি হিন্দু নমশূদ্র গ্রাম এবং একটি মুসলমান গ্রাম সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়।৫১’ এই দাঙ্গাটি সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না; কিন্তু ঠিক এই সময়ে যে কান্ডটি ঘটেছিল তা মনে করায় যে, নিছক জমি বা গরু-ছাগল নিয়ে বিবাদ এর কারণ ছিল না। এই সময় থেকেই হিন্দু মহাসভার স্বেচ্ছাসেবীরা এই অঞ্চলে তাদের সংগঠনের কাজ শুরু করেছিলেন, আর তার ফলস্বরূপই আমরা দেখি স্থানীয় নমশূদ্র এবং মুসলমান জনগণ বাগেরহাটে একে অন্যের সম্মুখীন হচ্ছেন সরাসরি রাজনৈতিক সাম্প্রদায়িকতার স্লোগান মুখে নিয়ে – একদিকের স্লোগান ছিল, ‘হিন্দু শক্তি কি জয়’ এবং ‘শ্যামাপ্রসাদ জিন্দাবাদ,’ আর অন্যদিকের, ‘মুসলিম শক্তি কি জয়’ এবং ‘শ্যামাপ্রসাদ ধ্বংস হোক।’ খুলনা জেলার স্থানীয় শাসনকর্তারা সম্ভবত সংগত কারণেই মনে করতেন যে এই বিরূপতা ছিল হিন্দু মহাসভার সংগঠকদেরই তৈরি৫২।
১৯৪৬-৪৭ সাল নাগাদ পূর্ববঙ্গের নমশূদ্র কৃষক তাদের হিন্দু আত্মপরিচয় সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবেই অনেক বেশি সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং হিন্দু মহাসভা এই সময়ে বাঙালি হিন্দুদের জন্য এক পৃথক রাজ্যের যে দাবি তুলেছিল তার স্বপক্ষেও তাঁরা যথেষ্ট সরব ছিলেন। বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর এবং খুলনা জেলার হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চলগুলি যাতে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং সে রাজ্য যাতে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়, তার দাবিতে উক্ত জেলাগুলির বিভিন্ন গ্রামে সংগঠিত হয়েছিল বহু জনসভা, যাতে বিপুল সংখ্যায় নমশূদ্র কৃষকরা যোগ দেন৫৩। তাঁদের এই মনোভাব তাঁদের নেতাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। ব্যতিক্রম ছিলেন যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল, যিনি একমাত্র সমর্থন জানিয়েছিলেন শরৎ বসু ও বঙ্গীয় মুসলিম লীগের আবুল হাসেম-সুরাবর্দী গোষ্ঠী কর্তৃক আনীত ‘সার্বভৌম সংযুক্ত বাংলা’-র প্রস্তাবকে। বঙ্গীয় আইনসভায় বাংলাভাগের প্রস্তাবটি ভোটাভুটির জন্য এলে চারজন বাদে আর সব তফসিলি জাতির সাংসদই ভোট দেন কংগ্রেস-মহাসভার পরিকল্পনার স্বপক্ষে, যাতে ছিল পশ্চিমবঙ্গকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল হিসেবে গঠন করে ভারতের অন্তর্ভুক্ত ক’রার কথা (গর্ডন ১৯৮৯, পৃঃ ৫৮১-৮২, ৫৮৬)। কিন্তু দেশবিভাগ শেষ পর্যন্ত নমশূদ্রদের সাহায্য করেনি, কারণ এর ফলে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব স্থায়ী বসতভূমি হারালেন। তাঁদের আশা এবং সব আবেদন সত্তেও যে ভৌগোলিক অঞ্চলটিকে আগে আমরা এদের প্রধান বসতি অঞ্চল বলে চিহ্নিত করেছিলাম, তার সমস্তটাই চলে যায় পূর্ব পাকিস্তানে, পশ্চিমবঙ্গে নয়। পূর্ববাংলার শেষ ব্রিটিশ গভর্নর F.C. Bourne-এর ১৯৫০ সালে লিখিত একটি প্রতিবেদন থেকে আমরা জানতে পারি যে দেশবিভাগের অব্যবহিত পরেই যে হিংস্র উন্মত্ততা দেখা দিয়েছিল তার ফলে এদের অনেকেই শুধুমাত্র তাঁদের জীবন এবং পরিহিত বস্ত্র ছাড়া আর সবকিছুই হারিয়েছিলেন৫৪।
তবে পূর্ববঙ্গের নমশূদ্র কৃষকদের একীভবনের আরও একটি স্তর ছিল। যাঁরা হিন্দুকরণের রাজনীতিতে সাড়া দিচ্ছিলেন, তাঁরাই কিন্তু আবার শ্রেণীভিত্তিক আন্দোলনেও যোগ দিচ্ছিলেন। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি কিভাবে কৃষক প্রজা পার্টি ১৯৩০-র দশকে তাঁদের সংগঠিত করে এবং পরে ১৯৩৭-এ কেনই বা তাঁদের আবার পরিত্যাগ করে। অন্যদিকে কিন্তু এই সময়েই ১৯৩৭-এর মার্চ মাসে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিষাণ সভা বাংলায় নিম্নবর্ণের কৃষকের এই প্রতিবাদী মনোভাবকে সংগঠিত করার চেষ্টা শুরু করে দেয়। ১৯৩৮-৩৯ সালে সারা প্রদেশে তাঁদের মাত্র ৫০,০০০ সভ্য থাকলেও (সেন ১৯৮২, পৃঃ ৭৫-৭৮), ১৯৩৭ সালের মাঝামাঝি থেকেই খুলনা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় ‘কম্যুনিস্ট ধাঁচে কৃষক সমিতি’ গড়ে উঠতে শুরু করে; আর এই জেলাগুলিতে হিন্দু কৃষকের অধিকাংশই ছিলেন নমশূদ্র৫৫। কৃষকদের দলবদ্ধ করার এই কম্যুনিস্ট প্রয়াস৫৬ আরও বেড়ে যায় ১৯৪২ সালের ২৮-২৯ জুন রংপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সম্মেলন হওয়ার এবং জুলাই মাসে কম্যুনিস্ট পার্টির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা উঠে যাওয়ার পর থেকে৫৭।
এই সংগঠনের ফল আমরা লক্ষ্য করি ১৯৪৭-এর তেভাগা আন্দোলনে, কারণ পূর্ববাংলায় এই আন্দোলনে যোগদানকারীদের অধিকাংশই ছিলেন ফরিদপুর, খুলনা এবং যশোর জেলার নমশূদ্র ভাগচাষি। এই অঞ্চলে কখনও কখনও অবশ্য বাইরের ষড়যন্ত্রের ফলে আন্দোলনকারীদের দৃষ্টি ঘুরে যায় মুসলমান প্রতিবেশীদের সঙ্গে তাঁদের পুরনো বৈরিতার দিকে, এর ফলে আন্দোলন ক্ষতিগ্রস্তও হয় যথেষ্ট পরিমাণে (কুপার, ১৯৮৮, পৃঃ ২২৫-২৬, ২৫৩, ২৫৬-৫৭, ২৬০)। তবে এই অবস্থা থেকে এটাও বোঝা যায় যে ‘শ্রেণী,’ ‘ধর্ম’ এবং ‘জাতের’ প্রতি তাঁদের আনুগত্য একাধার-অস্তিত্বকে বজায় রেখেছিল। এই আত্মপরিচয়ের সমূহ ভিন্নতা কারো স্থানচ্যুতি ঘটায়নি বা সমান্বিতও হতে পারেনি। অন্যদিকে, নমশূদ্র জাতি আন্দোলনের সনাতন নেতারা ভাগচাষিদের এই সংগ্রাম নিয়ে কখনই মাথা ঘামাননি, এবং বরাবরি দূরে সরে থেকেছেন, যদিও উত্তরবঙ্গের রাজবংশী নেতাদের মতো সরাসরি বিরোধিতা করেননি কখনও। এর থেকে এটাই স্পষ্ট হয় যে নমশূদ্র আন্দোলনে একটি বিভাজনের প্রক্রিয়া ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে যে সম্প্রদায়কেন্দ্রিক আত্মপরিচয় সযত্নে গড়ে তোলা হয়েছিল তা এবার ভাঙতে শুরু করেছে। নতুন আত্মপরিচয় গড়ার কাজ শুরু হয়েছে। অথবা তার নতুন সংজ্ঞা নিরূপিত হতে চলেছে।
৭
১৮৭২ থেকে ১৯৪৭ সালের বাংলায় নমশূদ্র আন্দোলনের এই ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে এই ধরণের আন্দোলন কখনই আগাগোড়া সমপ্রকৃতির থাকে না। এগুলির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে আমরা বিভিন্ন স্তরের চেতনা, বিবিধ উদ্দেশ্য এবং নানান ধরণের কাজকর্ম লক্ষ্য করি, তবে এর সবকিছুই একই আচ্ছাদনে ঢাকা থাকে, তাই সাধারণ মানুষেরা যখন সম্প্রদায়ের সম্মানহানির কল্পিত ভয়, সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ এবং অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ নিয়ে ভাবিত হয়, তখন তাদেরই মধ্যে অপেক্ষাকৃত বর্ধিষ্ণু গোষ্ঠী ধর্মীয় আচারগত মর্যাদার প্রতীক অথবা প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির সুবিধা-সুযোগ নিয়ে ভাবে। দুই দলই তাদের নিজস্ব উপায়ে সমাজে ক্ষমতার সম্পর্কে পরিবর্তন আনতে চায়। তাই এদের মধ্যে অন্যোন্যজীবীত্বের সম্পর্ক থাকে, কারণ এই দুই দলই, সবসময় সচেতনভাবে না হলেও, জাতিভেদ প্রথার কর্তৃত্বকে ভাঙতে চায়। তবে এই অন্যোন্যজীবীত্বের অর্থ কখনোই সমস্ত রকম সংঘাত অথবা পৃথকীকরণের সম্ভাবনার চিরতরে বিনষ্টি নয়।
কিছুদিনের মধ্যেই একটা সময় আসে যখন নতুন করে স্থান পরিবর্তন শুরু হয়ে যায়। এটা বিশেষ করে লক্ষ্য করা যায় যখন তিনের দশক থেকে সরকার ভারতে ঔপনিবেশিক শাসনের যথার্থ প্রমাণের জন্য নিম্নবর্গের আন্দোলনগুলি সমর্থন করতে শুরু করে। এই সময় এই আন্দোলনগুলির অনেক নেতাই দেশের সব থেকে ক্ষমতাশালী দল কংগ্রেসের সঙ্গে একাত্ম হওয়াই অনেক বেশি সুবিধাজনক বলে মনে করতে শুরু করেছিলেন। এই ধরণের একটা পরিণতি খানিকটা অবশ্যম্ভাবীও ছিল, কারণ শেষ পর্যন্ত এইসব নেতাদের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয় রাজনীতিতে নিজেদের ক্ষমতার আসনে বসানো, বৃহত্তর সমাজ থেকে নিজেদের পৃথক করে রাখা নয়। আর চারের দশকেই ভারতে রাজনৈতিক জাতির প্রতিনিধি হিসেবে কংগ্রেস সবরকম বাস্তবিক অর্থেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কংগ্রেসও ১৯৩৫-এর সাংবিধানিক সংস্কারে বিধিবদ্ধ প্রাতিষ্ঠানিক রাজনীতির ক্ষেত্রে এইসব নেতাদের গুরুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল, ফলে একীকরণ হয়েছিল সহজতর। অন্যদিকে নিম্নবর্গের জনসাধারণও সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের জন্য তাঁদের অসমাপ্ত সংগ্রাম চালিয়ে নিয়ে যায়। কখনও তার মাধ্যম ছিল জাত-ভিত্তিক সম্প্রদায়, যদিও একেই ক্ষমতার একমাত্র আধার বলে মেনে নিতে আর রাজি ছিলেন না তাঁরা। তাই কখনও তাঁরা জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন, কখনও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন, আবার কখনও বা সরাসরি শ্রেণীভিত্তিক কর্মসূচি ও সংগঠনের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। অন্যভাবে বলতে গেলে, যে আন্দোলন এক সময় শুরু হয়েছিল ‘নিম্ন বর্ণের আন্দোলন’ হিসেবে, তা একদিন বিভিন্ন পথে চলতে শুরু করে, কারণ জাত-ভিত্তিক আত্মপরিচয়কে বিভক্ত করে অথবা আচ্ছন্ন করে এমন অনেক নতুন আত্মপরিচয় গড়ে উঠতে অথবা সরব হয়ে উঠতে শুরু করেছে। এই আন্দোলনগুলির মধ্যে তাই সমপ্রকৃতি অথবা একমূখীন প্রগতির খোঁজ না করে এই ধরনের জটিলতারই অনুসন্ধান করা উচিত। সেই অনুসন্ধানই উত্তর দিতে পারবে কেন অত্যন্ত সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া এইসব নিম্নবর্ণের প্রতিবাদ ভারতীয় সমাজে প্রচলিত ক্ষমতার সম্পর্ককে ভেঙে ফেলতে সমর্থ হয়নি।
লিখেছেন – শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়
(ডঃ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অফ ওয়েলিংটন-এর ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনারত। বাংলার নমশূদ্র আন্দোলন ও উত্তর-ঔপনিবেশিক বঙ্গদেশে জাতি, বর্ণ, বিভাজনের ইতিহাস ও রাজনীতি নিয়ে তিনি বহু গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন। এই প্রবন্ধটি শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিৎ দাশগুপ্ত ও ভেলাম ভান সেন্দেল (সম্পাদিত) Bengal: Development, Communities and States (১৯৯৪) গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। লেখকের অনুমতিক্রমে বাঙালনামায় পুনঃপ্রকাশিত হ’ল।)









Related
This entry was posted on August 31, 2009 at 7:30 pm and is filed under ইতিহাস, জাত, তেভাগা আন্দোলন, নমশূদ্র আন্দোলন, পরিচয়, রাজনীতি. Tagged: Ashwini Kumar Dutta, খুলনা, ঢাকা, পূর্ববঙ্গের নমশূদ্র আন্দোলন, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, B R Ambedkar, Bakhargunj, Baruni Mela, Bengal Namasudra Association, Calcutta Scheduled Caste League, Chandal, Fazlul Haq, Guruchand Thakur, Independent Scheduled Caste Party, Jessore, Jogendranath Mandal, Matua, Matua religious sect, Mukunda Bihari Mullick, Namasudra, Namasudra Andolon, Pratham Ranjan Thakur, Prem Hari Barma, Pulin Bihari Mullick, Saral Dutta, Sekhar Bandyopadhyay, Shahlal Pir, Tebhaga Andolon, Upendra Nath Burman. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.


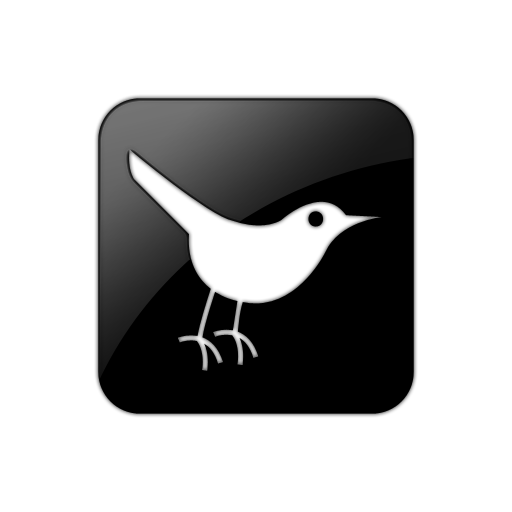
DCMALLICK said
SHEKHAR BABU. I BELONG TO NAMASUDRA COMMUNITY. STILLOUR COMMUNITY MEMBER ARE SUPPRESSED. AND IT IS DUE TO LACK OF EDUCATION. I HAVE COME TO KNOW THAT HINDUS WERE NOT IN FAVOUR OF OUR EDUCATION.HARICHAND, GURUCHAND, MAHATMA PHULE,SAVITRIBAI PHULE, BABASAHEB DR. BR AMBEDKAR, BEGAM ROKEA DID LOT FOR OUR EDUCATION.VIDYASAGAR, GANDHI, PROMOD DASGUPTA,JYOTIBASU WERE NOT AND NEVER WERE FOR OUR EDUCATION.NOW WE HAVE TO SOLVE OUR PROBLEM. CONGRESS CPM BJP TRINAMOOL CAN NOT IMPROVE OURSOCIAL, ECONOMICAL AND POLITICAL DEVELOPMENT.
DCMALLICK said
FURTHER: 2012 11MARCH 200YEAR JAYANTI OF LORD HARICHAND GOING TO BE INAUGURATED. UR WRITING HAS OPENED MY VISON TO SEE THINK AND ACT TO UNITE THE NAMASUDRA, SC/ST OBC AND CONVERTED MINORITIES TGETHER TO ESTABLISH REAL DEMOCRACY TO ESTABLISH PEACE AND HARMONY IN THE WORLD.DCMALLICK 9820053852
dcmallick said
MR MUKHOPADHAYA IS REQUESTED TO SEE IF RAMESH CHANDRA MAZUMDAR WAS AWARE OF THIS MOVEMENT OF HARIGURUCHAND
BEING AFRAID OF NAMASUDRA CONGRESS EXCLUDED FARIDPUR, BARISAL KHULNA JESSORE FROM INDIA. NAMASUDRA ARE BEING UNITED AND THEY MAY BE THE KING OF INDIA.MANUBADI PARTIES ARE VERY AFRAID OF NAMASUDRA WHO ARE SCATERED ALL OVER INDIA.CITIZENSHIP BILL HAVE BEEN PASSED IN 2003 AND TAHAT IS DETRIMENTAL TO INDIA.MATUA DHARMA IS UNIVERSAL AND NEARBY TO BUDDHISM.MATUA DHARMA PROTECTED CONVERTION TO MUSLIM AND CHRISTIAN DUE TO CASTISM IN MANUBAD.REMOVE CASTISM FROM HINDUSIM IT IS MANAB DHARM.SHEKHAR BABU IS REQUESTED TO PLEASE INCORPORATE THE 12 COMMANDMENTS IN HIS NEXT EDITION. HE MAY GO THROUGH THE THESIS BY DR. NANDADULAL MOHANTA AND DR. BIRAT BAIRAGYA. SHEKHAR BABU’S WRITE UP IS SO FAR THE BEST ONE . PRESENT KABIS CD/DVD WILL BE HELPFUL
dcmallick said
RECENTLY 10TH NOVEMBER TO13TH NOVEMBER BISWA MATUA MAHASAMMELAN STARTED TO CELEBRATE THE 200TH BIRTH CENTINARY OF SHRI SHRI HARIGURUCHAND IN VRINDAVAN. ASHWINI GOSAI CAME TO VRINDABAN WALKING 90 DAYS FROM ORAKANDI. HE WAS SINGING BRAJANATH GOT DAIBABNI THAT GOLOKBIHARI WAS IN ORAKANDI ITSELF.HE RETURNED BACK TO ORAKANDI.IT IS FELT THAT GOLOK BIHARI CAME BACK TO BRINDABAN AT 45 SURAJGHAT NEAR BANKEBIHARI/MADAN MOHAN TEMPLE.THOUNDS OF DEVOTEES CAME FROM DIFFERENT PARTS OF INDIA WHERE NAMASUDRA ARE SCATTERED.POTERU ASHRAM ORESSA,, RUDRAPUR ASHRAM NAINATAL,ITARSHI, BHOPAL, RAJASTHAN HARIYANA, THAKURNAGAR, BANGLADESH. VRINDABAN PARIKRAMA5KROSH=10MILES=A6.25 KMS IN NAKED FEET WITH 200 DANKAS, KANSAR, SINGA, RED FLAG CHANTING HARIBOL, HARIBOL, HARIBOL…… . MATUA MOVEMENT COVERING SPIRITUAL, PHYSICAL,ECONOMICAL, SWABHIMAN, POLITICAL, EDUCATION,YOGA, SATYA, PREM, PABITRATA. WORK PHYSICALLY HARIBOL BY VOICEHARICHAND GURUCHAND EARN MONEY BE HAPPY WITHFAMILY MAN, WITH OWN WIFE, OTHER WOMAN WILL BE TREATED AS MOTHER, ALWYAS SPEAK TH TREATH.I CAN BE WITH SEKHAR BABU TO VISIT ALL THE POINTS OF MATUAS IN INDIA.MOBILE +91 9820053852
iyun,may,mart said
iyun,may,mart…
[…]palashbiswaslive: A disciple of Guruchand, Mukunda Behari Mullick, fought for ‘Separate Electorate’ since 1921.[…]…
dcmallick said
AFTER VRIDAVAN A DEVOTEE DR. SANJIT BISWAS AND MOTHER CHANCHALA, DIDI MEGHA OF KURUKSHETRA ARRANGED A MATUA GATHERING AT BRAHMA SAROVAR, KURUKSHETRA ON 21ST JUNE 2012, SULEKHA TAPAS TIKADAR, GOKULANDA MANJURI OF VRIDAVAN ALONG WITH DRIVER SUNIL ATTENDED THE FIRST MATUA MEET AT KURUKSHETRA. A 5 KM PARIKRAMA WITH AROUND THE SAROVAR WITH 200 DEVOTEES, WAS THERE ON 21ST JUNE 2012 MORNING , WITH 10 JAIDANKA, 30 MATUA FLAGS AND AT ABOUT 10:00 WE TOOK BATH IN THE SAROVAR, THE GATHERING WAS ENDED WITH MY SPEECH WHICH IS INTHE LINE OF BUDDHA, BABASAHEB
dcmallick said
“HARIBOL” CHAITING IS DAY BY DAY INCREASING IN VRINDAVAIRN WHICH I’M OBSERVING AT OUR HARI TEMPLE AT 45, SURAJGHAT, MADAN MOHAN GHERA, PIN 28II21, DIST MATHURA, UP. CONTACT 8791306194, 9410040644, 9820053854 FOR FREE GUIDANCE FORVISITING VRINDAVAN, KURUKSHETRA, HARIDWAR,ETC AT OUR ABOVE ADRESS. FR OM MATHURA COME TO OUR MANDIR BY AUTO WHICH VARY FROM RS 150 TO 250 AT NORMAL TIME.