বাঙালবৃত্তান্ত – পর্ব তিন
Posted by bangalnama on September 13, 2010
– লিখেছেন রঞ্জন রায়
সতীনের নাম আরশোলা
সুষমা মারা গেছেন। খবরটা পেয়ে উদাস হয়ে সিগ্রেট ধরাতেই গিন্নি বল্লেন- কি, হয়েছেটা কি?
আমি বল্লাম যে নিজের সময়ের আগে জন্মানো একজন এই দুনিয়া থেকে পাততাড়ি গোটালেন। তারপর এই সুষমাটি কে? আমার সঙ্গে কিসের সম্পর্ক? – এইসব বাঁধাগতের হাবিজাবি কথা উঠতেই আমি ঠাকুমার একটি ছড়া ঝাড়লাম, — উনি আমার কি লাগেন? ঠাকুরবাড়ির গাই লাগেন।
তারপর বল্লাম যে উনি আমার কলকাতার পাতিপুকুর অঞ্চলের সেজপিসেমশায়ের সৎবোন, আবার ছত্তিশগড়ের রায়পুর শহরের দূর্গা কলেজের রেজিস্ট্রার কারকুনদা’র সৎমা। গিন্নি বিরক্ত হয়ে বল্লেন- পারো বটে খুঁজে খুঁজে আত্মীয় পাতাতে।
– বাজে বোকো না। বালকবয়সে আমি পাতিপুকুর বাড়ি গিয়ে ওনার জন্মসূত্রে অস্বাভাবিক মেয়ে নিশার ভাইফোঁটা নিয়েছি। এখন চিনিনা বললে চলবে? ধম্মে সইবে? তার চেয়ে লিপটনের চা বানাও আর সুষমার গপ্পো শোনো।
– আরে! বাল্যকালের স্মৃতি? ছোড়ো কাল কী বাতেঁ। জীবনে দ্বিতীয়বার দেখেছ ওই ঠাকরুণকে? ঐ কারকুনদাদার ছোটছেলে মুন্নার বিয়েতে। দাদা সৎমা সুষমাকে যথাবিহিত সম্মানের সঙ্গে কলকাতা থেকে “নাইয়র” এনেছিলেন।
– নাইয়র? সেটা কি জিনিস? খায় না মাথায় লাগায়?
– কি মুশকিল! সায়গলের বিখ্যাত ভৈরবী মনে নেই? সেই যে গো “বাবুল মোরা, নৈহর ছুট যায়”। নৌকো? আসলে আমাদের বাঙালদেশে বছরের অদিকাংশ সময় নৌকোপথেই যাতায়াত হত কি না। তাই নৌকো করে আসা সম্মানিত অতিথি হলেন “নাইয়র”। শচীনকর্তার গান গো- “কে যাস্ রে, ভাটিগাঙ বাইয়া? আমার ভাইধনরে কইয়ো “নাইয়র” যাইতো বইল্যা, তোরা কে যাস্?”
তা’ বিয়ে বাড়িতে পাকাচুল, ছিপছিপে, ফর্সা, চোখা নাকমুখ, চশমাচোখে মহিলাকে দেখে যেই বলেছি- ইনি কে? চাপাগলায় উত্তর এলো- উনি সুষমা, সুষমা কারকুন। মানে আমার সৎমা। তোমার পিসি হন।
মনে পড়েছে, গিয়ে ঢিপিস্ করে পেন্নাম করলাম।
কড়া চোখে একনজর দেখে বল্লেন– আরে, তুই কলকাতার পার্কসার্কাসের রায়েদের বাড়ির না? সেই যে ধাঙড়বাজারে মুসলমান হোটেলের সামনে দোতলার ভাড়া। গেছি তোদের বাড়িতে, তুই তখন সাত-আট বছরের।
আমি হতবাক। — আপনার মনে আছে? তিরিশ বছর পরে দেখেও চিনতে পারলেন?
– কেন? কিসের অসুবিধা? সারা কইলকাতায় এমুন কাইল্যা রং আর কার বাড়িতে আছে! হেই গায়ের রং দেইখ্যাই চিনলাম।
বিয়েবাড়ির হাসির হররার মাঝে আমি দন্ত কেলাসিত করলাম। ওনার সাথে সেই আমার শেষ দেখা।
– দন্ত কেলাসিত তো তোমার সিগ্নেচার স্টাইল। এখন বাজে কথা ছেড়ে সুষমার গপ্পো শোনাও, আমি লিপটন ঢালছি।
নৌকো চলেছে মেঘনা নদী বেয়ে। শরতের আকাশ, পঁেজা তুলোর মত মেঘ ভেসে যায়। পালে হাওয়া লেগেছে। ছই থেকে বেরিয়ে এসে নীলাম্বরবাবু একটু উসখুস করছেন। সিগারেট গেছে ফুরিয়ে। কিন্তু কলকাতার মেসবাড়ির অভ্যেস – একটু ধুঁয়ো না খেলে চলে না যে। ভাবছেন মাঝির সঙ্গে ভাব জমিয়ে হুঁকো চাইলে কেমন হয়? চোখে পড়লো আরেকজন, গলুইয়ের কাছে দাঁড়িয়ে ইতিউতি তাকাচ্ছেন। মনে হচ্ছে একই পথের পথিক। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন–
– মশায়ের পরিচয়?
জবাব এল — “নন্দীপুরের নন্দী আমি- ঈশান চন্দ্র নন্দী। আপনার?”
– “ধাড়ীশ্বরের ধাড়ী আমি নীলাম্বর ধাড়ী।”
– “এইডা কেমুন নাম হইল, মশয়?”
– “যেমুন আপনার। আপনার গ্রাম নন্দীপুর, আমার গ্রাম ধাড়ীশ্বর।”
– “হ’, বুঝেছি। যেমুন আমার মামার নাম মহাভারত রায়।”
– “আর আমার মামার নাম রাজকৃষ্ণ রায়ের গ্রন্থাবলী। কেমুন বুঝছেন?”
– “বুঝলাম যে আমি আধা বুঝছি আর আপনে পুরা বুঝছেন।”
যাহোক, দু’জনের বাগযুদ্ধের শেষমেশ মধুরেণ সমাপয়েৎ হল একজন আরেকজনের মুখে আগুন দিয়ে। ধোঁয়া টানতে টানতে নীলাম্বর ঈশানচন্দ্রকে বললেন, “একটা কথা জিগাই, শুনছি আপনার নন্দীপুরের একজন নাকি মাইয়ার বিয়া নিজের বন্ধুর লগে দিছে! হাছা না মিছা?”
– “হাছা কথা! আর কইয়েন না। এরা নামে ভদ্রলোক, কায়স্থ, পদবী নন্দী, ব্যবহারে ছুডুলোকের অধম। পয়সার লোভে সোনার পুত্তলি মাইয়াডারে বাপের বয়সি বুইড়া বরের লগে বিয়া দিল।”
– “বর কেডা?”
-”মৈমনসিংহের জংগলবাড়ির হরেন্দ্র কারকুন। সুদের কারবারি, মেলা পয়সা।” দু’জনে খানিকক্ষণ মৌনীবাবা হয়ে ধোঁয়া গিললেন। তারপর নীলাম্বরের কৌতূহল আর বাঁধ মানল না।
– “মেয়ের মা রাজি হইল?”
– “তার রাজি আর অরাজি! নন্দী বুইড়া ঘইন্যা ত্যান্দড়, মেয়ের মায়েরে জানায় নাই। সিধাসাধা মানুষটা, খবর শুইন্যা কাইন্দা আকুল। নন্দীবুড়া ধমকায়,- চোখ মুছ, মেয়ে-জামাই আইলে ভাল কইরা বরণ কর। চোখের জলে মেয়ের অমঙ্গল হইব।”
– “অমঙ্গলের আর বাকিডা কি, তারপর?”
– “মাইয়া বড় তেজী। বুইড়া বরে দিছিল তারে সোনা দিয়া মুইড়া, সে পাল্কির মইধ্যে বইয়া সারা গয়না খুইল্যা পোঁটলা বান্ধলো। ঘরের দরজায় পাল্কি নামতেই মা আইলেন বরণডালা নিয়া। মেয়ে কয়, -’মা আঁচল পাত।’ তারপর পোঁটলা খুইল্যা দিল হগ্গল গয়না ঝপাৎ কইরা মায়ের কোলে ফালাইয়া।
কইলো– নে, এর লোভেই তো আমারে বাপের বয়সী বুড়ার সঙ্গে বিয়া দিলি। আরও নে।”
– “এমুন জবাব দিল? মাইয়া তো বড় তেজী! শেষে বুড়ার ঘর করল? সতীন কয়জন? মানে বুড়ার আগের পক্ষের?”
– “একজনই আছে; কিন্তু সে ঠিক মানুষ নয়।”
– “সতীন আছে, মানুষ নয়! তবে কি ভূত-প্রেত?” নীলাম্বরের চোখ বড় বড় হয়ে ওঠে। নন্দীপুরের নন্দী এবার গঁোফের ফাঁকে মুচকি হাসেন।
– “না-না, বছর পনেরোর মাইয়া সুষমা নন্দীর সতীন হইল তেলচুরা, – যারে কইলকাতার ভাষায় কয় ‘আরশোলা’।”
নীলাম্বরের মুখের হাঁ বন্ধ হয় না। নন্দীমশায়ের করুণা হল। বুঝিয়ে বললেন যে সুষমা হলেন তাঁর স্বামীর পঞ্চমপক্ষ। প্রথম তিনজন গত হওয়ায় সুষমার জন্যে বিয়ের পঁিড়িতে বসার আগে সুতো বঁেধে একটি আরশোলাকে সাতপাক ঘুরিয়ে বুড়ো বর যমরাজকে ফাঁকি দিলেন। ফলে সুষমা চতুর্থ না হয়ে পঞ্চম হলেন, নইলে নাকি বছরঘোরার আগেই বিধবা হতেন। তবে এই তুক্্তাক ফলে গেলো। নন্দীবুড়োকে যমরাজা বছর তিনের মাথায় ডেকে নিলেন। ততদিনে সুষমার কোলে এসেছে জড় মেয়ে নিশা আর ছেলে অজয়।
নিন্দুকে বলে তুক্্তাক নয়। যমরাজা সুষমার প্রতি করুণায় নন্দীবুড়োকে কাছে টেনে নিলেন। ওসব কিছু না করলেই বরং উনি বেশ ক’বছর বাঁচতেন। উনি যে যমেরও অরুচি।
বাদল সরকারের “খাট-মাট-ক্রিং” নাটকে মানুষ মানুষকে ‘খাট-মাট-ক্রিং’ করে দুনিয়া থেকে নিশ্চিহ্ন করার পর দেখা গেল বঁেচে আছে শুধু আরশোলারা।
আরশোলার জান বড় কড়া হয়। কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে টঁিকে থাকার মন্ত্র ওদের জানা আছে। বুদ্ধিমতী সুষমা সতীনকে দেখে বঁেচে থাকার কলাকৌশল শিখলেন। উনি ততদিনে জেনে গেছেন– “এ দুনিয়া বড়ী ঘাগ্ হ্যায়”! কাজেই কোলেকাঁখে একছেলে-একমেয়ে নিয়ে বিধবা সুষমা দেশভাগের পর কোলকাতার পাতিপুকুর অঞ্চলের তঁেতুলতলায় উদ্বাস্তু কলোনিতে মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি গড়ে তুললেন (যেখানে এখন জয়া সিনেমা হল), জমির লড়াই লড়ে পাট্টা আদায় করলেন এবং দীর্ঘজীবি হলেন।
আর সমাজের চোখ-রাঙানিকে কলা দেখিয়ে উনি জীবনসঙ্গী হিসেবে এক ছুতোর ভদ্রলোককে নিজের বাড়িতে এনে আজীবন রাখলেন। এমন দাপটের সঙ্গে রইলেন যে সৎছেলের ভালবাসা ও শ্রদ্ধা আদায় করতে ওনাকে বিশেষ বেগ পেতে হল না। কিন্তু সে অন্য গপ্পো।
গিন্নি ছাড়বে কেন? বললো– যদি আর এক রাউন্ড চা খাবে তাহলে আগে আরো কিছু গপ্পো শোনাও। আর এসব কি নাম দিয়েছ, বাঙালবৃত্তান্ত? মানে বাঙালদের ঘরের কেচ্ছা-কেলেংকারি? তোমার কি ভীমরতি হল? নিজেদের ডার্টি-লিনেন কেউ রাস্তায় বসে কাচে? তাও এমন আছড়ে আছড়ে!
– আরে না-না, বৃত্তান্ত মানে কেচ্ছা নয়, এ হল যাকে বলে ‘টেইলস’- সেই ‘ক্যান্টারবেরি টেইলস্্’ এর মত।
“সক্কাল সক্কাল মরতে চাস্? ত’ কীনা’র মা’রে বিয়্যা কর।” — এর মানে জানো? এইসব প্রবাদের পেছনে একেকটি সামাজিক ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে, ঠিক লেজের মত। কীনার মা হলেন জনৈক মুসলমান মহিলা, বিধবা। লোকের বাড়ি বাড়ি ফাই-ফরমাস খেটে দিন গুজরান হয়। ছেলেপুলে নেই, আছে দুইবিঘে জমি, কংসনদীর পাড়ে। সেই জমির টুকরো গাপ্ করার লোভে লোকে আসে নিকের প্রস্তাব নিয়ে। কীনার মা রাজি হয়, কাজি আসেন। মহিলাটি একা থেকে দোকা হয়। কিন্তু, লোভী পুরুষটি বছর ঘোরার আগেই গোরের মাটি পেয়ে যায়। এমন বারচারেক হওয়ার পর লোকে ভয় পেল। ভাবলো– ওর পেছনে নিশ্চয়ই কোনো পোষা মামদো ভূত (মহম্মদী ভূত?) আছে।
ওকে বিয়ে করলে মৃত্যু অবধারিত। ব্যাস্, মুখে মুখে তৈরি হল প্রবাদ, “সক্কাল সক্কাল মরতে চাস? তো কীনার মা’রে বিয়া কর।”
অতিরিক্ত এককাপ চায়ের লোভে বলে উঠি– এটা শোন, “মুত্্তে ছাগী ধরে না, দৌড়াইয়া লাগাল পায় না।” এর মানে হচ্ছে- এ স্টিচ্ ইন টাইম, সেভস্ নাইন। কারণ হল – স্ত্রী-ছাগলকে দৌড়ে ধরে ফেলা কঠিন। কাজেই ও যখন সু-সু করছে–
– “বাস্ করো, রামদাস”। এবার ক্ষ্যামা দ্যাও। অনেক বোর করেছ। বরং তোমার আপনজনের কথা কিছু বল। ভাল গপ্পো শোনালে আজ দুপুরে মেটুলির দো-পঁেয়াজি বানিয়ে দেবো।
– তাহলে শোন, মাঝখানে ডিস্টার্ব করতে পারবে না কিন্তু।
(২)
আটষট্টির শীতের কলকাতা। সলিলকুমার মধ্যপ্রদেশের ভিলাইনগরের থেকে তাড়াহুড়ো করে নাকতলায় পরিবােরর এজমালি বাড়িতে উঠেছেন, ছেলের সঙ্গে দেখা করতে। সন্ধ্যে সাতটা বাজে, ছেলেকে খবর পাঠানো হয়েছে। এখনও এসে পৌঁছয়নি। সলিলের ছটফটানি বাড়ছে।
আসলে সলিল সাতদিন আগে মায়ের একটি চিঠি পেয়েছেন– তোমার ছোটছেলে বাড়ি ছাড়িয়া গেছে। লেখাপড়া করিবে না, দেশোদ্ধার করিবে। কোন্ বিদেশি গুরুঠাকুরের কাছে দীক্ষা নিয়াছে কে জানে! তিনি নাকি বলিয়াছেন– যে যত পড়ে সে তত মূর্খ হয়। অনেক বুঝাইয়াছি। ওরে, তোর মা-বাবার কথা একবার ভাব। কত আশা নিয়া ভিলাই হইতে টাকা পাঠাইতেছে, তোরা লেখাপড়া শিখিয়া পরিবারের মুখোজ্জ্বল করিবি। কিন্তু চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী। সে উল্টা আমাকে বুঝায়, — শচীমাতা যদি না কাঁদিত, নিমাই কি করিয়া জগৎকে প্রেমধর্ম শিখাইত?
তুমি একবার আসিয়া দেখ, যদি পথে ফিরাইতে পার। আমি হার মানিয়াছি।
দরজায় হাল্কা করে কড়া নড়ে উঠলো। সলিল সিগ্রেট অ্যাশ্্ট্রেতে গুঁজে প্রায় লাফিয়ে গিয়ে দরজা খুল্লেন। দু’টি ছেলে দাঁড়িয়ে, বয়স সতেরো-আঠেরোর মধ্যে। একজন ভেতরে এসে সলিলের পায়ে হাত দিয়ে প্রণামও করলো।
সলিল ছেলেকে বল্লেন– ভেতরে এস, বন্ধুকেও ভেতরে এনে বসাও।
– না, ও রাস্তায় অপেক্ষা করবে, আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবে।
– মানে? তুমি আজকে রাত্তিরে এখানে থাকবে না? তোমার মা ও এসেছেন, তাঁর সঙ্গে দেখা করবে না? কথা বলবে না?
– দেখা করবো না কেন? কিন্তু রাত্তিরে আমাকে ফিরে যেতেই হবে।
– সো মাচ্ কমিটমেন্ট! অ্যাট্ দিস্ টেন্ডার এজ্? বেশ, কিন্তু আমার সঙ্গে যে অনেক কথা বলার আছে। তার কি হবে?
– ঘন্টা দুই বসছি, এর মধ্যে সব কথা শেষ হওয়া উচিৎ।
– ইয়ং ম্যান, you owe me some explanation. Don’t you think so?
বাপ-ছেলের রাজনীতি-সমাজনীতি নিয়ে শাস্ত্রবিচার মাত্র কুড়ি মিনিটে শেষ। ছেলে বড় একগুঁয়ে। সলিল যত বলেন যে বিশাল বহুমাত্রিক ভারতবর্ষের সমস্যাকে বোঝা এত সহজ নয়, চীন-ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক গঠন আলাদা, চীনের চশমায় এ দেশকে বোঝার চেষ্টা বাতুলতা। এর চেয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের লেখা পড়লে ভালো হবে,..
— ছেলের মুখের ভাবে কোনো পরিবর্তন হয় না। যেন কাঁচের দেয়ালের সঙ্গে কথা হচ্ছে।
সলিলের ভেতরের চাপা অসহায় রাগ এবার ফুটে বেরুলো।
– আমি জানতে চাই, তুমি নিয়মিত পড়াশুনো করে হায়ার সেকেন্ডারির পর এখান থেকে এম. এ. কমপ্লিট্ করবে কি না? আমি আমার পরিশ্রমের পয়সা তোমাদের পেছনে জলের মত ঢালছি। সে কি ফুটোপাত্র? জবাব দাও। আর যে ভদ্রলোক পড়াশুনো করে মূর্খ হয় শেখাচ্ছেন তিনি নিজে কি পড়েন নি? বা বই লেখেন নি? পড়লেই যদি মূর্খ হয়, তাহলে ওঁর বইগুলোই বা কেন পড়তে হবে? তোমরা ধর্ম মান না। বেশ, কিন্তু ভেবে দেখেছ কি যে “রেড্্বুক” এর কোটেশন মুখস্থ করা আর না বুঝে রোজ গীতাপাঠ করা প্রায় একইরকম!
ছেলে চেয়ার থেকে উঠলো। — আমি যাচ্ছি, মা কে ডেকে দাও।
সলিল হতবাক। ক’মাস আগেও ছেলেটা এই বাড়িতে থেকে পড়াশুনো করেছে, স্কুলে গেছে। আর আজ এমন করছে যেন আউটসাইডার। ভেতরের ঘরে যাচ্ছেনা।
এর মধ্যেই এত দূরত্ব তৈরী হয়ে গেছে! কি করে?
(৩)
রাত প্রায় বারোটা। শীতের নাকতলা ঘুমিয়ে কাদা। সলিলের চোখে ঘুম নেই। ছেলে মায়ের কান্নাকাটিতেও গলে নি, চলে গেছে। এই ছেলেটা এমন পাষাণ হয়ে গেল? আর কি অহংকার! সলিলের প্রশ্নগুলোর ঠিক করে জবাব দেওয়ারও দরকার মনে করলো না! এইটুকু পুঁচকে ছেলে, মাত্র সেদিন ডিম ফুটে বেরিয়েছে। কি পড়েছে এরা? দেশকে কতটুকু জানে? দেশের ইতিহাস, জনমানস– এত সোজা বিপ্লব করা? বিপ্লবে লেখাপড়ার কোন দরকার নেই? কী সর্বনেশে কথা! এখনও তো স্কুলের গন্ডী ডিঙোয় নি।
(রাত্তিখানি উনিপুক, তার নাই নাকমুখ, হে আইছে আমারে শিখাইতে?)
কেন যেন সলিলের মনে পড়ে গেল আর এক উদ্ধত তরুণের কথা– গগনচন্দ্র রায়, সলিলের পিতামহ। সলিলের রোল মডেল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে নামজাদা সিভিল অ্যাডভোকেট। স্যার রাসবিহারী ঘোষের জুনিয়র। দীঘাপাতিয়া এস্টেটের মামলা জিতিয়ে দীঘাপাতিয়ার রাজার থেকে দোশালা উপহার প্রাপ্তি। কিন্তু নিষ্ঠাবান হিন্দু। নিজের জীবনে চতুরাশ্রম পালন, বাণপ্রস্থ গমন ও সন্ন্যাস, — কোনটাই ফাঁকি দেন নি। পয়েও ত্যাগ করতে পারার ক্ষমতা ভিক্টোরিয়ান রুচির সলিলকে বড় আকর্ষণ করে, আকর্ষণ করে ব্রহ্মচর্য্য। বিশ্বাস করেন যে বীর্য কে ধরে রাখা বীর্যত্যাগের চেয়ে বড়। বিশ্বাস করেন যে শরীরের ভাঁড়ারে বীর্যের স্টকপাইল্ যখন ছাদ বা ব্রহ্মতালু ছোঁবে তখন মানুষ অমিত শক্তিধর হবে।
কেন? বার বার চেষ্টা করেও হেরে যান বলে? তাই বোধহয় সমারসেট মম এর উপন্যাস “অফ হিউম্যান বন্ডেজ” সলিলের এত প্রিয়। কিন্তু আজ রাতে মনে পড়ছে প্রৌঢ় গগনচন্দ্রকে নয়, এক গর্বিত তরুণ গগন রায়ের কথা।
১৯৯৫ সালের ময়মনসিংহ শহর। তখনও এই শহর দেশের প্রথম র্যাংলার আনন্দমোহন বসু বা উমেশচন্দ্র বনার্জি বা নীরদ সি চৌধুরীর শহর হয়ে ওঠেনি। শহরটির উপকন্ঠে লালবাতি এলাকা। তার কাছেই শস্তার একখানি ঘর ভাড়া নিয়ে বিধবা মায়ের বড় ছেলে গগন প্রবেশিকা, থুড়ি এনট্রান্সের পড়া করছেন। স্বপাকে খান। কিন্তু একদিন এক বয়স্ক মহিলা এসে বল্লেন– তোমাকে দেখি। রোজ পাত্্কো থেকে রশি টেনে জল ভর, রান্না কর, তারপর খেয়ে বাসন মেজে পড়তে যাও। যদি কিছু মনে না কর, তাহলে আমি তোমাকে জল তুলে বাসন মেজে মশলা বেটে দেব, কোন পয়সা লাগবে না। আমার এই সামান্য সেবাটুকু স্বীকার কর, বাবাঠাকুর।
গগনচন্দ্র রাজি হলেন। খানিকটা নতুন বয়সের উদার চিন্তার প্রভাব, খানিকটা সেবা ও সুবিধে পেতে ভালো লাগে– রক্তে মিশে আছে যে।
এইভাবেই দিন কাটছিল। গগনচন্দ্রের স্বপ্ন বড় আকাশে ওড়ার। স্কুলের পর ওকালতি পাশ করে কলকাতায় প্র্যাক্টিস করা। আঠারবাড়িয়ার গ্রামীণ সমাজের আবহাওয়ায় কেমন যেন দমবন্ধ ভাব। আর একটা জিনিস ওনার বড় অপছন্দ, তা হল গ্রামের কৃষ্ণলীলা, — সে আসরে গড়াগড়ি িদয়ে কীর্তন গাওয়াই হোক বা “ঘাটু”, অর্থাৎ বর্ষাশেষে নদীর ঘাটে ছোটছেলেদের রাধা বা গোপিকা সাজিয়ে কৃষ্ণলীলা। বড় স্থূল, প্রায় অশ্লীল।
একদিন এক টেলিগ্রাম এল। — “মাদার ইল, কাম শর্াপ”। গগনচন্দ্র ভাড়াটে বাড়ির দরজায় তালা ঝুলিয়ে সেই বিগতযৌবনা রূপোপজীবিনী মহিলাকে চাবি দিয়ে গৃহগ্রাম আঠারবাড়িয়ার দিকে রওয়ানা হলেন। রেলস্টেশনে নেমে কয়েকমাইল হাঁটাপথ। মাঝরাস্তায় পেয়ে গেলেন গাঁয়ের দফাদার “মিছার-বাপ”কে। মিছার-বাপের আসল নাম আলাদা। কিন্তু সর্বজনস্বীকৃত নাম মিছার-বাপ। এবং উনি সার্থকনামা, মিথ্যে কথা বলতে একটু আটকায়না। তা’ বলে কর্তার সামনে মিথ্যে বলা? কাজেই গগনচন্দ্রের স্বাভাবিক প্রশ্ন– “মা কেমন আছেন?” এর উত্তর দিতে দফাদারের বিষম খাওয়ার অবস্থা। গলা খাঁকরে বল্লো– এখন ভালোই আছেন।
– কি হইছিলো? অসুখডা কি? — এর উত্তর দিতে আবার গলা খাঁকরি, এবং শেষে– আপনে বাড়ি গিয়া সব জানবেন।
রহস্যের গন্ধ! গগনচন্দ্র উত্তেজিত। সামনের মাসে পরীক্ষা। ভেবেছিলেন পরীক্ষা দিয়ে একেবারে শহরের পাট চুকিয়ে বাড়ি আসবেন।
বাড়ি পৌঁছে দেখলেন সামনের ঘরে মা মোড়া পেতে বসে আছেন। চেহারায় অসুস্থতার চিহ্ন মাত্র নেই। তাহলে তাঁকে মিথ্যে টেলিগ্রাম করে ডাকা হয়েছে! এই দুঃসাহস কার? গগনচন্দ্রের ক্রোধ গলার ঝাঁঝে প্রকাশ পেল। লেখাপড়া শেখা বড়ছেলের প্রশ্নের জবাবে অপরাধী মা আমতা-আমতা করে বল্লেন– দ্যাবতাদের নির্ণয় হইছে।
দ্যাবতা? মানে দেবতা? ও হরি! ভূদেব? মানে গাঁয়ের ব্রাহ্মণসমাজ!
ইতিমধ্যে দফাদারের পেছন পেছন বারান্দায় উঠেছেন জনাতিনেক বর্ষীয়ান ভদ্রলোক, খালি গায়ে উত্তরীয় সম্বল, যজ্ঞোপবীত চোখে পড়ে। সবার আগে যিনি তাঁর ধুতি ও উড়ুনি একটু দামী। শ্যামাচরণ চক্রবর্তী, রায়েদের পাল্টি ভূমধ্যাধিকারী পরিবার, ব্রাহ্মণসমাজের মাথা। — আইয়া পড়ছ বাপ? হাত-পাও ধইছ? কিছু মুখে দিছ?
এইতা সাইরা লও, তারপরে কথা হইব।
– গৌরচন্দ্রিকার দরকার নাই, কামের কথা কন। এইসব ছল-প্রপঞ্চের কি দরকার ছিল?
– দরকার ছিল, দরকার ছিল। মাথা ঠান্ডা কর, তবে বুঝবা। তাই কই- স্নান কইরা খাইয়া দাইয়া লইয়া তারপর কথাবার্তা কইলে কামে দিব।
– না আগে কন। না হইলে আমর গলা দিয়া অন্ন নামবো না।
চক্রবর্তী মশায়ের চোয়াল শক্ত হল।
– বেশ, কামের কথাই কই। তুমি ময়মনসিংহ শহরে গেছ অধ্যয়ন কইরা মানুষ হইতে, তোমার পিতাঠাকুর ঈশ্বর রামকানাই ইন্দ্রের ভূ-সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও বংশধারার প্রতিপালন করার যোগ্য হইতে। ঠিক কইলাম?
– ঠিক, কিন্তু আমার আচরণে এর অন্যথা হইতে কই দ্যাখলেন? আমি কি মন দিয়া পড়াশুনা করি নাই? তা হইলে পরীক্ষায় ভাল ফল হয় ক্যামনে?
– তুমি বুদ্ধিমান, পড়াশুনায় নিষ্ঠায় অভাব এমন কথা পরমশত্রুতেও কইবো না। কিন্তু আমাদের কাছে খবর আছে যে ইদানীং একটি ব্রাহ্মপরিবারে তোমার যাতায়াত বেশি। সেই বাড়িতে দুই বয়স্থা অবিবাহিত কন্যা। তারা পর্দা মানে না। পরিবারের বাইরের পুরুষের সঙ্গে অনায়াসে আলাপ করে, এমনকি তাদের গুরুজনদের উপস্থিত থাকা দরকারী মনে করে না। এই যাবনিক-আধা-কিরিস্তান পরিবেশে তোমার নিয়মিত উপস্থিতির খবরে তোমার মাতাঠাকুরাণীর বুকের ব্যথা সত্যই বৃদ্ধি পাইছিল।
তোমাদের বাড়ির নাটমন্দিরে গোবিন্দজীউ’র অধিষ্ঠান, নিত্য ভোগ আরতি হয়। শালগ্রাম শিলার পূজা হয়। তোমরা বংশপরম্পরায় ত্রিপুরার পত্তনের বিখ্যাত গোস্বামীপরিবারের যজমান। তুমি সনাতন হিন্দুধর্মের এই বৈভব ছাইড়া ইংরেজঘঁেষা ব্রাহ্মদের আবোলতাবোল তামসায় যোগ দিবা– এইডা কি উচিৎ?
রোগা, খঁেকুড়ে, টিকিতে ফুলবাঁধা আচায্যি চেঁচিয়ে উঠলেন– ব্রাহ্মরা ছেলেধরা। অরা মাইয়াদের বাল্যবয়সে বিয়া দেয় না। ভালবংশের ছ্যামড়া দেখলে বাড়িতে ডাইক্যা আইন্যা চা আর সায়েববাড়ির বিস্কুট খাওয়ায় আর মাইয়াদের লেলাইয়া দেয়।
ক্রুদ্ধ গগনচন্দ্র জলচৌকি থেকে উঠে দাঁড়ালেন। — ভূদেবরা এইবার আসেন। আমি প্রাপ্তবয়স্ক হইয়া নিজের বুদ্ধি-বিবেকের হিসাবে কি করবাম হেইডা আমার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। এই নিয়া গ্রামে সালিশীসভার প্রয়োজন দেখি না। আর ব্রাহ্মদের আপনারা কাছের থেইক্যা দ্যাখেন নাই। তাঁরা সংস্কৃতিবান রুচিশীল মানুষ। নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক। উপনিষদের মন্ত্র উচ্চারণ কইরা প্রার্থনা করেন। হ্যাঁ, পাথর বা গাছের গোড়ায় জল ঢাইল্যা পূজা করেন না। কিন্তু তারা যে হিন্দুধর্মের বাইরের সম্প্রদায় কি আধা-খ্রীস্টান, সেই বিচার আপনারা ক্যামনে কইরা ফ্যালেন?
শ্যামাচরণ চক্রবর্তী গোঁফের ফাঁকে হেসে ফেল্লেন। — তুমি কি আমরার লগে শাস্ত্রবিচার করতে চাও? এই বয়সেই নৈয়ায়িক হইবা? তুমার শাস্ত্রজ্ঞান কতটুকু?
গগনচন্দ্র দমবার পাত্র ন’ন। — বয়সের কথা ছাড়ান দ্যান। আপনারাই পরীক্ষা কইরা দেইখ্যা নেন।
শ্যামাচরণের চোখ গগনচন্দ্রের চোখে নিবদ্ধ। — বেশ, কিন্তু একখান শর্ত আছে। যদি পরাজিত হও? তাহইলে সারাজীবন নিষ্ঠাবান হিন্দুর আচার পালন করতে অইবো। আপত্তি আছে?
– কুন আপত্তি নাই। কিন্তু আমারও একখান শর্ত আছে। যদি উল্টাডা হয়, তাহইলে আপনেরা আমার কুন কামে বাধা দিতে পারবেন না। কি কন?
– রাজি। কাইল তোমাদের বাড়ির নাটমন্দিরের সামনে, সন্ধ্যারতির পর। জয়-পরাজয়ের নিষ্পত্তি কিভাবে?
– অতি সহজ। আমি আপনাদের প্রশ্নের সামনে নিরুত্তর হইলেই আমার হার।
সূর্য ডুবলেও আকাশে তখনও গোলাপি আভা। গাঁয়ে গাঁয়ে এই বার্তা রটি গেল ক্রমে। আরতির পর– “সে গোবিন্দ, হে গোপাল! কেশব-মাধব-দীনদয়াল” শেষ হল। নাটমন্দিরের সামনে খালি জায়গাতে গোটা দুই তক্তপোষ আর চারটে জলচৌকি। একটু দূরে দাঁড়িয়ে পাশের তিনচার গাঁয়ের জনা তিরিশেক ইতরজন। এই মল্লভূমিতে কোন মহিলা উপস্থিত ন’ন।
পূর্বপক্ষ গগনচন্দ্র শুরু করলেন।
– ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্মের বিশিষ্ট অঙ্গ, শুধু তাই নয়, চিন্তনপ্রক্রিয়ায় সবচেয়ে অগ্রগামী অংশ। উপনিষদের দর্শনচিন্তার সার হল শঙ্করাচার্য্য প্রচারিত অদ্বৈতবেদান্ত। অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। ঈশ্বর এক ও অদ্বিতীয়। কাজেই নিরাকার। কারণ এই “অণোরণীয়ান মহতোমহীয়ান” তত্ত্বকে কোন পরিচিত আকারে বাঁধা যায় না। অতএব এই নিরাকার ব্রহ্মের উপাসক ব্রাহ্মধর্মকে কি ভাবে বৃহত্তর হিন্দুসমাজের বিরোধী ও যাবনিক বলা যায়?
আর এরা জ্ঞানমার্গের পথিক। সাধনপদ্ধতিতে নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনা অতি উত্তম। ভক্তিমার্গ, পুরাণকথা, তেত্রিশকোটি দেবতার পূজা– এইসব অশিক্ষিত ইতরসমাজের উপযুক্ত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত ভদ্রসমাজের জন্য ব্রাহ্মমত সর্বথা উৎকৃষ্ট।
– অ! আগে জগৎমিথ্যাত্ব প্রতিপাদিত কর!
– দার্শনিক স্তরে যাহা অপরিবর্তনীয় বা শাশ্বত, তাহাই সত্য। নামরূপের বন্ধনে প্রকাশিত এই জগৎ সদা পরিবর্তনশীল, যাহা দেশকালের ঊর্ধ্বে নয়, অপরিবর্তনশীল নয়, তাহা নশ্বর। অতঃ মিথ্যা।
– এই ‘মিথ্যা’ জগৎ কিভাবে সৃষ্ট হয়? বা সত্যরূপে প্রতিভাত হয়?
– ব্রহ্মের মায়ায়। জীবের চেতনায় অবিদ্যাজনিত ভ্রমের কারণে এই নশ্বর অসত্য জগৎ সত্যরূপে প্রতিভাত হয়, যথা রজ্জুতে সর্পভ্রম।
পন্ডিতেরা মুখচাওয়া-চাওয়ি করে চোখে চোখে একটু হাসলেন, সেটা গগনচন্দ্র দেখতে পেলেন না।
– এই “মায়া” কি ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র কোন তত্ত্ব? না ইহা ব্রহ্মের কোন ধর্ম?
গগনচন্দ্র গুগলিটা দেখতে দেরি করে ফেলেছেন।
ওনার ইতস্ততঃ ভাব দেখে আচায্যি উঁচু স্বরে বল্লেন– কিছু বলার আগে ভাল কইরা ভাব। যদি মায়া ব্রহ্মনিরপেক্ষ কোন স্বতন্ত্র বস্তু হয়, তাহা হইলে অদ্বৈতের জায়গায় দ্বৈতবাদের স্থাপনা হয়। যদি ইহা ব্রহ্মেরই ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য হয়, তাহা হ্যলে বিকৃতিশূন্য নির্গুণ ব্রহ্ম থাকে কই?
গগনচন্দ্রের গলায় আগের জোর নেই। তবু বল্লেন– মায়া ব্রহ্মের অনির্বচনীয় ধর্ম। মানবমন ব্যবহারিক নামরূপের জগৎ ও নিরাকার নির্গুণ ব্রহ্মের মাঝে সেতুস্বরূপ এই মায়ার কল্পনা করে।
– বেশ, তবে পারমার্থিক ছাড়া এই নামরূপের জগৎকে তোমরা “ব্যবহারিক” রূপে স্বীকার কর। শংকর প্রচ্ছন্নবৌদ্ধ ছিলেন। বেদান্তের শংকরভাষ্য পড়েছ, কিন্তু রামানুজের সাতটি আপত্তি পড়া হয় নাই। আসলে তোমার অধ্যয়নের অগ্নিমান্দ্য হয়েছে।
শোন, আমরা বৈষ্ণবধর্মাবলম্বীরা বৃহৎ অর্থে রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের অনুযায়ী, আর সূক্ষ্ণ অর্থে চৈতন্যমহাপ্রভুর “অচিন্ত্যভেদাভেদ” দর্শনের। আরও শোন, — পারমার্থিক জগৎ ছাড়াও নামরূপের ব্যবহারিক জগতের অস্তিত্বকে কেবল বাগ্্বিভূতি দিয়ে অস্বীকার করা যায় না। শংকরও পারেন নাই। তাই পরে শিবাষ্টক স্তোত্র, গঙ্গাস্তোত্র লেইখ্যা পাপ-স্খালনের চেষ্টা।
এই জগৎ মায়া নয়, ব্রহ্মের লীলা। “একোহং বহুস্যাম”। একাকী ব্রহ্ম মনে করিলেন আমি বহু হইব। এই এক থেকে বহু হওয়ার ইচ্ছা মানবমনের একটি চিরন্তন সংস্কার। কারণ আমরা ব্রহ্মের অংশ। তাই পুরুষ-প্রকৃতি, তাই সন্তান-সন্ততির আকাঙ্ক্ষা। তাই সমাজনির্মাণ। নইলে মানুষ আজও জঙ্গলে থাকিত।
গগনচন্দ্র নিরুত্তর।
শ্যামাচরণ চক্রবর্তী যেন দেখেও দেখলেন না।
–জ্ঞানমার্গ সবার জন্যে নয়। তুমি সেই পথের পথিক, ভাল কথা। কিন্তু বহুসংখ্যক মানুষের ভক্তিমার্গ নিয়া আবেগকে তুচ্ছ কর কোন অধিকারে?
চৈতন্যমহাপ্রভু প্রথম জীবনে তোমার মত উদ্ধত নৈয়ায়িক ছিলেন। নবদ্বীপে লোকে কইত “নাস্তিকের শিরোমণি”। তিনিই পরে নামলেন নগরসংকীর্তনে, — “আচন্ডালে ধরি দেই কোল”। আর নিরাকারসাধনা একাঙ্গী, সাকারসাধনায় নিরাকারও নিহিত আছে, বর্জিত নয়। রাজপথ ছেড়ে অন্ধগলিতে যাও কেন?
ব্রাহ্মসমাজ আসলে নিরাকার সাধনার আড়ালে মূলতঃ সনাতন হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে “পৌত্তলিকতা”র অপবাদ দিয়া ইংরেজদের রাজধর্মের তোষামোদ করে।
অধিকাংশ ব্রাহ্মপরিবার ধনী। তারা ইংরেজ রাজপুরুষদের চাটুকারিতা করে– ইহা দেখ নাই?
আমাদের বৈষ্ণবধর্ম আপামর জনসাধারণের জন্যে। সমাজের বিরুদ্ধতা করায় মানুষ শক্তিহীন হয়, সঙ্গে থাকলে শক্তিবৃদ্ধি।
গগনচন্দ্র নিরুত্তর।
তামাসা দেখা লোকজন হতাশ হয়ে অনেক আগেই কেটে পড়েছে। নাটমন্দিরে ঘন্টা বাজলো। ঠাকুরকে শোয়ানোর সময় হয়েছে। পূজারী এসে সবাইকে প্রসাদ দিলেন। গগনচন্দ্র খানিকক্ষণ ভাবলেন, তারপর মাথায় ছুঁইয়ে গ্রহণ করলেন।
পাঁচ প্যাকেট পানামা সিগ্রেট শেষ। বাগানে নারকোল গাছে কোন একটা পাখি ডেকে উঠলো। পাশের সুপুরি গাছ থেকে জবাব দিল আরো একটা পাখি। অন্ধকার ফিকে হয়ে আসছে। সলিল বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন।
ঠাকুর্দা গগনচন্দ্র কথা রেখেছিলেন। সারাজীবন নিষ্ঠাবান হিন্দু রইলেন। ওকালতিতে ও তালুকদারিতে সফল হলেও “পঞ্চাশোর্ধ্বে বনং ব্রজেৎ” এই আপ্তবাক্য স্মরণ করে ছেলে সতীশচন্দ্রের হাতে সংসারের ভার সঁপে দিয়ে বৃন্দাবনে কুটির নির্মাণ করে রইলেন। দু’বেলা মাধুকরীবৃত্তি করে (গোদা বাংলায় “ভিক্ষে দাও গো ব্রজবাসী” বলে) আহর করলেন। বারো বছর পরে দেশের বাড়িতে ফিরে এসে বাইরের দিকে একটা ঘর বানিয়ে শেষ জীবনটা কাটিয়ে দিলেন।
হ্যাঁ, বড় নাতি সলিল কুমার প্রায়ই সন্ন্যাসীদাদুর পুকুরের ঘাটে পায়খানা করে রাখতেন। মনে আশা যে দাদুর পা ওখানেই পড়বে। সে আশা প্রায়ই পূর্ণ হত।
অজান্তেই সলিলের ঠোঁটের ফাঁকে একচিলতে হাসি ফুটে উঠলো। তারপর বুকের মধ্যে একটা ব্যথা চিনচিন করে উঠলো। না, তাঁর আর ছেলের কথাবার্তা ঠাউর্দার প্রথম জীবনের বিতর্কসভার মত করে শেষ হয়নি। দুর্বিনীত ছেলে মাথা নোয়ায় নি, চলে গেছে।
সময় বদলে গেছে অনেকখানি। প্রায় আশিবছরের তফাৎ। এবার সলিলকে ফিরতে হবে, ভিলাইয়ে, নীরস কর্মক্ষেত্রে। বাড়িতে থাকবেন মাত্র দু’জন। সলিল আর স্মৃতিকণা। খালি সময় যেন গিলতে আসবে। তবু তাঁরা অপেক্ষায় থাকবেন। যদি ছেলে ফিরে আসে, অকাল-বনবাস থেকে, কোন মাস, কোন বছর।
(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)


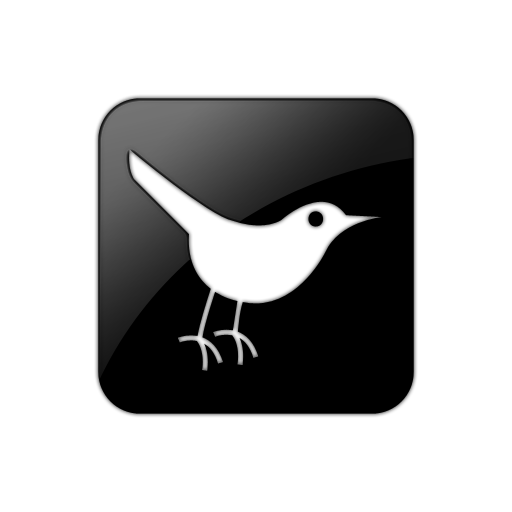
Leave a comment